তাঁকে লিখবার জন্য একটা খাতা চাই, লাল কাপড়ে বাঁধাই করা, হলদে রঙের নির্জন পাতার এক খাতা। ছোটগল্পের মতন তিনি, স্পর্শ করা যায়, বেঁধে ফেলা যায় না। শেষ হয়েও হয় না শেষ। শব্দসীমার মাঝে ফেলে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে ধারণ করবার চেষ্টাটা অসম্পূর্ণ তাই। তবু অসময়ে তাঁকে নিয়ে লিখছি এই ভেবে যে, অল্প করে তবে শুরু হোক। তাঁকে নিয়ে লিখে যাব, যখন যেমন ইচ্ছে, একটু একটু করে। স্রোতস্বিনীর মতন, অবিরাম জলধারার মতন লিখতে লিখতে হয়তো তাঁর সৃজনশীলতা, মননশীলতা আর বিশালতাকে খানিকটা স্পর্শ করা যাবে।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ছোটগল্পগুলো স্রেফ একরৈখিক কোনো গল্প নয়। আমি তাঁর ছোটগল্পে খুঁজে পেয়েছি উপন্যাসের বীজ। গল্পের ভাঁজে ভাঁজে তিনি নতুন গল্প সৃষ্টি করেছেন। এই যেমন, ‘সম্মতি’ গল্পটি আসিফ, রোজিনা আর কিসলুর গল্প। গল্পের স্রোতে আমরা পেলাম এক পার্শ্বচরিত্র হিসেবে বদিকে। বদির গল্পও পূর্ণতা পেল, যেন গল্পের ভেতর আরেকটি সম্পূর্ণ গল্প। বদিকে তিনি গল্পের স্রোতে ভেসে যেতে দেন নি। জোনাকি আলোর মতন করে গল্পে মেলে ধরেছেন তাঁকে, ক্ষুদ্র কিন্তু আলোকময়।
যদি আরও জানতে চান, বদি পথেই ভ্যান গাড়িতে মারা গিয়েছিল। মারা যাওয়ার মুহূর্তে বদি দেখেছে, স্ত্রী তার মাথার পাশে বসে তাকে আদর করছে, পানি খাওয়াচ্ছে। বদির তাই মনে হলো না যে সে মারা যাচ্ছে। এজন্য কিনা, ময়নাতদন্তওয়ালা ডাক্তার তার মুখে একটা হাসি দেখে চমকে উঠেছিলেন।
এতটুকুতেই বদির এক জীবনের পূর্ণতা।
তিনি লিখতে লিখতে পাঠককে উপেক্ষা করেন নি, তাঁর অঢেল জ্ঞানঐশ্বর্য প্রকাশ করে পাঠককে মুগ্ধ করতে চান নি। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছি তাঁর পরিমিতিবোধে। জ্ঞানের প্রকাশ দেখেছি তাঁর চরিত্র ও গল্প নির্মাণের গভীরতায়। তাঁর গল্প সকলের জন্য, যে যেমন করে যতটুকু গ্রহণ করতে চায়। ‘ডিডেলাসের ঘুড়ি’ তাঁর লেখা এক নন্দিত গল্প। এ গল্পে পৌরাণিক চরিত্র ডিডেলাস ও ইকারুসকে টেনে এনেও তিনি পাঠকের নাগালের বাইরে যান নি। বরং গল্পের ভাঁজে তিনি পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেন ডিডেলাস ও ইকারুসের সঙ্গে, পরিমিতি আর সহজতার মিলেমিশে—
আহা, ইকারুসের গল্পটা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে বললে আমার গল্পের কী হবে ? কেন, মনে নেই, গ্রিক পুরাণের সেই ডিডেলাসের কথা, পুত্র ইকারুসের গায়ে মোমের ডানা লাগিয়ে যে ভাসিয়ে দিয়েছিল আকাশে। ছেলেটা পুলকিত উড়াল দিল অনেকক্ষণ, বাবা নিচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল। কিন্তু রোদের আঁচে মোম গলে যেতে থাকলে...মাগো!
গল্পকারকে যুক্তির সাথে কষে বোঝাপড়াটা করতে হয়ে। গল্পে আকাশ থেকে হাতি নেমে এসে সূর্যমুখী ফুল হয়ে যেতেই পারে, কিন্তু কেন পারে সেই যুক্তিটা দক্ষ গল্পকার কোন এক কৌশলে পাঠককে জানিয়ে দেন আলতো করে। ‘ডিডেলাসের ঘুড়ি’ এই কারণে আমার প্রিয়। পাঠকের মনে যে প্রশ্ন জমে, গল্পে গল্পে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তার উত্তর আমাদের খুঁজে দিয়েছেন। এই যেমন অশিক্ষিত সেতু মিয়া যখন তার পুত্র ঈমানকে ঘুড়ির সাথে বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দিতে চাইছে ইকারুসের মতন, তখন আমার পাঠক মনে প্রশ্ন এল, মূর্খ সেতু মিয়া তবে ইকারুসের গল্প জানে! আমাকে অপেক্ষা করতে হয় নি, আমার প্রিয় গল্পকার তাঁর উত্তর দিয়েছেন গল্পে এভাবে, “অথবা, এ রকম হয়তো মনে পড়ে নি বা পড়া সম্ভব ছিল না তার, হেতু তার শিক্ষার অভাব। আমরাই তার ওপর আমাদের চিন্তাটা চাপিয়ে দিয়েছি।”
উত্তর পেয়ে আমি হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি, গল্পের উঠোনজুড়ে হেঁটে বেড়িয়েছি আবার।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে আমি ভালোবাসি তাঁর মমত্ববোধের কারণে। তাঁর মায়ার ছায়া রয়েছে আমার জীবনভরে, আমার মতন অনেকের জীবন জুড়ে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরাও সে মায়া থেকে বঞ্চিত হয় নি। তিনি হাঁটতে ভালোবাসতেন। তাঁর গল্প পড়লে মনে হয়, পথ চলতে চলতে হয়তো কোনো পথিকের সাথে তাঁর দেখা। তাঁর থেকে খুঁজে পাওয়া গল্পটা গভীর মমতায় আসনপিঁড়ি হয়ে তিনি বলছেন আমাদের। যেমন—
মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র একটা ব্রিফকেসের গল্প জুড়ে দিল। তার গলা এমনিতে নিচু, তারপর তোতলামি আছে কিছুটা। আর গল্প যদি বলতেই হয় বাবা, মৌচাকের সামনের জলকাদা আর আবর্জনাময় রাস্তার কাঁধটা কেন বেছে নেওয়া ? রাস্তা দিয়ে বাস ট্রাক রিকশা যাচ্ছে যে যার মতো সময় নিয়ে, আর মোহাম্মদ আলী ইনিয়ে-বিনিয়ে মুখ খিঁচিয়ে ব্রিফকেসের গল্প করছে। রাস্তার শব্দ তার গল্পকে গিলে খাচ্ছে, অথচ গল্পটা তো আমাকে বলা, রাস্তার শব্দকে নয়।
এই সহজ অথচ তীক্ষè পর্যবেক্ষণ এবং কৌতূহল সৃষ্টিতে তিনি অনন্য। ব্রিফকেসের ভেতরের গল্প না জানা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই।
আবার ‘কাঁঠালকন্যা’ গল্পটা শুরু করেছেন এভাবে—
আফসারের গল্পটা কোনো কাঁঠাল বিশেষজ্ঞকে শোনাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাই, জগতে কাঁঠালবিশেষজ্ঞ বিরল। আমার বিশ্ববিদ্যালয়েও কোনো কাঁঠালবিশেষজ্ঞ নেই। অবাক, এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়! এত কাঁঠাল গাছ এর ক্যাম্পাসে! উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ডঃ মনিরুল আলম হর্টিকালচার বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। তাকে কাঁঠাল নিয়ে প্রশ্ন করতে বললেন, ‘দুঃখিত, প্রফেসর সাহেব। আমি ডুরিয়ান সম্পর্কে যতটা জানি, কাঁঠাল সম্পর্কে ততটা না। ডুরিয়ান কাঁঠালের থাই সংস্করণ, যদি জানতে চান।
আহা, আফসারের গল্পটি বলতে চাওয়ার যে অস্থিরতা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন প্রথম বাক্যে, তা আমাদের প্রভাবিত করে। আমরা তাঁর পাশে হাত-পা ছড়িয়ে গালে হাত দিয়ে বসে যাই ‘কাঁঠাল কন্যার’ গল্প শুনব বলে। তিনি গল্পের সাথে কোনো চতুরতা করেন নি। ভাষার কৃত্তিম সোনালী-রুপালি রাংতা মোড়ানো ঝলকানির ফাঁদে পাঠককে ফেলে তিনি গল্পকে আড়াল করেন নি, স্পষ্ট করে গল্পটা বলেছেন। জটিলকে ততটুকু সহজ করেছেন, যেখানে গল্প সকলের হয়ে ওঠে। তাঁর গল্প তাই আমাদের বিষণ্ন করেছে, বিরহ আর বিহ্বলতায় মাঝে বেঁধে ফেলেছে, বিপুল আনন্দ জাগিয়েছে।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের গল্প শুরুর ভঙ্গিটা একান্ত নিজস্ব; ব্যক্তিজীবনে তাঁর মমতাময় সম্ভাষণের মতোই আন্তরিক, স্নিগ্ধ ও গভীর। মনে পড়ে যায় তাঁর ‘একাত্তর’ গল্পটির কথা। প্রসঙ্গক্রমে বলি, একাত্তর নিয়ে তাঁর লেখা গল্পগুলো নিয়ে বিশদে গভীর বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, কারণ তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রান্তিক মানুষের স্বর হয়ে উঠেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে না পারার কষ্ট এখনো তাঁর অন্তরে হুল ফোটায়। বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে অনেকেই যুদ্ধ করেছেন, অথচ তাঁদের অনেকেই কোনো স্বীকৃতি পান নি, এই বাস্তবতা তাঁকে কষ্ট দেয়। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন চা-বাগানের কুলি ও শ্রমিকদের কথা, যারা যুদ্ধ করেছিলেন, অথচ ইতিহাসে যাঁদের নাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাঁর নিজের কথায়, অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করতে না পারার পাপমোচনের দায় থেকেই তিনি লিখতে চেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের গল্প; সেই প্রান্তিক মানুষের গল্প, মায়েদের বয়ানে যুদ্ধের গল্প। তিনি জানিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের উপেক্ষিত চরিত্রদের গল্প।
তাঁর লেখা ‘একাত্তর’ সেই প্রান্তিকজনেরই গল্প। বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা এক অনন্য সৃষ্টি এটি। গল্পটি পাঠককে নিয়ে যায় গভীরে, অরণ্যের গাঢ় আড়ালে, মানবিকতার অনিশ্চিত সীমানায়।
অতটুকু গভীরে, যেখানে আমরা শুনতে পাই—
আমাকে নিতে এসেছে বাঘটা, আমি সুচিত্রা সেন। কিন্তু সে আমার সম্ভ্রম নেবে না। শুধু প্রাণ নেবে। একটা ভয় অন্তত নেই।
গল্পের শুরুটা হয়েছিল এমন করে—
এই গল্পটার নাম হতে পারত ‘বাঘ’, শুধুই ‘বাঘ’, যেহেতু একাত্তরের কয়টা দিন একটি বাঘই ছিল আমাদের কাছে বড় বিভীষিকা; বাবার বর্ণনায় শোনা দূরের বন্দুক-বোমার শব্দ, অথবা রাতে পুবের আকাশের হাঁটু পেঁচিয়ে উঠতে থাকা আগুনের শিখা আর মানুষের কান্না-কোলাহল থেকেও। বাবা বলতেন, এবং আমরা শুনতাম, এবং জানতাম, কোথাও মানুষ মরছে, কোনো গ্রামে আগুন লেগেছে। জানতাম আর কল্পনা করতাম, এরপর এই মানুষগুলোর জীবনের জায়গাটাতে থাকবে একটা বড় শূন্য, অথবা তারা যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়বে অন্য একটা জীবনে, যে জীবন তাদের নয়; যে জীবন সন্তান, স্বজন কিংবা সম্ভম হারানো মানুষ অথবা উদ্বাস্তুর।
কথকের বাবার বর্ণনায় শুরু হলো গল্পটি। ‘বাবা’ চরিত্রটি তাঁর বোধহয় খুব প্রিয় ছিল। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বাবা সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, যিনি সারাজীবন শিক্ষাবিভাগে কাজ করেছেন। বাবাকে হারিয়েছেন তিনি তরুণ বয়সে। পাঠক হিসেবে বারবার মনে হয়েছে আমার, অনেকদিন আগে হারিয়ে ফেলা বাবার সাথে অসমাপ্ত কথোপকথন তিনি বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন গল্প থেকে গল্পে। তাঁর নিজের লেখা প্রিয় গল্প ‘বাঁদর’, গল্পটির শুরু বাবাকে ঘিরেই।
আমার বাবার জন্মই যেন হয়েছিল একটা কঠিন জীবনকে কাঁধে তুলে বয়ে বেড়ানোর জন্য। কিন্তু কত দূর, কোন দিকে, কোন গন্তব্যে, জীবনটাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, সে বিষয়ে কোনো ধারণা তার ছিল না।
প্রান্তিকের চেয়েও অধিক প্রান্তিক এক জীবনের গল্প, বাবার টিকে থাকার গল্প, কী নির্লিপ্ততায় বলে গেলেন! একফোটা করুণা প্রত্যাশা না করেই। ‘ভাষা’ গল্পের এক ক্লান্ত বাবার গল্পও কেমন সহজ বিকেলের আড্ডার মতন করে বলে গেলেন, শুরু করলেন এমন করে—
বাড়িতে যখন বাবার সামনে বসে আমি বই পড়ি, অথবা ছবি আঁকি, অথবা তাঁর ছেঁড়া পাঞ্জাবিটা মেরামত করি, আর বাবা কথা বলেন, প্রায়ই তখন আমার কানের ভেতর হিয়ারিং এইডের দুই জটিল মাথা গুঁজতে ভুলে যাই, তারা আমার কাঁধের দুই দিকে ঝুলে থাকে।
বাবার ছেঁড়া পাঞ্জাবিটা সব ছাপিয়ে গল্পের মূল চরিত্র হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। সেই গল্পের গহিন অরণ্য পথের ডালপালা সরিয়ে সরিয়ে আমরা হাঁটতে থাকি।
তাঁর রসবোধ যেমন আড্ডার প্রাণ ছিল, সাহিত্যকর্মেও তার ঝলমলে প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে কাঁঠাল কন্যার প্রসঙ্গ আবার টানতে হয়—
কিন্তু তার আগে আফসারের প্রেম ও বিবাহ নিয়ে বলা যায়। আফসার প্রেম করেছিল বাংলার ছাত্রী মানসীকে। কোনো ইংরেজির ছাত্র কোনো বাংলার ছাত্রীকে পাখি ভাইয়ের ঘটকালিতে বিয়ে করলেও সাধারণত একটা প্রীতিময় সম্পর্কে বাঁধা পড়ে। আফসার-মানসীর বিয়ে আবার প্রেম করে। কিন্তু শুরু থেকেই তাদের সম্পর্ক ছিল কণ্টকময়। অথবা দা এবং কুমড়ার মতো। এখানে আফসার দা, মানসী কুমড়া। এবং দায়ের ক্ষমতার সামনে কুমড়ার ভাগ্যে যা ঘটে, মানসীরও তাই ঘটেছিল।
আফসার নিজে আমাকে গল্পটা বলেছে। বিয়ের পাঁচ বছর পর। তার বিয়েতে আমি গিয়েছিলাম, অর্থাৎ যেতে হয়েছিল, যেরকম চেপে ধরেছিল সে। কাজেই বিয়ের পাঁচ বছর পর দেখা হওয়াতে বেশ খুশি হয়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার কথা, মানসীর কথা। সে মানসীর কথা শুনে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ‘এক ভয়ানক ডাইনির হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি স্যার।’
‘ভয়ানক ডাইনি ? কার কথা বলছ ?’ ‘জি স্যার। ডাইনি থেকেও ভয়ানক। সাকিউবাস। আমাকে খেয়ে ফেলেছে স্যার। ধ্বংস করে ফেলেছে।’
মুখ ঢেকে এরপর আধামিনিট কেঁদেছে আফসার। আফসারের গল্পটা এরপর শুনতে হয়েছে আমাকে।
পুরো গল্প জুড়ে তাঁর রসবোধ পাঠককে ভাবায়, হাসায়। কিন্তু লেখক এখানে নির্লিপ্ত। তিনি তাঁর তীব্র রসবোধ দিয়ে আফসারকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, কিন্তু তিনি পাঠকের উপর ভালো-মন্দের কোনো হিসাব চাপিয়ে দেন নি। যেমন দেননি ‘নেই’ গল্পে। তাঁর না-থাকার গল্প হিসেবে এই গল্পটি পাঠকদের আলোচনায় বারবার এসেছে। আসবে না কেন, কী নির্লিপ্ততা আর মমতায় তিনি বলে গিয়েছেন না-থাকার গল্প। যেন তিনি জানতেন না-থাকা কেমন হয়! গল্পটি এমন এক পরিবারের, যার প্রধান নারী চরিত্রটি পৃথিবী ছেড়ে সদ্য চলে গিয়েছেন। সেই নারীর স্বামী, পুত্র এবং পুত্রবধূর বয়ানে তিনি বলে গিয়েছেন তাদের হারানোর গল্প কিংবা মুক্তির গল্প। তিন চরিত্রের বয়ানে একটি মৃত্যুর গল্প—কারও জন্য সে মৃত্যু হারানোর বেদনা কারও জন্য মুক্তির আনন্দ।
সদ্যমৃত নারীটির দীর্ঘজীবনের সঙ্গী স্বামী চরিত্রটি ভাবছে, "ইক্যুয়ালের শিশিটা আছে, আমার চায়ের বাদামি পোরসেলিনের কাপটা আছে, টেবিলের ওপর ঘুরতে থাকা সিলিংফ্যানের ছায়াটা আছে, টেবিলের এক কোণে ওয়ান ব্যাংকের ক্যালেন্ডারটা আছে, আটটা কোস্টারের একটা সেটও আছে।
কোথাও এসবের থাকার কোনো বিড়ম্বনা নেই, বিরতি নেই, নড়চড় নেই। শুধু বোবা এই জিনিসগুলোকে একজন যে আনন্দিত ভাষা দিত প্রতিদিন, যে ভাষায় সারা সকাল-দুপুর এগুলো আমার সঙ্গে কথা বলত, সে-ই নেই।
নেই।”
পুত্র রাজু তার মা হারানোর শোকে ভাবছে, “কী এমন হলো যে সব ছেড়ে মা চলে গেলেন ? বাবাকে ছেড়ে ? আমাকে ছেড়ে ? এখন এ বাড়িতে হেঁটে বেড়ানোও একটা ভয়ানক কষ্টের বিষয়। এখন বাড়িজুড়ে শূন্যতা। সারা বাড়িতে হাহাকার। সেই হাহাকারে শামিল খাবার-টেবিলে ঘুরতে থাকা পিঁপড়াগুলোও। তারাও জানে, যার হাতের স্পর্শ থেকে ঝরে পড়া মধু ছিল তাদের প্রতিদিনের আহার, সেই মানুষটি আজ নেই।
নেই।”
আর রাজুর স্ত্রী টুম্পা ভাবছে, “আজ অনেক দিন পর সকালের খাবার-টেবিলে বসেছেন বাবা আর রাজু। দুজনই বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। দুজনের কান্না আমাকেও কাঁদিয়েছে।...টেবিলে ঘুরতে থাকা পিঁপড়াগুলোও যেন আমাকে বলছে, তোমার চারদিকে যে একটা বেড়ি বাঁধা ছিল, সেটি আজ নেই। আজ তুমি আমাদের মতো ঘুরে বেড়াও।
আজ তোমার তুমি হতে আর কোনো বাধা নেই।”
এখানেই গল্প শেষ। তিনি তার মতো কিংবা উচিত-অনুচিতের জ্ঞান আমাদের উপর চাপিয়ে দেন নি। ধূসর অঞ্চলে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের গল্পেরা বাস করে—যেখানে জীবন সাদা-কালো নয়। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের গল্প তাই বড় নির্ভার করে আমাকে। আর ভাবিয়ে তোলে তাঁর গল্পের শেষটুকু। তাঁর ছোটগল্পের সমাপ্তি টেনে নিয়ে যায় নতুন অনিশ্চিয়তায়, পাঠকের মন আর মগজের দরজাগুলো একটা একটা করে খুলে দিয়ে তিনি গল্প শেষ করেছেন বারবার।
“এসব প্যান্ট-লুঙ্গি-পাজামা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো, যাঃ হাতের সঙ্গে হাতে ধরা পারুলের রিপোর্টটাও যে উড়ে গেল। আমার বহুমূত্র হয়েছে কিনা, আর জানা হবে না। আফসোস।” ( ব্রিফকেস)
‘সম্মতি’ গল্পটি যেমন শেষ করেছেন নির্লিপ্ততায় আর পাঠকের জন্য রেখে গিয়েছেন হাহাকার, “রোজিনা কী বলেছিল মানুষের শব্দে তা শোনা মুশকিল ছিল। কিন্তু আমাদের মনে হলো, রোজিনা বলছে, আমিও রাজি, আসিফ। বা এই রকম কিছু। যাই হোক।”
ঠিক তাঁর ছোটগল্পের মতন করেই কী সহজ নির্লিপ্ততায় চলে গেলেন তিনি, আমাদের জন্য রেখে গেলেন হাহাকার। কিন্তু আমি জানি, সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা চলবে। আমার বিশ্বাস সময়ের সাথে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং পাঠক বৃদ্ধি পাবে। তিনি যে কালোত্তীর্ণ! তাঁর লেখা মঞ্চনাটক, চিত্রনাট্য, এমনকি সেই সিঙ্গার ওয়াশিংমেশিনের বিজ্ঞাপনের জন্য তাঁর লেখা বিপুল জনপ্রিয় সেই সংলাপ—“এত কষ্ট, জীবন নষ্ট!” সময়ের সাক্ষী হয়ে থাকবে।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ফেলে গেলেন মায়া, জীবনের অসম্পূর্ণতার মুখোমুখি রেখে গেলেন আমাদের, যার উত্তর কেউ জানে না। তাঁকে লিখে যেতে চাইলে লাল মলাটের সেই খাতাটা আমার প্রয়োজন, পাতার পরে পাতা লিখে যাব তাঁকে। তাঁর মায়ার গল্প, হাসির গল্প, শহরের কাদামাখা পথ ধরে আত্মভোলা এক পথিকের পথ হেঁটে যাওয়ার গল্প। ছোটগল্পের মতন তাঁর অতলস্পর্শী যে জীবন, তার কাছে প্রশ্ন করে যাব, ‘আপনার মতন করে কে বলবে আর আমাদের গল্প ?’
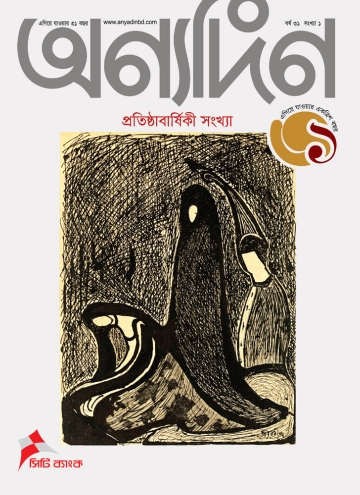














Leave a Reply
Your identity will not be published.