[১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায় ইংরেজবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন নতুন রূপ পেতে থেকে। বাংলা এবং ভারতবর্ষের এই বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে পড়ল জার্মানি এবং রাশিয়া। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বিপ্লব-প্রয়াসের প্রায় সমান্তরালে চলতে থাকল বাংলা এবং ভারতবর্ষে ইংরেজবিরোধী বিপ্লবের প্রচেষ্টা। এই উপন্যাসে একই সঙ্গে ধারণ করা হয়েছে রুশ বিপ্লবী এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া বাঙালি বিপ্লবীদের প্রেম এবং বিপ্লবের কাহিনি ও এই দুই ভূখণ্ডের বিপ্লবীদের আন্তঃসম্পর্ক। লেখাটির প্রথম খণ্ডের কাহিনি শেষ হয়েছে ১৯১৪-১৫ সালে এবং এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০২৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ড ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে ‘অন্যদিন’-এ। এই খণ্ডের গল্প আরম্ভ হয়েছে ১৯১৪ সালের রাশিয়ায় আর শেষ হয়েছে ১৯২১-২২ সালে গিয়ে।]
১০
ফেব্রুয়ারি ১৯১৬।
প্রিয় ইনেসা,
প্যারিসে তুমি যা করেছ তার কোনো তুলনাই হয় না। সবাই প্যারিসে তোমার ভূমিকার প্রশংসা করেছে। আমি এখন কী চাই জানো ? আমি চাই তুমি রাশিয়া যাও। আমি জানি ব্যাপারটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব না । তুমি প্রথমে নরওয়ে যাবে। ওখানে তুমি বলশেভিকদের প্রতিনিধি হবে। তোমার ছেলেমেয়েরাও ওখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। তারপর তুমি যদি নরওয়ে থেকে রাশিয়া যেতে পারো, তাহলে খুবই ভালো হয়। আমি তোমাকে নকল পাসপোর্ট করে দেব। কী বলো ?
ইতি,
ইলিচ
ইনেসা চিঠির জবাবে বলল, ঠিক আছে। তুমি পাসপোর্ট বানাও। আমি তারপর সিদ্ধান্ত নেব।
কিন্তু চারদিকে কড়াকড়ি, অনেক চেষ্টা করেও এবার নকল পাসপোর্ট করা গেল না।
লেনিন ইনেসাকে আবার চিঠি লিখে বলল—
ইনেসা,
তুমি এক কাজ করো, নাদিয়ার পাসপোর্ট নিয়ে রাশিয়া যাও, টাকা যা লাগে, আমি পাঠাচ্ছি।
কিন্তু ইনেসা শেষ পর্যন্ত রাজি হলো না। লেনিন তখন বলল, তাহলে তুমি সুইজারল্যান্ডে বলশেভিকদের অফিসিয়াল পাবলিকেশনে সাহায্য করো।
ইনেসা তাতেও রাজি হলো না। কারণ সব সময় দেখা যায় গায়ে খাটার কাজগুলো ওকে করতে হচ্ছে আর লেখালেখি করছে লেনিন। ইনেসা এখন নিজে লেখালেখির পেছনে সময় দিতে চাচ্ছে। লেনিনের মতো সেও চায় বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃতি।
ইদানীং লেনিন যা বলে তাতেই ইনেসা গাইগুই করে। তারপরও লেনিন ইনেসার খোঁজখবর নিতে ভুলছে না। সেদিন লেনিন লিখল,
ইনেসা,
আর সরেনবার্গে থেকো না। এত ঠান্ডা ওখানে, তুমি শীতে জমে যাবে। অনেকদিন তোমার সাথে দেখা হয় না। ইচ্ছে করছে তোমার মুখোমুখি বসে দুটো কথা কই আর তোমার হাত দুটো আমার হাতে চেপে ধরি। তুমি সেদিন লিখেছ ঠান্ডায় তোমার হাত-পা ফুলে গেছে। কী একটা ভয়াবহ অবস্থা! নিজেকে এভাবে শাস্তি দিচ্ছ কেন ? সরেনবার্গে যদি থাকতেই হয় অন্তত মনমরা হয়ে থেকো না। তুমি তো স্কি করতে পারো! জানো তো শীতকালে সরেনবার্গের পাহাড়ে স্কি করার সময় রাশিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়।
ইতি
ইলিচ
১৭ ডিসেম্বর লেনিন আবার লিখল।
ইনেসা,
তোমার শেষ চিঠিটা এত বিষাদমাখা! পড়ে আমার খুব মন খারাপ লাগল, থ হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। প্লিজ, একটা অজপাড়াগাঁয়ের প্রবল শীতে আর নিঃসঙ্গতায় নিজেকে নিঃস্ব করে ফেলো না। এরপর যখন বাড়ি ঠিক করবে, আমি আসতে পারব কি পারব না, প্লিজ সেটা বিবেচনায় এনো না। আমার কথা ভুলে নিজের যত্ন নাও। যেখানে তোমার সবচেয়ে সুবিধা হয়, সেখানে বাড়ি নাও।
ইনেসার লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইচ্ছে দিনদিন বেড়েই চলেছে। সমাজতান্ত্রিক মহলে লেখকদের সবাই সম্মান করে। ইনেসা এই সম্মানটা চাচ্ছে। কিছুদিন আগে সোশাল ডেমোক্রেট পত্রিকায় ইনেসা একটা লেখা পাঠিয়েছিল। লেখাটার শিরোনাম ছিল, যুদ্ধের আসল খরচ কারা বহন করে ? ওরা লেখাটা প্রত্যাখ্যান করেছে। ইনেসা লেনিনকে জিগ্যেস করল, লেনিন, তোমাদের পত্রিকায় আমার লেখা রিজেক্ট হলো কেন ? তুমি কি লেখাটা আটকেছো ?
লেনিন বলল, তোমার লেখা আমি কেন আটকাব ? আমার কী লাভ ? আমার নিজের আর্থিক অবস্থাই এখন শোচনীয়। আমি কম ভাড়ার একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজছি। আমার মনে হয়, কোনো অনিবার্য কারণে ওরা তোমার লেখাটা এখনো ছাপে নি। হয়তো পরে ছাপবে।
লেনিনের আর্থিক অবস্থা আসলেই খুব খারাপ। লেনিন আর নাদিয়া জুরিখের স্পিগেলগাসের একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করেছে। বাড়িটা খুব সরু পাথুরে পথের পাশে আরও অনেকগুলো তিনতলা বাড়ির লাগোয়া। সব সময় বাইরে থেকে সসেজ ফ্যাক্টরির গন্ধ ভেসে আসে। বাধ্য হয়ে ওদের ঘরের জানালা বন্ধ করে রাখতে হয়। ঘরে কোনো হিটিংয়ের ব্যবস্থা নাই। রান্নাঘর বাড়ির মালিকের সাথে ভাগ করে নিতে হয়। টাকার অভাবে খাবার কেনা অনেকটা দুঃসাধ্য হয়ে গেছে। প্রায় দুপুরেই ওরা ওটমিল খেয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। লেনিন এখন হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছে। লেনিন সেদিন ওর দুলাভাইকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছে, দেখো তো আমাকে অনুবাদকের কোনো কাজ জুটিয়ে দিরে পারো নাকি ?
আরেকদিন ওর বন্ধু শ্লিয়াপনিকভকে লিখেছে, নাদিয়া আর আমার এখন যে অবস্থা তাতে ক’দিন বাদে না খেয়ে মারা যাব।
তার উপর একটার পর একটা বিপদ আর দুঃসংবাদ লেগেই আছে। জুলাই মাসে লেনিনের মা মারা গেছে। লেনিনের বোন আনাকে গ্রেপ্তার করে আস্ত্রাখানে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য অসুস্থার জন্য আনা শর্ত সাপেক্ষে ছাড়া পেয়েছে। এদিকে ইনেসা জানিয়েছে, সে প্রবল বিষণ্নতায় ভুগছে। কোথাও যেন কোনো আলোর রেখা নেই। লেনিন কারও জন্য কিছুই করতে পারছে না।
লেনিনের দিকে তাকিয়ে নাদিয়ার কখনো কখনো করুণা বোধ হয়, কখনো মন খারাপ লাগে। মনে পড়ে একবার ওরা লন্ডনের চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল। ওখানে একটা সাদা নেকড়ে ছিল। চিড়িয়াখানার লোকটা বলল, কত জীবজন্তু এনে আমরা খাঁচায় ভরি। প্রথমে সবাই তড়পায় কিন্তু আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে। শুধু রাশিয়ার উত্তর থেকে আনা এই সাদা নেকড়ে কখনো খাঁচার জীবন মেনে নেয় না, দিনরাত খাঁচার প্রাচীরে মাথা ঠোকে। লেনিনকে দেখে নাদিয়ার মনে হয়, সে উত্তর রাশিয়ার সাদা নেকড়ে, কোনো কিছুই মেনে নিতে পারছে না।
ইদানীং লেনিনের সবার সঙ্গে সহজেই ঝগড়া বেঁধে যাচ্ছে। জিনভিয়েভ, রোজা লুক্সেম্বার্গ, বুখারিন কেউই লেনিনের শিশুসুলভ চিৎকার চেঁচামেচির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। রাগারাগি করতে করতে লেনিনের মাথাব্যথা হয়ে যায়, মুখ ফুলে যায়, তারপরও সে শান্ত হয় না। বিশেষ করে ইনেসা লেনিনের সঙ্গে একের পর এক তর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো ইনেসার রাগের পেছনে লুকিয়ে থাকে প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকার হাহাকার মাখা আক্রোশ। লেনিনের চিঠির জবাব সে ইচ্ছে করেই দেরিতে দেয়। একধরনের জোর করে অবহেলা দেখাবার এই প্রয়াস আসলে কাজে দেয়, লেনিন ধৈর্যহারা হয়ে ওঠে। তবু লেনিন সেদিন ধৈর্য দেখিয়ে লিখল,
প্রিয় ইনেসা,
আমার অনেক চিঠির উত্তর তুমি দাও না। হয়তো আমার প্রতি তোমার মনোভাব বদলে গেছে। হয়তো তোমার নিজের জীবনযাত্রাই বদলে গেছে। কী থেকে যে কী ভাবব আমি বুঝতে পারি না। আমি কি তোমাকে কোনোভাবে আহত করেছি ? নাকি বাড়ি বদল নিয়ে তুমি বেশি ব্যস্ত ছিলে ? নাকি অন্যকিছু ? এর বেশি জিজ্ঞেস করতেও ভয় পাই। এসব প্রশ্ন তোমার মেজাজ হয়তো আরও বিগড়ে দেবে।
ইনেসার ক্রমাগত অবহেলায় লেনিন কখনো কখনো দিশাহারা হয়ে যায়। সেদিন বিরক্ত হয়ে লেনিন ইনেসাকে লিখল,
তোমার কাছে শুধু জানতে চেয়েছি ফরাসি অনুবাদটা হয়েছে কি না। তাতেই এত ক্ষেপে গেলে ? এতে রাগের কী আছে ? আজব ঘটনা! তারচেয়ে ভয়ংকর হলো, রেগে গিয়ে তুমি একদম চুপ মেরে বসে থাকো, কোনো সাড়াশব্দই পাওয়া যায় না। অদ্ভুত!
লেনিন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না যে ওদের দুজনের সম্পর্কের সমীকরণ এবং ভারসাম্য পাল্টে যাচ্ছে। লেনিন একা বাণী দেবে আর ইনেসা গভীর মনোযোগ দিয়ে তা আত্মস্থ করবে, সেই অবস্থা এখন নেই। ইনেসা সমাজ এবং রাজনীতি নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করছে। ধীরে ধীরে ওর নিজস্ব কণ্ঠস্বর তৈরি হচ্ছে। লেনিন যখন ওকে লেখা অনুবাদ করবার জন্য পাঠায়, ইনেসা মাঝেমাঝে লেনিনের কোনো কোনো যুক্তি কিংবা বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে। লেনিন কখনো সেগুলো মেনে নেয়, কখনো মানে না। মাঝেমাঝে লেনিনের দু একটা বাক্য পড়ে ইনেসা ক্ষেপে গিয়ে লিখে, আমি এই অংশটা অনুবাদ করব না। লেনিন জবাবে লেখে, তুমি অনুবাদ না করলে আমার কিছু করার নেই, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন আমার বাক্যটা সেন্সর করলে। দিনদিন ইনেসা আহত বাঘিনীর মতো লেনিনকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোকাবেলা করছে। ইনেসার তর্কে যুক্তি আছে, তাই ওগুলো সহজেই পাশ কাটানো যাচ্ছে না। এই যুক্তিতর্কের আড়ালে ইনেসার অভিমানী অবাধ্যতা লেনিনকে পীড়া দিচ্ছে। কিন্তু লেনিন জানে ইনেসাকে বারবার দুঃখ দিয়ে সে-ই এমন আচরণ উস্কে দিয়েছে।
১১
মাসখানেক হলো অ্যাগনেস টের পেয়েছে ও গর্ভবতী। ওর সব রাগ, ক্ষোভ আর ঘৃণা এখন আর্নেস্টের ওপর। আর্নেস্টকে অ্যাগনেস অনেকবার বলেছে, আমি কোনো ছেলেমেয়ে চাই না। অথচ আর্নেস্ট মোটেও সাবধান হয় নি। অ্যাগনেসের অনীহা উপেক্ষা করে আর্নেস্ট প্রায় প্রতি রাতেই ওর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।
বাচ্চা হওয়ার ভয়ে অ্যাগনেসের আচরণ দিনদিন উদ্ভট থেকে উদ্ভটতর হয়ে যাচ্ছে। অ্যাগনেস ক্রমশ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার অবস্থা।
সেদিন অ্যাগনেসের বাড়িওয়ালী সোফি সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাচ্ছিল। হঠাৎ পা পিছলে গেল। নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়ে সোফি সিঁড়ির দিকে তাকাল। অ্যাগনেসের ফ্ল্যাটের দরজা দিয়ে বাইরে পানি গড়িয়ে আসছে। আর সেই পানিতেই ওর পা পিছলে গিয়েছিল। অ্যাগনেসের বাড়ির ভেতর থেকে মনে হলো হেঁচকির মতো আওয়াজ ভেসে এল। সোফি অ্যাগনেসের দরজায় কড়া নাড়ল। কিন্তু কেউ দরজা খুলল না। অ্যাগনেস কি অসুস্থ ? খারাপ কিছু হয় নি তো ?
সোফি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। আশেপাশের লোক জড়ো করে বাড়িতে নিয়ে এল। ওরা দরজা ভেঙে অ্যাগনেসের ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকল। একজন জলের ধারা লক্ষ করে বলল, পানি তো আসছে বাথরুম থেকে। ওরা বাথরুমে গিয়ে দেখল অ্যাগনেস বাথটাবের জলে তলিয়ে যাচ্ছে। ওরা তাড়াতাড়ি অ্যাগনেসকে বাথটাব থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে এল। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝল, অ্যাগনেস বিষ গিলেছে। খবরটা আর্নেস্টের কানে পৌঁছুতেই ও হাসপাতালে ছুটে এল। অ্যাগনেস তখনো ঠিকমতো কথা বলতে পারছে না। আর্নেস্ট ওর হাত ধরে বসে রইল।
সেই রাতটা অ্যাগনেসকে হাসপাতালেই কাটাতে হলো। পরদিন বাড়ি ফেরার পর আর্নেস্ট অ্যাগনেসের মুখোমুখি বসে বলল, আমি কী ভুল করলাম যে তুমি এমন করলে ?
অ্যাগনেস বলল, তুমি ভালো করেই জানো আমি বাচ্চা নিতে চাই না।
কিন্তু কেন ? বিয়ে করলে ছেলেমেয়ে হবে সেটাই তো স্বাভাবিক।
তোমাকে তো আগেও বলেছি, ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার ট্রমা আছে। বাচ্চা নিলে আমি বদ্ধ পাগল হয়ে যাব।
আর্নেস্ট অ্যাগনেসের কথায় আহত হলো। কিন্তু আর্নেস্টেরও এই মুহূর্তে কিছু করার নেই। তর্ক করলেই অ্যাগনেস আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করবে। আর্নেস্ট বলল, তাহলে এখন তুমি কী চাও ?
আমি আবর্ট করতে চাই।
অ্যাবরশন এ দেশে অবৈধ। আর্নেস্ট অনেক খুঁজে একজন ডাক্তারকে জোগাড় করল। সেই ডাক্তার অনেক টাকা নিয়ে গোপনে অ্যাগনেসের গর্ভপাত ঘটাল। শারীরিক-মানসিক ধকল কাটিয়ে উঠতে অ্যাগনেসের বেশ অনেকদিন লেগে গেল। সুস্থ হওয়ার পর অ্যাগনেস একদিন আর্নেস্টকে বলল, আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো। কিন্তু আমি তোমার সাথে এক বাড়িতে থাকতে পারব না।
আর্নেস্ট অবাক হয়ে বলল, কেন ? এখন আবার কী হলো ?
আমরা একসঙ্গে থাকলে আজ হোক কাল হোক আবার একই অবস্থা হবে। আমি প্রেগন্যান্ট হয়ে যাব।
অ্যাগনেস শহরের অন্যপ্রান্তে বাসা ভাড়া করল। আর্নেস্টের মন খারাপ দেখে বলল, তুমি চাইলে মাঝেমাঝে এসে দেখা করতে পারো।
কিন্তু এতেও অ্যাগনেস শান্তি পাচ্ছে না। এ শহর থেকেই ওর মন উঠে গেছে। অ্যাগনেস অন্য অনেক শহরে চাকুরির আবেদন করছে। অনেক অ্যাপলিকেশন জমা দেওয়ার পর স্যান ডিয়োগো নর্মাল কলেজে ফ্যাকাল্টি সেক্রেটারির চাকুরির অফার এসেছে। অ্যাগনেস এ সুযোগ হাতছাড়া করল না। বেশ তাড়াহুড়া করেই সান ডিয়েগো চলে এল। স্যান ডিয়েগো নর্মাল স্কুলের কাছেই লজিং নিল।
আর্নেস্ট অ্যাগনেসকে বাধা দেয় নি। জানে দিলেও কোনো লাভ হতো না। চাকুরিতে একটু থিতু হওয়ার পর অ্যাগনেসের ইচ্ছে হয়েছে ওই কাজের পাশাপাশি স্যান ডিয়েগো নর্মাল কলেজে পড়বে। কিন্তু ভর্তির টাকা নেই। অ্যাগনেস টাকা চেয়ে আর্নেস্টকে চিঠি লিখেছে। আর্নেস্ট কোনো আপত্তি করে নি। সঙ্গেসঙ্গেই টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। অ্যাগনেস টিচার্স ট্রেনিংয়ে পোস্ট হাইস্কুল ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়েছে।
কলেজে ভর্তি হওয়ার পর অ্যাগনেসের মাঝে যেন হারানো উদ্যম আর চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। অ্যাগনেসের গুণের কমতি নেই। ও এখন স্টুডেন্ট ম্যাগাজিন ছাপাচ্ছে। কোত্থেকে একটা ক্যামেরাও জোগাড় করেছে। সেটা দিয়ে দেদারছে ছবি তুলছে। ও ভালো গাইতে পারে, নাচতে জানে, আপেলের বিচি দিয়ে ভাগ্য গণনা করতে পারে, আবার ‘মারচেন্ট অফ ভেনিস’ নাটকটিও সে কদিন আগে থিয়েটারে নামিয়েছে। ক্যাম্পাসে অ্যাগনেস এখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। বুদ্ধি আর হাসির ছটায় ক্যাম্পাসের সবাইকে ও মাতিয়ে রাখছে।
কিন্তু কিছুদিন বাদেই হরদয়ালের গদর পার্টিতে আবার ওর ডাক পড়ল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হরদয়ালের নামে হুলিয়া জারি হয়েছে। গ্রেপ্তার এড়াতে হরদয়াল আমেরিকা থেকে পালিয়ে সুইজারল্যান্ডে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সুজারল্যান্ডে বেশি দিন থাকে নি। সেখান থেকে জার্মানি চলে এসেছে। গদর পার্টির বিপ্লবীরা দলে দলে আমেরিকা থেকে জাহাজে ভারত চলে যাচ্ছে। ওদের ধারণা ভারত স্বাধীন করার এটাই উপযুক্ত সময়। এই বিপ্লবীদের কেউ কেউ ধনী ঘরের, কিন্তু বেশির ভাগই শ্রমিক শ্রেণির, অশিক্ষিত এবং দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে। এদের কারও মাঝেই মৃত্যুভয় নেই। ওদের অদম্য স্পৃহা অ্যাগনেসকে ভীষণ নাড়া দিচ্ছে। ওদের দেখেই অ্যাগনেস আবার গদর আন্দোলনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। এভাবে জড়ালে লেখাপড়া শেষ হবে কিনা কে জানে!
হরদয়াল চলে যাওয়ার পর ভগবান সিং, রামচন্দ্র এবং মৌলভী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ গদর পার্টির নেতৃত্বে চলে এসেছে। কিন্তু আমেরিকায় নানা ঝামেলায় ফেঁসে মৌলভী বরকতুল্লাহও ইউরোপে চলে গেছে। কিছুদিন পর খবর এল, বরকুতুল্লাহ এখন প্রবাসী ভারতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী। ওর ওপর নানা দেশের গোয়েন্দাদের কড়া নজর।
অ্যাগনেসের চাকুরিতে দায়িত্ব বেড়েছে। ও এখন স্যান ডিয়েগো কলেজের কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে স্টেনোগ্রাফি আর টাইপিং শেখায়। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে লুকিয়ে রাখার জন্য এটা খুব ভালো আড়াল। কিন্তু আড়াল রেখেও সুবিধা করা যাচ্ছে না। ব্রিটিশরা গদর আন্দোলন দমন করার জন্য দেশে-বিদেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওদের চোখ এড়িয়ে চলা মুশকিল।
ব্রিটিশদের দুর্বল করবার জন্য জার্মানরা ভারতের স্বাধীনতার আগুনে ইন্ধন জোগাচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য বার্লিনে ইন্ডিয়া কমিটি বানানো হয়েছে। স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য জার্মান সরকার দু শ’ পঞ্চাশ হাজার ডলার বরাদ্দ করেছে। আমেরিকা এখনো যুদ্ধে নিরপেক্ষ। এ কারণে বার্লিনের পাশাপাশি আমেরিকাকেও স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে বিপ্লবীরা। যুদ্ধের সুযোগে প্রচুর অস্ত্রসহ বিপ্লবীদের ভারতে পাঠানো হচ্ছে। পেছন থেকে এর তত্ত্বাবধানে আছে জার্মানরা। এ রকম একটা অস্ত্রভরা জাহাজের আঞ্জাম করতে নরেন পেনাং গিয়েছিল, আর বাঘা যতিন বালাসরে নিহত হয়েছিল।
সানফ্রানসিসকো বে এরিয়া গদর বিপ্লবীদের গোপন তৎপরতার মূল কেন্দ্র। স্যান ডিয়াগো এলাকায়ও কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে। গদর পার্টির হয়ে অ্যাগনেসের দায়িত্ব হলো, পার্টির গোপন চিঠি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আনা-নেওয়া করা। গোপন নথি আর অস্ত্র নিরাপদে রাখার জন্য সেইফ ডিপোজিট বক্স ভাড়া করাটাও অ্যাগনেসের কাজ। কারণ শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কাজ করবে, সেই সন্দেহ এখনো ব্রিটিশ আর আমেরিকান গোয়েন্দাদের মনে জোরদার হয় নি। জার্মান টাকা বিভিন্ন জায়গায় বিতরণের জন্য আরও সাদা চামড়ার এজেন্ট প্রয়োজন। এদেরও অ্যাগনেস খুঁজে বের করছে। ভারতীয় আর শ্বেতাঙ্গ মিলেমিশে গদর পার্টির বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পালে ভালো হাওয়াই লাগিয়েছে।






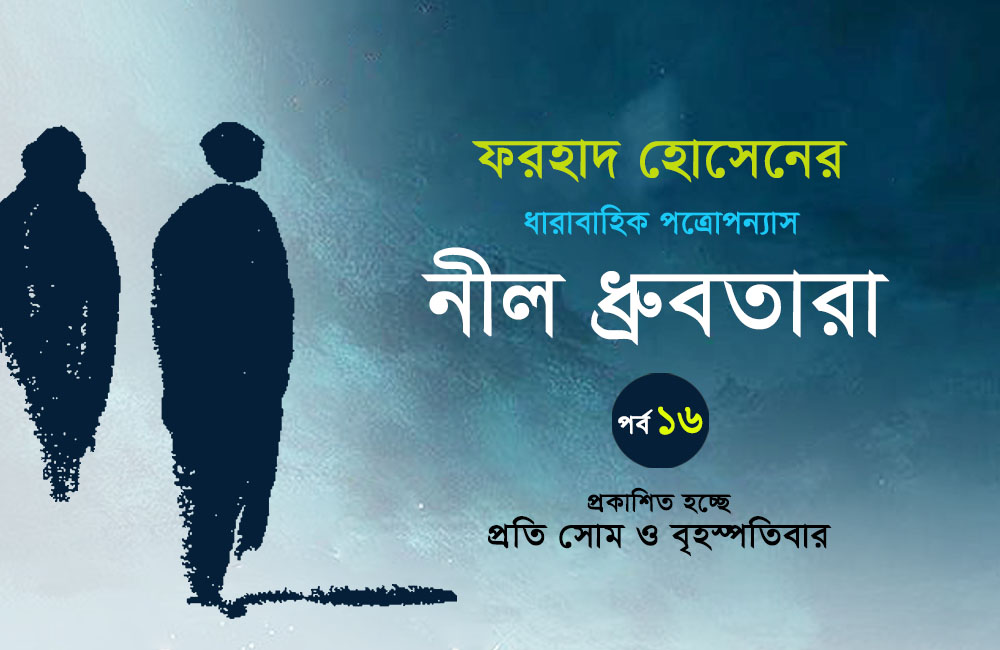


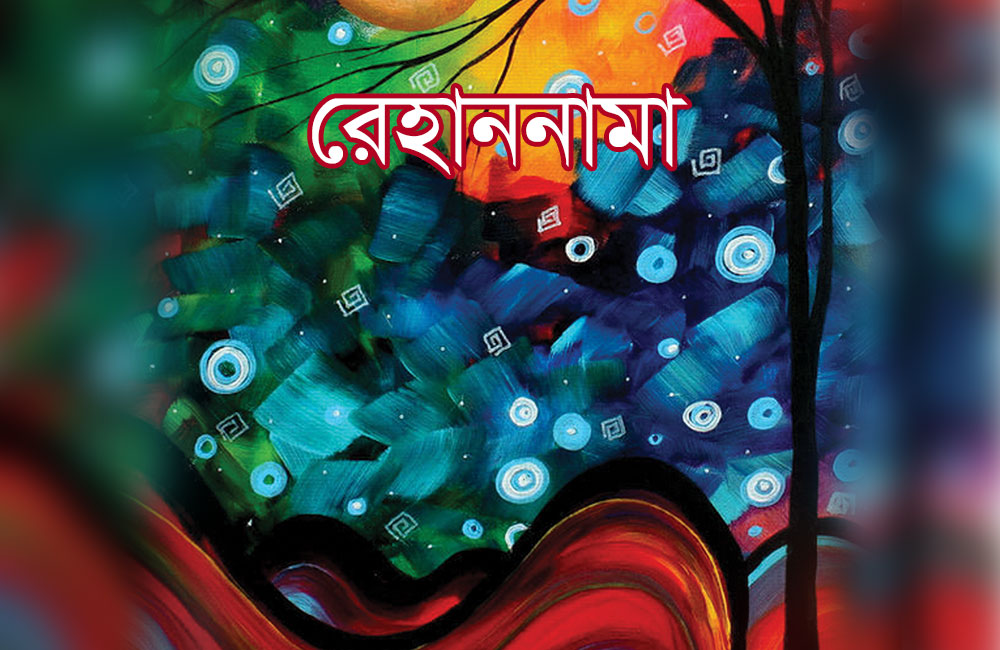





Leave a Reply
Your identity will not be published.