[বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীও রয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য ভুবন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধÑসব ধরনের রচনাতেই নারীরা সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। এমনকি সংস্কৃতিতেও। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সেইসব স্মরণীয় নারী এবং তাঁদের কীর্তির কথাই এই ধারাবাহিক রচনায় তুলে ধরা হয়েছে।]
৭১) রানী রাসমণি (১৭৯৩-১৮৬১) : চব্বিশ পরগনার অধীনে কোণা গ্রামের হরেকৃষ্ণ দাসের অপরূপ সুন্দরী ও বহু গুণে গুণান্বিতা কন্যা রাসমনি। কলকাতার বিখ্যাত ধনী রাজচন্দ্র মাড়ের স্ত্রী। ১৮৩৬ সালে স্বামী রাজচন্দ্রের মৃত্যু হলে রানী রাশমনি বিপুল ধন-দৌলতের মালিক হন, কিন্তু তিনি নিজেই অগাধে বিত্ত বৈভব ভোগ না করে দান ধ্যান আর ধর্মেকর্মে তা খরচ করেন। দক্ষিণেশ্বর-এর বিখাত কালী মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী এই নারী রাজছত্রের অধিকারী ইংরেজদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সরব প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জেলেদের স্বার্থ রক্ষার্থে তিনি গঙ্গা নদী ইজারা নিয়ে বিদেশি বণিকদের গঙ্গানদীতে স্টিমার চালানো বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন। রানী রাশমনি এত রকম গুণাবলির জন্যে ইত্নি লোকমাতা বলে আখ্যায়িত ছিলেন। কথিত আছে রানী রাশমনি ও তাঁর নায়েব মোহন ঘটক নীল চাষকে কেন্দ্র করে প্রজাদের ওপর অমানবিক অত্যাচারের কথা শুনে হোসেনপুরের অদূরে যে নীলকুঠী ছিল, মিলিত শক্তি নিয়ে তারা রাতারাতি সেই কুঠী ভেঙে দিয়ে সারা রাত ধরে কলাগাছ রোপণ করেন। সেই থেকে ওই জায়গাটির নাম হলো কলারোয়া।
৭২) রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০) : বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’-এর লেখক রাসসুন্দরী দেবী। পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। বারো বছর বয়সে ফরিদপুর জেলার রাদিয়া গ্রামের জমিদার সীতানাথ সরকারের সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের সময় রাসসুন্দরী নিরক্ষর ছিলেন। কেননা সেকালে মেয়েদের লেখাপড়ার কোনো সুযোগ ছিল না। রাসসুন্দরী নিজের চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে, সংসারের সমস্ত ভার বহন করেও পড়তে ও লিখতে শেখেন। আঠারো বছর থেকে একচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বারো সন্তানের জননী হয়ে সন্তানদের লালনপালন করে, গৃহস্থালির সকল কর্তব্য সমাপন করে এই সবকিছুর-ই ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যচর্চা করেন। স্বশিক্ষিত রাসসুন্দরী এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত মনোগ্রাহী ভঙ্গিতে বিষদভাবে বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে তাঁর রচিত কবিতা ও সংগীত-ও স্থান পেয়েছে। ১৮৬৮ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর বছরেই ‘আমার জীবন’ প্রথম প্রকাশিত হয়। রাসসুন্দরীর বয়স তখন ঊনষাট। দীর্ঘ জীবনের অধিকারী রাসসুন্দরীর বয়স যখন ৮৮, তখনো নিজের হাতে তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সংশোধন করে দেন তিনি। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রাসসুন্দরী দেবী শুধু বাঙালি নারীর ইতিহাসেই নয়, সমগ্র বাঙালির ইতিহাসেও এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।
৭৩) রাশমণি হাজং (১৮৯৮-১৯৪৬) : টংক কৃষক বিদ্রোহের অসীম সাহসী, বীরযোদ্ধা নেত্রী রাশমণি হাজং। তিনি ১৮৯৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় বেদীকুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জমিদার ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কৃষক ও মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে ৩১ জানুয়ারি কুমুদিনী হাজংকে বাঁচাতে গিয়ে মুখোমুখি সংগ্রামে লিপ্ত হন। এটা ছিল ১৯৪৬-৫০ সালে নেত্রকোনা অঞ্চলের কৃষকদের পরিচালিত একটি আন্দোলন। টংক প্রথা হলো উৎপন্ন ফসল দ্বারা জমিদারদের খাজনা পরিশোধ করা। যেটা টাকায় খাজনা পরিশোধের চেয়ে বেশি ছিল। হাজং সম্প্রদায় এ ব্যবস্থায় দিনে দিনে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এ সময় সুসং দুর্গাপুরের জমিদারদের ভাগ্নে কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মনি সিংহ-এর নেতৃত্বে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে টংক প্রথা উচ্ছেদ, টংক জমির খাজনা স্বত্ব, জোত স্বত্ব, নিরিখ মতো টংক জমির খাজনা ধার্য, বকেয়া টংক মওকুফ, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ইত্যাদি দাবি নিয়ে টংক আন্দোলন শুরু হয়। হাজং সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থেই টংক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। সে সূত্রেই কুমুদিনী হাজং-এর স্বামী লংকেশ্বর হাজং ও তাঁর তিন ভাই টংক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য জমিদার ও ব্রিটিশ পুলিশ দমন-নিপীড়ন চালাতে থাকে। ১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারি সকাল ১০টার দিকে বিরিশিরি থেকে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বহেরাতলী গ্রামে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর একটি দল লংকেশ্বর হাজং-এর বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু তাদের না পেয়ে অষ্টাদশী গৃহবধূ কুমুদিনী হাজংকে বন্দি করে বিরিশিরিতে নিয়ে যেতে থাকে। এদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে রাশিমনি হাজং-এর নেতৃত্বে হাজার হাজার হাজং নারী-পুরুষ ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীকে ঘিরে ফেলে ও কুমুদিনী হাজংকে ছেড়ে দিতে বলে। ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর সেনারা হাজং গ্রামবাসীর কথায় কর্ণপাত না করে বিরিশিরির দিকে যেতে থাকে। রাশমণি হাজং কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে কুমুদিনী হাজংকে ছাড়িয়ে নিতে গেলে সশস্ত্র সেনারা নৃশংসভাবে তাঁদের ওপর গুলি চালায়। এতে রাশমণি হাজং গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে পেছনের পুরুষ দলের নেতা সুরেন্দ্র হাজং রাশমণিকে ধরতে গেলে তাঁকেও নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় অন্যান্য হাজং নারী-পুরুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সশস্ত্র সেনাদের উপর বল্লম ও রামদা দিয়ে হামলা চালায়। তাঁদের হামলায় ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর দু’সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। বাকি সেনারা দৌড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। টংক বিদ্রোহের প্রথম শহীদ রাশমণি হাজং। নিঃসন্তান হয়েও রাশমণি হাজংদের কাছে আজও হাজং মাতা হিসেবে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার পাত্র। ‘হাজং মাতা রাশমণি স্মৃতিসৌধ’ দুর্গাপুর উপজেলা পরিষদ থেকে ছয় কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কুল্লাগড়া ইউনিয়নের বহেড়াতলী গ্রামে চৌরাস্তার মোড়ে অবস্থিত।
৭৪) লায়লা সামাদ (১৯২৮-১৯৮৯) : ১৯২৮ সালের ৩ এপ্রিল কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পিতা খান বাহাদুর আমিনুল হক ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। মাতার নাম তাহমীনা খাতুন, ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। এসরাজ বাজাতেন। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত ‘আঞ্জুমান’-এ-খাওয়াতীন-এর সদস্য ছিলেন লায়লার মা। ‘সওগাত’-এ তাঁর লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। লায়লা প্রথমে জলপাইগুড়ি মিশনারি স্কুলে এবং পরে কলকাতা’য় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে পড়েন। প্রবেশিকা পাস করার পর তিনি আশুতোষ কলেজ ও ব্রেবোর্ণ কলেজে পড়াশোনা করেন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লায়লা সামাদের পিতা জলপাইগুড়ি’তে বদলি হয়ে যান। সেখানেই লায়লা সামাদের রাজনৈতিক জীবনের শুরু। কলকাতা থাকাকালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মোজাফফর আহমেদসহ অনেক কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। লায়লা সামাদের স্বামী মির্জা সামাদ চাবাগান ও রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নে কাজ করার দায়িত্ব নেন। বিয়ের পর লায়লা সামাদও স্বামীর সঙ্গে এ পার্টিতে একাত্ম হয়ে কাজ করতে থাকেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তিনি দেয়ালে-দেয়ালে নিজ হাতে পোস্টার সেঁটেছেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতির (সভাপতি সুফিয়া কামাল) যুগ্ম-সম্পাদক, নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির জুঁইফুল রায়ের সঙ্গেও কাজ করতেন। সাংবাদিক লায়লা সামাদ চুয়ান্নর ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের সাফল্যের জন্য রাত-দিন পরিশ্রম করেছেন। এসময় লায়লা সামাদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ সরকার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। তিনি শিশুকন্যাসহ কলকাতা’য় পালিয়ে যান। সেখানে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা অনুষদে ভর্তি হন এবং সাংবাদিকতায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর ফলে তিনি পদ্মজা নাইডু’র হাত থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন।
এছাড়া তিনি কলকাতায় তুলসী লাহিড়ী’র ‘ছেঁড়া তার’ নাটকে অভিনয় করে তুমুল আলোড়ন তোলেন এবং পুরস্কৃত হন। সে সময় ঢাকা’র মঞ্চে কোনো মহিলার অভিনয় ছিল অভাবনীয় ঘটনা। পুরুষেরাই সাধারণত নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে এসে তিনি একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দৈনিক ‘সংবাদ’-এর মহিলা বিভাগের সম্পাদনার কাজে নিজেকে জড়িত করেন। তাঁর আগে অন্য কোনো নারী এই দেশের কোনো কাগজে বিভাগীয় সম্পাদক হওয়ার সম্মান লাভ করেন নি। তিনি অধুনালুপ্ত ‘অবজাভার’ গ্রুপের সাপ্তাহিক ‘পূর্বদেশ’-এও কাজ করেন। ডা.ইব্রাহিমের অনুরোধে লায়লা সামাদ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ‘চিত্রিতা’ নামে বিনোদনমূলক একটি পত্রিকার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন তিনি। লায়লা সামাদ ‘চারণিক’ নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। টিভি ও বেতারের নাট্যকার হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সফল। ছোটগল্পের জন্য তিনি ‘বাংলা একাডেমি’ পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি অর্গান বাজিয়ে চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারতেন। খেলাধুলাতেও তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। তিনি সমাজসেবায় ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাশীল। অনেক মেধাবী গরিব ছাত্রকে নিজের খরচে পড়িয়েছেন। তিনি বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন আমন্ত্রিত লেখিকা হিসাবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, প্যারিস, সিঙ্গাপুর, হংকং ও ভারতে সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। তিনি ঢাকা লেডিস ক্লাবের সম্পাদিকা, মহিলা পরিষদ ও কর্মজীবী ক্লাবের সহ-সভানেত্রী, জোন্টা ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন । তাঁর লেখা কয়েকটি বই রয়েছে। সেগুলো হলো ‘দুঃস্বপ্নের অন্ধকার’, ‘কুয়াশার নদী’, ‘অরণ্যে নক্ষত্রের আলো’, ‘বিচিত্রা’, ‘কলরোল’, ‘স্বাক্ষর’, ‘শ্রী শ্রীবিড়ালোত্তম দাস’, ‘কড়চা-৭১’, ‘যুক্তরাষ্ট্রের দিন’ ইত্যাদি ? তিনি একাধারে ছিলেন সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী, নাট্যকার এবং নারী প্রগতি আন্দোলনের পথিকৃৎ। ১৯৭১ সালে লায়লা সামাদ বাংলাদেশের মাটিতে থেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন। এই মহিয়সী নারী সাংবাদিক ১৯৮৯ সালের ৯ আগস্ট ভোর ৪টায় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। লায়লা সামাদ ছিলেন অত্যন্ত সংগ্রামী চিন্তা-চেতনা এবং বিপ্লবের আদর্শে উজ্জীবিত এক ব্যক্তিত্ব।
৭৫) লীলা নাগ (রায়) (১৯০০-১৯৭০) : এক অনন্য বিপ্লবী সাধক নারী। লীলা নাগ একজন বাঙালি সাংবাদিক, জনহিতৈষী এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। লীলা নাগ-এর জন্ম অক্টোবর ২১, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি সাংবাদিক, জনহিতৈষী এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সহকারী ছিলেন।
লীলা নাগ আসামের গোয়ালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর পিতৃ-পরিবার ছিল তৎকালীন সিলেটের অন্যতম সংস্কৃতিমনা ও শিক্ষিত একটি পরিবার। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে লীলা নাগ বিয়ে করেন বিপ্লবী অনিল রায়কে। বিয়ের পর তাঁর নাম হয় লীলা রায়।
তাঁর ছাত্রজীবন শুরু হয় ঢাকার ইডেন স্কুলে। ১৯২১ সালে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। পরীক্ষায় তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ‘পদ্মাবতী স্বর্ণ পদক’ লাভ করেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে এম.এ-তে ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনিই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম.এ ডিগ্রিধারী নারী। তখনকার পরিবেশে সহশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলে লীলা রায়ের মেধা ও আকাক্সক্ষা বিচার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চান্সেলর ড. হার্টস তাঁকে পড়ার বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন। লীলা নাগ ঢাকা কলেজে পড়তেন। তাঁর এক ক্লাস উপরের ছাত্র ছিলেন সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন। লীলা নাগ সম্পর্কে তিনি তাঁর স্মৃতিকথা নামক প্রবন্ধ সংকলনে লেখেন, এঁর মতো সমাজ-সেবিকা ও মর্যাদাময়ী নারী আর দেখি নাই। এঁর থিওরি হলো, নারীদেরও উপার্জনশীলা হতে হবে, নইলে কখনো তারা পুরুষের কাছে মর্যাদা পাবে না। তাই তিনি মেয়েদের রুমাল, টেবলক্লথ প্রভৃতির ওপর সুন্দর নকশা এঁকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসব বিক্রি করে তিনি মেয়েদের একটা উপার্জনের পন্থা উন্মুক্ত করে দেন।” বাঙালি নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ঢাকার আরমানীটোলা বালিকা বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল এবং শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয় (তৎকালীন নারীশিক্ষা মন্দির) প্রতিষ্ঠা করেন। বিয়ের পর তাঁর নাম হয় শ্রীমতি লীলাবতী রায়। ভারত বিভাগের পর লীলা নাগ কলকাতায় চলে যান এবং সেখানেও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯২৩ সালে লীলা রায় ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাস করেন। পরীক্ষা পাসের পর বাংলার নারী সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন অভিশপ্ত জীবনে জ্ঞানের আলো বিকিরণের উদ্দেশ্যে ১২ জন সাথি নিয়ে গড়ে তোলেন ‘দীপালি সংঘ’।
মেয়েদের প্রতি অন্যায়-অবিচার, অসম্মানের বিরুদ্ধে তাঁর চিরদ্রোহী মন ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবে প্রসারিত হয় মাতৃভূমির পরাধীনতার পুঞ্জীভূত অবমাননা ও বেদনার অবসান সংকল্পে।
১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেস ও বাংলার বিপ্লবী দলগুলো সুভাষচন্দ্রের চারপাশে সমবেত হতে থাকে। সহকর্মীদের সঙ্গে অনিল রায় ও লীলা নাগ সেখানে উপস্থিত হন। লীলানাগ তখনো বিপ্লবী দলের নেপথ্যে। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস উপস্থাপনের সময় লীলা মঞ্চে উঠেন। বিপ্লবী দলে যোগদানের পথ এরই মধ্য দিয়ে প্রশস্ত হয়।
এর কয়েক বছরের মধ্যে দীপালি সংঘের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। দলে দলে মেয়েরা এর পতাকা তলে সমবেত হতে থাকে। বিপ্লবী নেত্রী লীলা নাগের কাছে দলের ছেলেরাও আসেন নানা আলোচনার উন্মুখতা নিয়ে। নেত্রী হিসেবে তাঁর সঙ্গে গণআন্দোলনের সম্পর্ক ছিল। দীপালি সংঘ ছাড়াও তিনি যুক্ত ছিলেন অনিল রায়ের শ্রীসংঘের সঙ্গে। শ্রীসংঘে যোগদানের পর বিপ্লবী আন্দোলনেও তিনি অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে যান প্রথম সারিতে। ১৯৩০ সালে বাংলার সব বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয়দের ইংরেজ সরকার একযোগে গ্রেপ্তার শুরু করলে অনিল রায় ও তাঁর সহকর্মীরাও গ্রেপ্তার হন। তখন শ্রীসংঘের সর্বময় নেতৃত্বের দায়িত্ব লীলা নাগের কাঁধে বর্তায়। শ্রীসংঘের সদস্যরা সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালনা করার জন্য অস্ত্রসংগ্রহ ও বোমা তৈরি করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলার জন্য লীলা নাগ ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের ইন্দুমতি সিংহকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে দেন। সূর্য সেনের পরামর্শে প্রথম নারী বিপ্লবী শহীদ প্রীতিলতা দীপালি সংঘের সদস্য হয়ে বিপ্লবী জীবনের পাঠ নিয়েছিলেন লীলা নাগের কাছে। ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর দুর্ধর্ষ রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের পর বিপ্লবীদের কার্যকলাপ আরও জোরদার হয়। ১৯৩১ সালের এপ্রিলে এই দলের সদস্যদের গুলিতে পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং আলিপুরের জেলা জজ গার্লিক ও কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স নিহত হন। ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে দুজন তরুণী জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর দীপালির প্রদর্শনীর কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পর লীলা নাগকে গ্রেপ্তার করা হয়। লীলা নাগ ভারতবর্ষে বিনা বিচারে আটক প্রথম নারী রাজবন্দি। লীলা নাগের গ্রেপ্তারের পর তাঁর অনেক নারী সহকর্মী গ্রেপ্তার ও বন্দি হন। কেউ বা বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। জেলে গিয়ে লীলা নাগ দলীয় কর্মীদের দলের সাংগঠনিক সংহতিকে বৈপ্লবিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড করার নির্দেশ দেন। নেত্রীর নির্দেশে এই কাজের দায়িত্ব কাঁধে নেন অনিল দাস। ১৯৩৬-এর সাধারণ নির্বাচনে ঢাকার মহিলা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে তিনি মনোনয়ন পান। কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন নি। তাঁর পরিবর্তে হেমপ্রভা মজুমদার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
১৯৩৭-এর অক্টোবরে লীলা নাগ কারামুক্ত হন। কারামুক্তির আগেই অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে তাঁর গোপন যোগাযোগ হয়। ফলে বাইরের পরিস্থিতি তিনি কিছুটা আঁচ করতে পারেন। ৮ অক্টোবর তাঁর কর্মতৎপরতা আগের মতো শুরু হয়ে যায়। তিনি মহিলা সমাজের মুখপাত্র হিসেবে ‘জয়শ্রী’ নামে একটি পত্রিকা বের করেন। লীলা রায় ছবি আঁকতেন এবং গান ও সেতার বাজাতে জানতেন। ১৯৬৬ সাল থেকে লীলা নাগের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে পি.জি. (বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ২৩ দিন পর সংজ্ঞা ফিরে এলেও বাকশক্তি ফিরে আসে না। ডানদিক সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। ৪ আগস্ট শেষ সেরিব্রাল আক্রমণে তাঁর সংজ্ঞা লোপ পায়। আড়াই বছর সংজ্ঞাহীন থাকার পর ১৯৭০ সালের ১১ জুন ভারতে এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।
৭৬) লীলা মজুমদার রায় (১৯০৮-২০০৭) : কলকাতায় বিশাল আয়োজনে উদ্যাপিত লীলা মজুমদারের মৃত্যুবার্ষিকীতে (২০১৫) শ্রীজাত বলেন, ‘অগণিত কোমল কাহিনির জন্মদাত্রী হয়েও তাঁর জীবন কাঠিন্যে ভরা!’ তিনি আরও বলেন, ‘যে-শিল্পীর কলম থেকে এত পেলব, এত কল্পনাপ্রবণ, এত আদুরে আর এত ফুরফুরে সমস্ত লেখা বেরিয়েছে, তাঁর ভেতরকার ভিতটা যে এইরকম পোক্ত আর অনড় হতে পারে, অনেক সময়েই তা আমরা ভেবে উঠতে পারি না। তাঁর অন্তঃকরণের সমস্তটুকুকে তাঁর সৃষ্টি দিয়েই মাপতে চাই।’ প্রসঙ্গটা আসে লীলা মজুমদারের সঙ্গে তাঁর পিতার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে। সমস্ত ঘটনাটি শুনলে মনে হয় শরৎচন্দ্রের কোনো নাটকের গল্প। বাড়িতে আসা-যাওয়া করা তরুণ ডাক্তার সুধীন কুমার মজুমদারের গভীর প্রেমে পড়েন তখনকার দিনের অসামান্য আকর্ষণীয়া তরুণী লীলা রায়। প্রেমটা উভয়পাক্ষিক। কিন্তু প্রচণ্ড দাম্ভিক ব্রাহ্মপিতা প্রমদারঞ্জন রায় (উপেন্দ্রকিশোর রায়ের সহোদর) কিছুতেই কন্যাকে হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। সমঝোতা করার মেয়ে লীলা রায় নয়। তিনি সুধীনের সঙ্গে ঘর ছাড়লেন। বিয়ে করে ঠিক পর দিনেই পিতার কাছে এসেছিলেন তাঁর রাগ ভাঙাতে, তাঁর আশীর্বাদ নিতে। স্বামীসহ। তাদের ঘরে ঢুকতে দেখেই লীলার পিতা ঘর থেকে চলে গেলেন। লীলা মজুমদারের ভাষায়, ‘শুধু ঘর থেকেই নয়, আমার জীবন থেকেই সরে পড়লেন।’ তারপর আরও আঠারো বছর বেঁচে ছিলেন তাঁর পিতা। কিন্তু তাঁদের আর কখনো পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয় নি। আঠারো বছর পরে যখন তাঁর পিতা মারা যান, তখন কেবল শেষবারের মতো তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন লীলা। তখনকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লীলা বলেন, ‘তিনি চোখ বুজলেন, আমি এতটুকু ব্যক্তিগত অভাব বোধ করি নি। যে অভাব, যে বেদনা ছিল, ওই সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে টের পেলাম।’
এমনই দৃঢ়চেতা ছিলেন লীলা মজুমদার। এটাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নীতিগত কারণে আর আত্মমর্যাদার প্রশ্নে তিনি কখনো কারও সঙ্গে আপোষ করেন নি। কোনো কাজের সঙ্গে নয়, কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও নয়, কোনো ব্যক্তির সঙ্গে নয়, সে ব্যক্তি নিজের পিতা হলেও নয়।
লীলার জীবনের আরেকটা বড় বৈশিষ্ট্য, স্থির হয়ে বা শান্তমনে বেশিদিন কোথাও টিকতে না পারা। কোনো স্থান, পাত্র বা পদ নিয়ে নীতিগত কোনো বিরোধের সম্ভাবনা বা সত্যিকারের মন কষাকষি সৃষ্টি হলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল, অতিপ্রিয় হলেও, বিরোধের উৎস খুঁজে নিয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করা।
শৈশবের শিলং শহরে বাস, সে-শহরের বেড়ে ওঠার দিনগুলো তাঁর পিছু ছাড়ে নি কোনোদিনও। তিনি ছেড়ে এসেছেন সেই শহর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে হয়ে গিয়েছেন কলকাতার, খানিকটা শান্তিনিকেতনেরও বটে। কিন্তু নিয়ত ছুটে চলা দীর্ঘ জীবনে পাহাড়ঘেরা ছোট্ট সাহেবি কেতার শহর শিলং এবং সেই শহরে তাদের বাড়ি বরাবর মনে রেখে দিয়েছেন তিনি।
‘পাহাড়ের ঢালের ওপর বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে কাঁকড় বিছানো পথ দিয়ে নেমে বারান্দায় পৌঁছতে হতো। একহারা লম্বা বাংলো, সামনে টানা বারান্দা, তার কাঠের রেলিং। বাড়ির তিনদিক ঘিরে বৃষ্টির জল যাওয়ার জন্য নালা কাটা। তার ওপর দুটি চ্যাপ্টা পাথর ফেলা। তার ওপর দিয়ে বারান্দায় উঠতে হয়। বারান্দার ছাদ থেকে তারের বেড়ায় অর্কিড ফুল ঝুলত। তাদের তলায় সবুজ কাঠের বাক্সে জেরেনিয়ম ফুল ফুটত। লোকে এমন বাড়ি স্বপ্নে দেখে।’
এই ছিল শিলং-এ লীলা আর তার দাদা-দিদির স্বপ্নের বাড়ি ‘হাইউইন্ডস’। সপরিবারে এই বাড়িতেই কর্মসূত্রে আট বছর (১৯১১-১৯১৯) কাটিয়ে ছিলেন প্রমদারঞ্জন। সেই আট বছরে লীলার মনে দাগ কেটে যায় রূপকথার রাজ্যের একটা নিজস্ব ছক। বাকি জীবন তিনি সেই ছক থেকে নকশা বুনে গিয়েছেন।
এ বাড়ির স্মৃতিকে স্মরণ করে রূপকথার মতো কত গল্প রচনা করেছেন লীলা সারা জীবন! ছোটবেলায় লিখিত সেইসব গল্প পড়তে পড়তে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়তেন বাড়ির অন্য বাসিন্দারা।
শিলং থেকে শৈশবের ফুলে ঘেরা সেই বাড়ির স্বপ্নই শুধু বয়ে বেড়াতেন না লীলা, আরেকজন বড় মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ও ঘটেছিল এখানে এই শিলংয়েই, এক বিকেলে, যাঁর কথা জীবনে বারবার ভেসে উঠেছে, তাঁর স্মৃতিও প্রায় সর্বক্ষণই অনুপ্রেরণা দিত তাকে। যেই অসাধারণ মুহূর্তে দেখা হয়েছিল তাঁর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে, সেই বিকেলের কথা তাঁর মনে রীতিমতো গেঁথে রয়েছে। এর পর রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে একাধিকবার তিনি শান্তিনিকেতন গেছেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে শিশুদের পড়াশোনা করানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। কিন্তু কিছুদিন গেলেই কেমন অস্থিরতায় ভুগতে শুরু করেছেন লীলা। নানা জাগতিক ও পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হওয়ায় বেশি দিন একনাগাড়ে থাকতে পারেন নি। ছুটে গেছেন কলকাতা। তবে দাদা এবং প্রেরণাদাতা সুকুমার রায়ের কাছে ছড়া ও মজার কাহিনি শোনা, এবং তাঁর কাছ থেকে শিখতে ও লিখতে গিয়ে লীলার মনে হলো, দাদা সুকুমার রায়ের নির্দেশিত পথই তাঁর পথ। তিনি অনবরত লিখতে শুরু করলেন। ছোটবেলায় প্রেস থেকে ‘সন্দেশ’ বেরুবার সময় কলকাতার বাড়িটি মনে হতো কাঁপছে। সেই চলন্ত ছাপাখানায় কম্পিত বাড়ি থেকে বেরুনো কাগজ ‘সন্দেশ’য়েই প্রথম লেখা ছাপা হয় তাঁর, আর সেখানেই নিয়মিত লিখতে শুরু করলেন তিনি।
কিন্তু সুকুমার রায়ের অকাল মৃত্যুতে ‘সন্দেশ’ বন্ধ হয়ে গেল, পারিবারিক ব্যবসা প্রায় গুটিয়ে ফেলা হলো। লীলার জীবন-ও তখন থেকে অকস্মাৎ বদলে গেল। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে দুই-দুই বার শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছুদিন কাজ করে চলে আসেন, একপর্যায়ে দার্জিলিং-এ মেয়েদের স্কুলে পড়াবার কাজ নিয়ে ট্রেনে চেপে বসেন দার্জিলিং-এর উদ্দেশে। সেই স্কুলটা চালাতেন শিবরাম শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা সরকার। সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। মন বসে না। আবার ছুটে আসেন শান্তিনিকেতন, থাকার জন্যে একটি বাসস্থান করেন সেখানে। কিন্তু কিছুদিন বাদেই চলে আসেন কলকাতা। সেখানে আকাশবাণীতে কর্মরত থাকেন কিছুদিন। লীলা মজুমদার এই অবিরত ছোটাছুটি ও কাজকর্মের মাঝেও সময় করে লেখেন। বিশেষ করে ‘আকাশবাণী’তে থাকাকালীন সেখানকার কাজের অংশ হিসেবেই শিশুতোষ বেশির ভাগ লেখা লিখেন তিনি। কিন্তু ‘আকাশবাণী’র ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তার এক নেতিবাচক মন্তব্য শুনে হঠাৎ করেই কাজে ইস্তফা দেন লীলা, যা বহু উচ্চতম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যস্থতা সত্ত্বেও তিনি তুলে নেন না। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর বিখ্যাত রান্নার বইও প্রকাশ করে সুনাম অর্জন করেছেন। তবে সারা জীবন ছোটাছুটি করে জীবনের শেষভাগে এসে তিনি তাঁর মনের মতো কাজ পেয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় যখন নতুন করে আবার ‘সন্দেশ’ বের করতে শুরু করলেন উপেন্দ্রকিশোরের আরেক নাতনি নলিনী দাশের সঙ্গে, তিনি তার আদরের ‘লিলুপিসি’কেও সন্দেশ সম্পাদনায় টেনে নেন। লীলা মজুমদারের দুই কন্যা তখন কলেজে যান, ফলে তাঁর ঝাড়া হাত-পা।
লীলা মজুমদারও বাকি জীবন শিশুসাহিত্য রচনা করে আর ‘সন্দেশ’ সম্পাদনা করে কাটিয়ে দেন।। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে পাকদণ্ডী, আর কোনখানে (রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত), রান্নার বই, বাতাস বাড়ি, খেরোর খাতা, সব ভুতুড়ে, আমিও তাই, কাগ নয় উল্লেখযোগ্য। ‘আর কোনখানে’র শুরুর লাইনটি কী অসাধারণ! ‘পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান ছিল আমার মায়ের বাড়িটি।’
৭৭) লীলা রায় (১৯১০-১৯৯২) অ্যালিস ভার্জিনিয়া বলে আমেরিকার টেক্সাস অঙ্গরাজ্য থেকে এক পিয়ানোবাদক ভারতে সংগীত শিখতে এসে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রেমে পড়ে যান। তাঁরা বিয়ে করার পর রবীন্দ্রনাথ অ্যালিসের নাম রাখেন লীলা রায়। বিয়ের অনুষ্ঠান হয় শান্তিনিকেতনে। বিয়ের পোশাক হিসেবে লীলা রায় বেছে নেন শাড়ি আর অন্নদাশঙ্কর স্যুট-প্যান্ট। লীলার বহু ভাষার ওপর পারদর্শিতা ছিল। তাই অনায়াসে তিনি অনেক বাংলা ও ইংরেজি লেখার ভাষান্তর করতে পেরেছিলেন। শাড়ি পরা, অনর্গল বাংলা বলা, সাধারণ জনগণের সঙ্গে সহজে মিশে যাওয়া এত সহজ ছিল তাঁর জন্যে যে লীলা রায়কে দেখলে মনেই হতো না বাংলার বাইরের মানুষ। তিনি নিজেও একজন সৃজনশীল লেখক ও কবি। অন্নদাশঙ্কর লেখক ছাড়াও একজন সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা ছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় পূর্ব বাংলার অনেক জায়গায় কর্মোপলক্ষে থেকেছেন এবং এই দেশের হালচাল, নিয়ম, বিশ্বাস, মন-মানসিকতা খুব ভালো বুঝতে পারতেন। তরুণ এই দম্পতির সন্তানের জন্মও এপার বাংলায়। অন্নদাশঙ্কর স্ত্রীকে বাংলা শেখাবার জন্যে বেছে নেন হারামণি-খ্যাত অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনকে। মাহবুব-উল-আলম রচিত 'মোমেনের জবানবন্দী' বইটি ১৯৪৬ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রী লীলা রায় ‘ঈড়হভবংংরড়হ ড়ভ ধ ইবষরবাবৎ’ শিরোনামে। সে সময়ে এ বইটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় লীলা রায় ও অন্নদাশঙ্কর রায় বাস্তুত্যাগী শরণার্থীদের প্রচুর সাহায্য করেছেন এবং অনেককে বাড়িতে রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরির কাজ—দেশের ভেতর ও আন্তর্জাতিক আঙিনায় করে গেছেন অকাতরে। যে তিন নারী সেই সময় বাংলাদেশ থেকে আগত লেখক, শিল্পী, শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনায় ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা হলেন লীলা রায়, মৈত্রেয়ী দেবী ও গৌরী আইয়ুব। স্বাধীনতার পর দেশ থেকে বহিষ্কৃত কবি দাউদ হায়দারকে দীর্ঘদিন নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে আপন দৌহিত্রের মতো করে স্নেহের বন্ধনে বেঁধেছিলেন অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায় ।
৭৮) শরৎকুমারী চৌধুরাণী (১৮৬১-১৯২০) : পিতা শশিভুষণ বসু। আন্দুলের সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবারের অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে শরৎকুমারী দেবীর বিয়ে হয়, যখন শরতের বয়স ছিলও মাত্র দশ। ঠাকুর পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী। ছেলেবেলায় শরৎকুমারী পিতার কাছে লাহোরে থাকতেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘লাহোরিণী’ বলে ডাকতেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মাতৃভাষার অনুরাগী ছিলেন এবং ভারতী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শরৎকুমারী অতি উঁচু মাপের সাহিত্য নির্মাণ করেছেন। তাঁর বহু রচনা সেকালের বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় (সবুজপত্র, মানসী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা, ভাণ্ডার, ধ্রুব, বিশ্বভারতী, বালক, ইত্যাদি) অনামে প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত একটিই মাত্র বই ‘শুভবিবাহ’। কিন্তু প্রকাশিত এই একটি মাত্র বইতেও তাঁর নাম নেই। এই বইটি সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, ‘... রোমান্টিক উপন্যাস বাংলা-সাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তব চিত্রের অত্যন্ত অভাব, এ জন্যও এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম।’ শরৎকুমারী ও তাঁর স্বামী অক্ষয় চৌধুরী উভয়েই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎকুমারীর সাহিত্যের সমঝদার ছিলেন। তিনি শরৎ রচিত গ্রন্থাবলিই কেবল পাঠ করেন নি, তিনি তাঁকে মাঝে মাঝে গল্পের প্লট দিতেন যেমন দিয়েছেন অন্য লেখকদেরও। এভাবে একবার তিনি ভুলে একই প্লট দিয়ে ফেলেছিলেন শরৎকুমারী চৌধুরানী ও বনফুলকে। তাঁরা উভয়েই অতি যত্নের সঙ্গে ওই প্লট থেকে দুটি ভিন্ন মধুর ছোটগল্পের জন্ম দেন। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে শরৎকুমারী চৌধুরানী ‘ভারতী’ পত্রিকায় একটি গল্প লিখেছিলেন, ‘আদরের না অনাদরের’। ওই গল্পে দুই প্রজন্মের নারীদের মধ্যে তর্কবিতর্কের মধ্যে এটিই প্রতিষ্ঠা করা হয় যে মেয়েসন্তান আদরের, অনাদরের নয়।
৭৯) শান্তি ঘোষ (১৯১৬-১৯৮৯) : বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও মা শৈলবালা ঘোষ। শান্তি ঘোষ-এর বাবা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। বাবার উৎসাহে শান্তি ঘোষ বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। শান্তি যখন জেলে তখন মেয়ের কাছে এক পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘তুমি যে হস্ত দ্বারা এই বিপ্লবী কর্মটি করেছ সে হাত ঈশ্বরের ছিল, ঈশ্বরই তোমাকে জেল থেকে মুক্ত করে আমার কোলে ফিরিয়ে আনবে।’
মাত্র ১৪ বছর বয়সে নওয়াব ফয়েজুন্নেসা স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী থাকা অবস্থায় ব্রিটিশদের কাছ থেকে দেশ স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন কুমিল্লার সাধারণ ঘরের কিশোরী শান্তি ঘোষ। তিনি বিপ্লবী দলের সদস্য হয়ে দেশক্ষার প্রয়োজনে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সহচরী ও সমবয়সী সুনীতি চৌধুরীর সঙ্গে পার্টির কথা মতো সুচারুরূপে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলি করে হত্যা করেন শান্তি ও সুনীতি। কিন্তু হত্যা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তাঁরা। আদালতে বিচার শেষে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন দুজনেই। তাদের পরিবারের ওপর নেমে এলো অমানবিক নির্যাতন। গান্ধীর উদ্যোগে রাজবন্দিদের মুক্তির আন্দোলনের ফলে ১৯৩৯ সালে তাঁরা মুক্তি পান। পরবর্তীকালে শান্তি ঘোষ সাংবিধানিক রাজনীতি করেন এবং দেশ স্বাধীন হলে পশ্চিমবাংলার প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৯৫২-১৯৬৮)। ১৯৪২ সালে শান্তি ঘোষ চট্টগ্রামের আরেক বিপ্লবী চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তার আত্মজীবনী গ্রন্থ রয়েছে ‘অরুণ বহ্নি’। ১৯৮৯ সালের ২৮ মার্চ শান্তি ঘোষ মারা যান। তাঁর আত্মজীবনী ও সংবাদপত্রে লিখিত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় সেই বিশেষ দিনের কর্মতৎপরতা।
১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর। এই দিন কুমিল্লার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সিজিবি স্টিভেন্সকে তার বাসায় গুলি করে হত্যা করেন স্কুলছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। এই দুই বান্ধবী কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেছা স্কুলের অষ্টম ও সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। স্টিভেন্স ছিলেন অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মকর্তা। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সেই সময় বিপ্লবীরা তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী স্টিভেন্সকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় শান্তি ও সুনীতিকে। শুরু হয় তাদের অস্ত্র চালনা শিক্ষা।
১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্ব^র আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবেই চলছিল শহরের সকলের কাজ। দুই বিপ্লবী ছিলেন কেবল ব্যতিক্রম। শান্তি, সুনীতির বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ। স্কুলে অনুষ্ঠান আছে— এ কথা বলে শাড়ি পরে শরীরে চাদর জড়িয়ে তারা বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। চাদরের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন অস্ত্র। শান্তি .৪৫ ক্যালিবারের রিভলভার এবং সুনীতি .২২ ক্যালিবারের রিভলবার সঙ্গে নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও সেদিন তারা সঙ্গে নিয়েছিলেন কুমিল্লায় সাঁতার প্রদশর্নীর একটি অনুমতিপত্র।
এরপর তারা বিনা বাধায় ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে পৌঁছে যান। তখন সকাল দশটা। ইন্টারভিউ স্লিপ দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলোর অফিসে এলেন তাদের প্রত্যাশিত সিজিবি স্টিভেন্স। সঙ্গে এলেন মহকুমা প্রশাসক নেপাল চন্দ্র সেন। এগিয়ে আসতেই শান্তি এগিয়ে দিলেন সাঁতার প্রদর্শনীর দরখাস্তটি। সেখানে ফয়জুন্নেছা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিস বিশ্বাসের অনুরোধ লিপিবদ্ধ ছিল। সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করে স্বাক্ষর দিলেন স্টিভেন্স। কিন্তু স্টিভেন্স দরখাস্তটি শান্তির হাতে ফেরত দেওয়ার পূর্বেই গর্জে উঠল শান্তির .৪৫ বোরের রিভলভার। অব্যর্থ নিশানা। স্টিভেন্স লুটিয়ে পড়লেন। এ সময় সুনীতির গুলিতে আহত হলেন এসডিও সাহেব। চারপাশ থেকে স্টিভেন্সের কাজের লোক ও সাহায্যকারীরা এসে শান্তি ও সুনীতিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।
থানায় মামলা হলেও কলকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বিচার সম্পন্ন হয়। ১৯৩২ সালের ২৭ জানুয়ারি রায়ে বিচারকগণ বলেন, তাদের কারোরই বয়স ১৬ বছরের অধিক না হওয়ায় তাদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।
৮০) শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) : শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯০৮ সালে নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বেগম মাহমুদের শিক্ষাজীবন অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি তিন বিষয়ে ডিস্টিংশন নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি ডাক্তার ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর অনেকদিন পড়াশোনা করতে না পারলেও পরে বেগম মাহমুদ ১৯৩২ সালে বি.এ এবং ১৯৪২ সালে এম.এ পাস করেন। তিনিই বাংলাদেশের মুসলিম মেয়েদের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট।
লেখিকা হিসেবে তাঁর রয়েছে প্রচুর অবদান। অতি শৈশবেই শামসুন নাহারের সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত তৎকালীন কিশোর পত্র ‘আঙুর’-এ তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। সেটাই একটি কবিতা। তাঁর ছাত্রজীবনের লেখার সংকলন ‘পুণ্যময়ী’ (১৩৩১)। এখানে রয়েছে রাবেয়া, ফাতেমা, আয়শা প্রমুখ প্রাচীন সতী সাধ্বী আট মুসলমান নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী। পরবর্তীকালে বেগম মাহমুদ রচনা করেছেন ‘রোকেয়া জীবনী’, ‘বেগম মহল’, ‘শিশুর শিক্ষা’, ‘আমার দেখা তুরস্ক’ ও সর্বশেষ রচনা ‘নজরুলকে যেমন দেখেছি’। ১৯৩৭ সালে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা ‘রোকেয়া জীবনী’ প্রকাশিত হলে জীবনীকার ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ‘নজরুলকে যেমন দেখেছি’ (১৯৫৮) নজরুলের সঙ্গে লেখিকার আবাল্য পরিচয় ও সাহিত্য রচনায় কবির উৎসাহ দানের স্মৃতিকথা। নাহারের অগ্রজ হাবিবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে কলকাতা থেকে ‘বুলবুল’ (১৯৩৪-৩৯) সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করার সময় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শামসুন নাহারের রচনাবলীর প্রধান উপজীব্য হচ্ছে শিশু ও নারী।
ব্যক্তিগত জীবনে শামসুন নাহার বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে লিপ্ত ছিলেন। তিনি নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদের সাবেক পাকিস্তান শাখা, ঢাকা ইডেন কলেজ, আর্ট ইনস্টিটিউট, নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভানেত্রী, আন্তর্জাতিক মহিলা মৈত্রী সংঘের এশীয় আঞ্চলিক প্রতিনিধি ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তান শিশু কল্যাণ পরিষদের সভানেত্রী হিসেবে এ দেশের নারী শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ কর্মতৎপরতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ১৯৩৫ সালে কলকাতায় প্রখ্যাত তুর্কি সাহিত্যিক ও রাজনীতিক খালিদা এদিব হানুমের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।






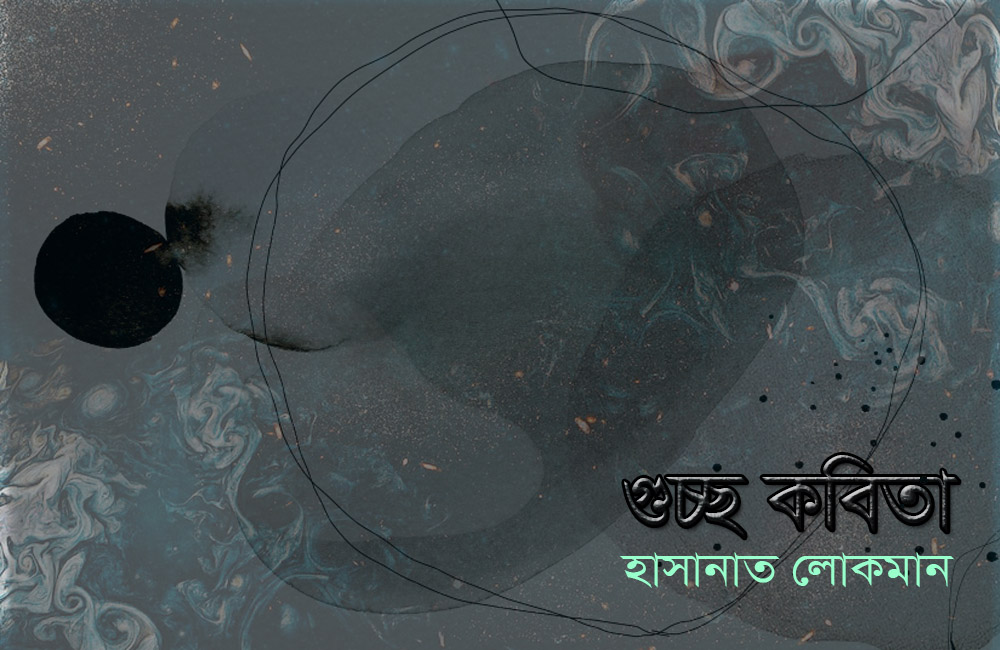


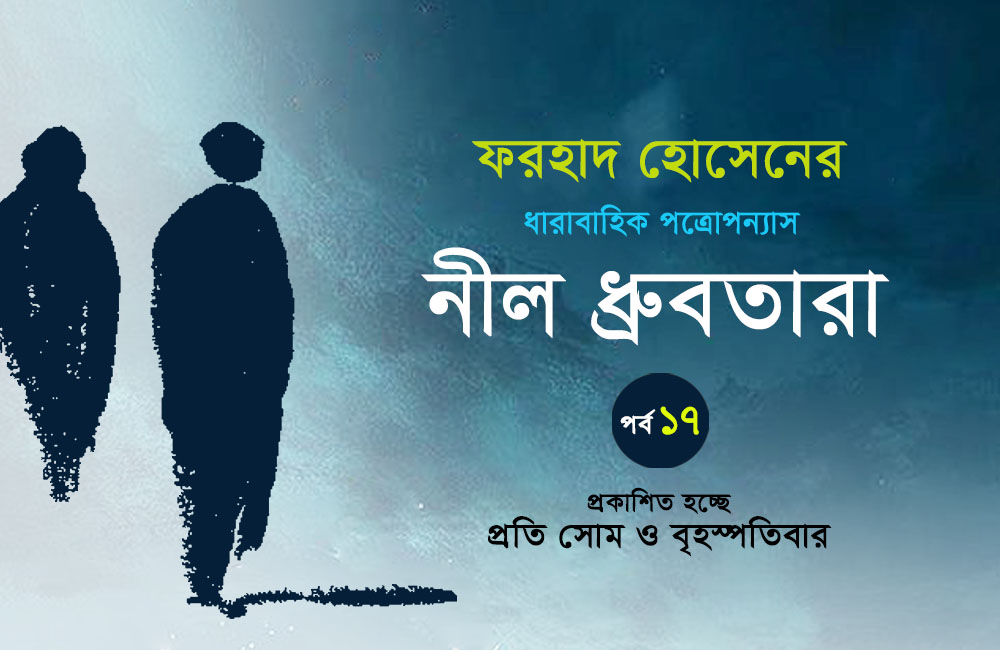

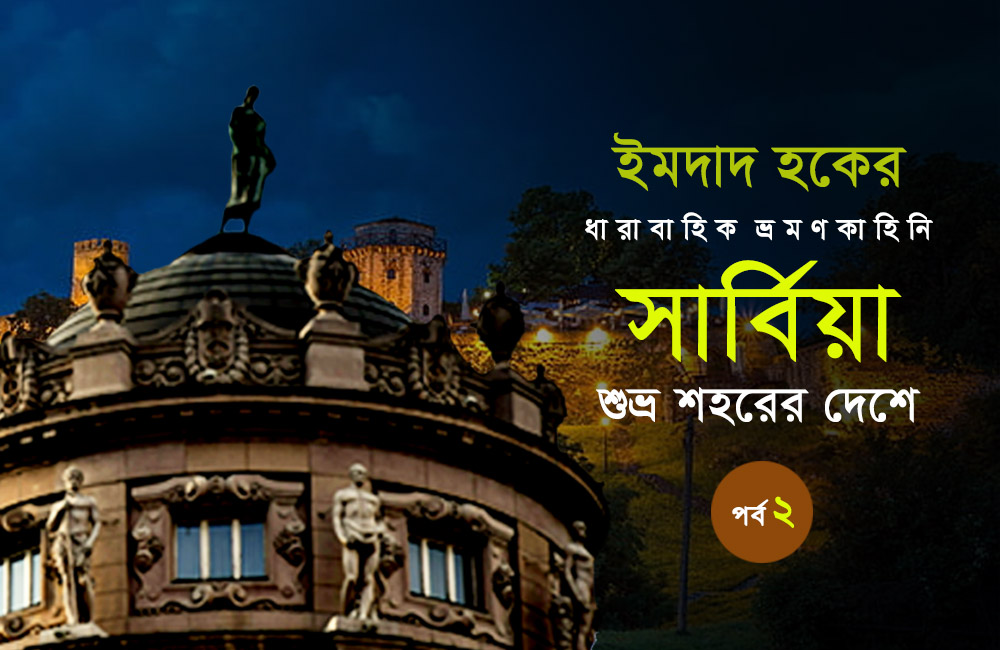
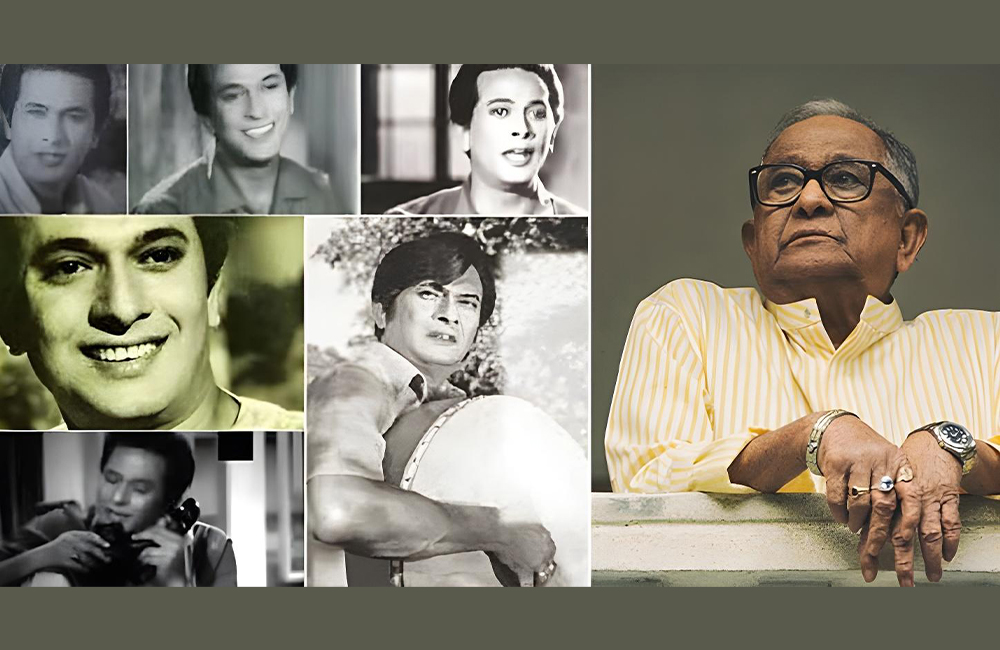


Leave a Reply
Your identity will not be published.