[১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায় ইংরেজবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন নতুন রূপ পেতে থাকে। বাংলা এবং ভারতবর্ষের এই বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে পড়ল জার্মানি এবং রাশিয়া। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বিপ্লব-প্রয়াসের প্রায় সমান্তরালে চলতে থাকল বাংলা এবং ভারতবর্ষে ইংরেজবিরোধী বিপ্লবের প্রচেষ্টা। এই উপন্যাসে একই সঙ্গে ধারণ করা হয়েছে রুশ বিপ্লবী এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া বাঙালি বিপ্লবীদের প্রেম এবং বিপ্লবের কাহিনি ও এই দুই ভূখণ্ডের বিপ্লবীদের আন্তঃসম্পর্ক। লেখাটির প্রথম খণ্ডের কাহিনি শেষ হয়েছে ১৯১৪-১৫ সালে এবং এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০২৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ড ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে ‘অন্যদিন’-এ। এই খণ্ডের গল্প আরম্ভ হয়েছে ১৯১৪ সালের রাশিয়ায় আর শেষ হয়েছে ১৯২১-২২ সালে গিয়ে।]
১৪
১৯১৬ সালের ১৪ জুন। সূর্যটা গনগনে হয়ে আকাশ থেকে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। এই মাত্র একটা জাপানি জাহাজ হুইসেল বাজিয়ে ভিড়েছে সানফ্রানসিস্কো বন্দরে। আমেরিকার মাটিতে নামবার জন্য যাত্রীদের মাঝে হুড়াতাড়া লেগে গেছে। একটু পরই ভিড় কিছুটা কমে আসতেই জাহাজ থেকে এক ভারতীয় যুবক নেমে এল। যুবকটির ডান হাতে বাইবেল, গলায় ঝোলানো সোনার ক্রুশ। যুবকটি পন্ডিচেরী থেকে এসেছে। যুবকটি ধর্মতত্ত্ব পড়তে প্যারিসে যাবে। পথিমধ্যে কিছুদিনের জন্য আমেরিকায় যাত্রাবিরতি। এই যুবকের নাম ফাদার মার্টিন। ইমিগ্রেশনে তেমন ঝামেলা ছাড়াই ফাদার মার্টিন সানফ্রানসিস্কো শহরে প্রবেশ করল।
ফাদার মার্টিন মানে নরেন সমুদ্র বন্দরে বেশি দাঁড়িয়ে থাকবার ঝুঁকি নিল না। একটু তাড়াহুড়া করেই ট্যাক্সিতে চড়ে বসল। সানফ্রানসিস্কোর গদর পার্টির লোকেরা ওর জন্য হোটেলে বুক করে রেখেছে। অন্য কোথাও না গিয়ে নরেন সরাসরি হোটেলে চলে এল।
হোটেলে পৌঁছে নিজের রুম খুঁজে পেতে নরেনের কোনো ঝামেলা হলো না। ঘরে ঢুকেই নরেন কাপড়জামা না বদলেই বাথরুমে চলে গেল। অনেক সময় নিয়ে স্নান করল। তারপর আবার তাড়াহুড়া করে সানফ্রানসিস্কো শহর ঘুরতে বেরিয়ে গেল। বিশাল শহরটা হাঁটতে হাঁটতে নরেন যখন ক্লান্ত তখন লক্ষ করল সামনেই গোল্ডেন গেট পার্ক। নরেন ভেতরে ঢুকে একটা কাঠের বেঞ্চে বসে পড়ল। তারপর কোটের বাঁ পকেট থেকে লাল রঙের একটা নোটবুক বের করল। এই নোটবুকে অনেকের নাম আর ঠিকানা লেখা। নরেন প্রথম দুপাতায় চোখ বুলিয়ে নিল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একটা বাজে। নরেন উঠে দাঁড়াল। কাছেই গদর পার্টির নেতা রামচন্দ্রের অ্যাপার্টমেন্ট। ওনার সঙ্গে দেড়টার সময় মিটিং।
রামচন্দ্রের সঙ্গে নরেনের কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। বছর খানেক আগেই স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির লেকচারার হরদয়াল ছিল গদর পার্টির সভাপতি। টোকিও ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন প্রফেসর মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ আর রামচন্দ্র ছিল ওর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ আবার গত বছর থেকে প্রবাসী ভারত সরকারের প্রথম প্রধানন্ত্রী। তাই হরদয়ালকে আমেরিকা থেকে বের করে দেওয়ার পর ওর অন্য সহযোগী রামচন্দ্র গদর পার্টির নেতৃত্ব নিয়েছে। রামচন্দ্রকে দেখে মনে হলো ওর বয়স পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ হবে। বলিষ্ঠ শরীর, ঠোঁটের ওপর পুরু কালো গোঁফ। নরেনকে স্বাগত জানিয়ে রামচন্দ্র বলল, আপনি আসায় ভালোই হলো।
তাই ?
হ্যাঁ। আপনি তো জানেন গদর পার্টির বেশিরভাগ সদস্যই শিখ। বাংলা প্রদেশে শুনেছি স্বাধীনতার আন্দোলন দানা পাকিয়ে উঠেছে। অথচ আসলে যে কী হচ্ছে সেই খবর ঠিকমতো পাই না। আপনি আসায় সত্যিকার নিউজ পাওয়া যাবে।
তা পাবেন, কলকাতার সঙ্গে এখনো আমার ভালো যোগাযোগ আছে।
আপনি চাইলে গদর পার্টিতে কাজ করতে পারেন। হরদয়াল যাওয়ার পর আমি পার্টিকে অনেক গুছিয়ে ফেলেছি। ফান্ডিংও আসছে।
জার্মানদের থেকে ?
হ্যাঁ। আমাদের লোকেরাও চাঁদা দেয়। পার্টিতে কাজ করার এটাই সেরা সময়।
আমি তো এখানে বেশি দিন নেই। জার্মানি চলে যাব। ওখান থেকে অস্ত্রের চালান নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরব।
জার্মানদের আমার জানা আছে। এসব করতে অন্তত ছ মাস লেগে যাবে। এমন কি বছরখানেকও লাগতে পারে। এর ভেতর আপনি গদর পার্টির জন্য কাজ করতে পারবেন। নিউয়র্কের বাঙালি বিপ্লবীদের সাথে সান ফ্রান্সিস্কোর গদর পার্টির সম্পর্ক আরও জোরদার করতে হবে।।
সে করা যাবে।
আপনাদের লালা লাজপত রায়কে বলেছিলাম গদর পার্টির দায়িত্ব নিতে। কথাটা শুনে উনি একদম মিইয়ে গেলেন। সবাইকে দিয়ে তো আর বিপ্লবের কাজ হয় না। কিন্তু আপনি তো শুনেছি কলকাতায়ও বিপ্লবে জড়িত ছিলেন।
তা ছিলাম, তবে আমি ব্যস্ত থাকব অস্ত্রের জোগান নিয়ে। আপনারা তো এখানকার পলিটিক্সেও জড়িত। কিন্তু আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতকে স্বাধীন করা।
আমাদের সবার উদ্দেশ্যই তো তাই। ভারতকে স্বাধীন করতে হবে। তবে এখন আমরা পৃথিবীব্যাপী কাজ করছি। যেখানে উপনিবেশ সেখানেই বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছি। গদর ছাড়াও আমাদের পার্টির আরেকটা নাম আছে জানেন তো ?
না, জানি না।
ফ্রি রিপাবলিক অফ ইউনাইটেড স্টেটস অফ ইন্ডিয়া।
শুনতে কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার মতোই লাগছে। ওদের ডেকারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সে সমতা, অধিকার নিয়ে বড় বড় কথা লেখা। কিন্তু আসল চালাকি করেছে ওরা ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনে আমেরিকার শাসনতন্ত্র লেখার সময়। কী করেছে জানেন ?
না। এ ব্যাপারে আমার কোনো পড়ালেখা নেই।
ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনে শাসনতন্ত্র লিখেছে সব ধনীরা একত্র হয়ে। দি টয়লিং মাস আর শ্রমিকদের কোনো প্রতিনিধিত্বই ছিল না সেখানে। ধনীরা এমনভাবে শাসনতন্ত্র লিখেছে যেন ধনীদের আধিপত্য আমেরিকায় চিরকাল ধরে চলতে থাকে। অথচ স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছিল শ্রমিক শ্রেণি। অথচ দেখবেন সবাই সব সময় ডেকেয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স আর ফাউন্ডিং ফাদারদের গল্প শোনায়।
আপনি আমেরিকায় না থেকেও আমার থেকে বেশি জানেন। কিন্তু একটা কথা বলি, ভারত আমেরিকার মতো গণতন্ত্রের ভেক ধরা বর্ণবাদী রিপাবলিক হবে না। ইউনাইটেড স্টেটস অফ ইন্ডিয়ায় কোনো শ্রেণি কিংবা বর্ণবৈষম্য থাকবে না।
নরেন জানে এসব বাঁধাবুলি শুনতে ভালোই শোনায়, কিন্তু বাস্তবে এমন হয় না। তারপরও দেশের স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই। রামচন্দ্রের স্ত্রী পদ্মাবতী বাইরে ছিল। সে ঘরে আসতেই রামচন্দ্র উনাকে নরেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পদ্মাবতী খুশি হয়ে বলল, আপনি সেই কলকাতা থেকে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। দুপুরে না খাইয়ে আপনাকে ছাড়ছি না। আপনি বসুন, আমি চট করে কিছু রেঁধে ফেলছি।
পদ্মাবতী রান্নাঘরে গিয়ে শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন নরেনের জন্য দুপুরের খাবারের আয়োজনে। রামচন্দ্র আবার নরেনকে রাজনীতির নানা আঁটঘাট বোঝাতে লাগল। রামচন্দ্রের সব কথাই যে নরেনের মনঃপূত হলো তা না। তবে গদর পার্টি যে ওরেগন আর সানফ্রান্সিস্কো থেকে সুদূর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য মরণপণ করে চেষ্টা চালাচ্ছে সেই ব্যাপারটাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। রামচন্দ্রের চোখেমুখে কেমন যেন একটা ধূর্ততা লুকানো। তাই রামচন্দ্রের সঙ্গে কাজ করবার ব্যাপারে নরেনের মনে কোনো আগ্রহ তৈরি হলো না।
আরও কিছু হাতের কাজ সেরে হোটেলে ফিরতে সেদিন নরেনের বেশ রাত হয়ে গেল। ভ্রমণ ক্লান্তি আর সময়ের পার্থক্যের জন্য ঘুমও চলে এল খুব তাড়াতাড়ি। পরদিন ঘুম থেকে উঠেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। এত ভোরেও এই শহর মহাব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাস্তার উল্টোদিকে একটা রেস্টুরেন্ট। নরেন হাতমুখ ধুয়ে ওই রেস্টুরেন্টে গিয়ে সকালের নাশতা সারল। ছাত্র এবং শ্রমিক মিলিয়ে এই সানফ্রানসিস্কো শহরে অনেক শিখ থাকে। তাই শ্যামবর্ণের মানুষ দেখে এখানকার লোকজনের খুব একটা অবাক হওয়ার কথা না। কিন্তু নরেন লক্ষ করল অনেকেই ওর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে নরেন সামনের নিউজপেপার স্ট্যান্ডে গেল। একটা পত্রিকা হাতে নিতেই নরেন হতবাক। পত্রিকার হেডলাইনে বড় বড় করে লেখা, রহস্যময় কে এই আগন্তুক আমেরিকায় ? ও কি কুখ্যাত হিন্দু বিপ্লবী নাকি ভয়ংকর জার্মান গুপ্তচর ?
১৫
নরেন তাড়াতাড়ি করে পুরো খবর পড়ল, কাল যখন হংকং থেকে আগত নিপ্পন মারু জাহাজ সানফ্রানসিস্কো বন্দরে ভিড়ল, তখন জাহাজ থেকে নেমে এল এক রহস্যময় যুবক। হাতে তার বাইবেল, গলায় ক্রুশ। ইমিগ্রেশনের খাতায় এনার নাম ফাদার মার্টিন। নাম যাই হোক না কেন, গোপনসূত্রে প্রাপ্ত খবরের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে ইনি কোনো খ্রিস্টান ধর্মযাজক নন। ইনি আসলে একজন রহস্যময় হিন্দু ব্রাহ্মণ। তথাকথিত ফাদার মার্টিন বন্দরে নেমে ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি ভারতের ফরাসিশাসিত পন্ডিচেরি নামের বন্দর থেকে জাহাজে উঠেছিলেন। কিন্তু জাহাজের অনেক যাত্রীরা দাবি করেছেন, তিনি ওই বন্দর থেকে জাহাজে ওঠেন নি। এরচেয়েও আতঙ্কজনক ব্যাপার হলো, অনেকে সন্দেহ করছে তিনি হয় একজন দুর্ধর্ষ ভারতীয় বিপ্লবী নেতা নতুবা জার্মান সরকারের ধুরন্ধর গোয়েন্দা। জাহাজের এজেন্টকে তিনি সানফ্রানসিস্কোর যে ঠিকানা দিয়েছেন সেটা আরও চাঞ্চল্যকর। ঠিকানাটি হলো ৯০ বেকার স্ট্রিট, সানফ্রান্সিস্কো। এই ঠিকানায় বাস করেন চরমপন্থী গদর পার্টির নেতা রামচন্দ্র ভরদওয়াজ। আমেরিকান সরকারের সময় থাকতেই এই ভয়ংকর ভারতীয় সন্ত্রাসীর ব্যাপারে সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত।
লেখাটা পড়ে নরেন তটস্থ হয়ে গেল। ব্রিটিশ আর আমেরিকান চৌকস গোয়েন্দাদের এড়িয়ে পৃথিবীর কোথাও নিশ্চিন্তে পা ফেলার উপায় নেই।
পত্রিকায় হেডলাইন হওয়ার পর সানফ্রান্সিস্কোতে নিজের খুশিমতো ঘোরাফেরা করা নরেনের জন্য বিপজ্জনক হয়ে গেল। নরেনের সঙ্গে গদর পার্টির সম্পর্ক পর্যন্ত পত্রিকাওয়ালারা ধরে ফেলেছে। নরেন তাড়াহুড়া করে হোটেল রুমে ফিরে এল। দ্রুত ব্যাগ গুছিয়ে নিল। তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে বসল। ট্যাক্সি ছুটল পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে পালো আলতোর পথে। গন্তব্য আমেরিকার বিখ্যাত স্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটি। কলকাতায় থাকতে নরেনের বিপ্লবী বন্ধু যদুগোপাল বলে দিয়েছিল আমেরিকায় কোনো ঝামেলায় পড়লে নরেন যেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি চলে যায়। সেখানে যদুগোপালের ছোট ভাই পড়ালেখা করছে।
যদুগোপাল বাঘা যতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একজন। বাঘা যতিনের মৃত্যুর পর যদুগোপালই যুগান্তর দলের হাল ধরেছে। যদু গোপাল সারা পৃথিবী থেকে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লব চালানোর জন্য তার দুই ভাইকে দুই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। ছোট ভাই ধনগোপাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি পড়তে জাপান গিয়েছিল ছয় বছর আগে। কিন্তু সেখানে এসেম্বলি লাইন পদ্ধতি ধনগোপালের কাছে অমানবিক মনে হয়েছে। জাপানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিছুদিন পরই সওদাগরি জাহাজের খালাসি হয়ে ধনগোপাল চলে এসেছিল সানফ্রানসিস্কো। সানফ্রানসিস্কো এসে ধনগোপাল পাগলের মতো কাজ খুঁজে বেড়িয়েছে। শেষমেশ কাজ পেয়েও গেছে। কাজ করে যে টাকা আয় হয় তা দিয়ে ধনগোপাল ওর পড়ালেখা চালায় আর কোনো রকমে খেয়েপরে টিকে থাকে।
ধনগোপাল প্রথমে তিন বছর ইউ সি বার্কেতে পড়েছে। ওখানকার বামপন্থী আর অ্যানার্কিস্টদের সাথে ধনগোপালের গলায় গলায় ভাব জমে উঠেছিল। কিন্তু একদিকে টাকাপয়সার টানাটানি, অন্যদিকে কট্টরপন্থী রাজনীতির কারণে ইউ সি বার্কেতে ধনগোপাল নানা চাপের মুখে পড়ে। একপর্যায়ে ইউ সি বার্কে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ভাগ্য ভালো যে ধনগোপাল স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে একটা সুযোগ পেয়ে যায়। এখানে সে দু বছর আগে মেটাফিজিক্সে ডিগ্রি শেষ করেছে। আরও লেখাপড়ার জন্য এখনো সে স্ট্যানফোর্ডেই আছে।
পালো আলতোর যাওয়ার পথে নরেনের মনে পড়ল গদর পার্টির আগের নেতা হরদয়াল এই স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন। কিন্তু গদর পত্রিকায় জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লেখার কারণে ওকে চাকুরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কেবল স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি না, গ্রেপ্তার এড়াতে হরদয়াল অ্যামেরিকা ছেড়ে জার্মানি চলে গেছেন।
কলকাতায় যদুগোপালের সাথে নরেন ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। কিন্তু ওর ছোট ভাই ধনগোপালের সাথে ভারতে থাকতে ওর কখনো দেখা হয় নি। ধনগোপালের বয়স বিশ কি একুশ হবে। যদুগোপালের মতো এই ভাইটিও দারুণ সুদর্শন। আমেরিকায় বিপ্লবের কাজে এলেও এখানে এসে ধনগোপালের আরেকটা সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে। ও দারুণ ভালো লিখতে পারে। ওর ইংরেজিতে লেখা গল্প-কবিতার বেশ সুনাম ছড়িয়ে গেছে পুরো আমেরিকায়। গত বছর পল এল্ডার এন্ড কোং ধনগোপালের দুটো কবিতার বই পরকাশ করেছে, ‘সংস অফ টুইলাইট’ আর ‘সংস অফ দা নাইট’। লাইলী মজনু নামে ওর একটা গীতিকাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। নিজের সাফল্য নিয়ে ধনগোপাল নিজেও উচ্ছ্বসিত। ওর থাকার কথা জাপানে, ওখান থেকে অ্যামেরিকায় এসে ইংরেজি সাহিত্যে এভাবে নিজের প্রতিভার ছাপ রাখতে পারবে সেটা ধনগোপাল স্বপ্নেও কল্পনা করে নি।
নরেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি পৌঁছুল বিকেল বেলা। ধনগোপালকে ক্যাম্পাসে খুঁজে পেতে তেমন সমস্যা হলো না। বড় ভাইয়ের বন্ধু নরেনকে কাছে পেয়ে ধনগোপাল বিশেষ উচ্ছ্বসিত হলো। সমস্ত বিকেল ধরে ধনগোপাল নরেনকে মহা উৎসাহে স্ট্যানফোর্ড ক্যাম্পাস আর লাইব্রেরি ঘুরে দেখাল। রাতে একসঙ্গে ডিনার করবার সময় ধনগোপাল বলল, নরেনদা একটা কথা বলব ?
হুম বলো।
অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আপনাকে বেশ অনেকদিন আমেরিকায় পড়ে থাকতে হবে। তারপর হয়তো আপনি জার্মানি যাবেন।
এখনই কিছু বলতে পারছি না। সব যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। রাম চন্দ্র বললেন আমাকে হয়তো এখানে আরও এক বছর থাকতে হতে পারে।
সেক্ষেত্রে আমি বলব আমেরিকায় বসে নির্বিঘ্নভাবে কাজ করতে চাইলে আপনি কিন স্লেট হয়ে যান।
বুঝি নি। কিন স্লেট কীভাবে হব ? আরও খুলে বলো।
সানফ্রান্সিকোর গোয়েন্দারা সম্ভবত এতদিনে আপনার আসল নাম, ঠিকানা বের করে ফেলেছে।
তাই ভাবছো ?
জি। এদের হাত থেকে সহজে নিস্তার পাবেন না। আপনাকে ওরা ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেবে।
তাহলে এখন কী করা যায় ?
আপনি আপনার নাম, পরিচয় ভুলে যান। নতুন নাম, নতুন পরিচয় নিন।
আমি এতদূর পর্যন্ত ভাবি নি। তবে আইডিয়াটা খারাপ না।
আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি আপনার জন্য একটা নাম ঠিক করে ফেলেছি।
এটাই ক্রিয়েটিভ মানুষের ক্ষমতা। কী নাম ঠিক করেছ ?
আজ থেকে আপনি আর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নন। আপনার নতুন নাম মানবেন্দ্রনাথ রায়, সংক্ষেপে এম এন রায়। সারা পৃথিবী ভবিষ্যতে আপনাকে এম এন রায় বলে চিনবে।
যতিন আর অমৃতার মৃত্যুর পর নরেন মনে মনে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু একটার পর একটা ঝড় সামলাতে সামলাতে সে শোক করার সময় পায় নি। শোক করার সময় হবে বলেও মনে হয় না। নরেন ভাবল সেই শোকার্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ভারতের মাটিতেই পড়ে থাক। এখানে না হয় জন্ম হোক এম এন রায়ের, যার একটাই স্বপ্ন। সেই স্বপ্নটি হলো, ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করা। নরেন আবেগ চেপে বলল, আমার কিন্তু নামটা পছন্দ হয়েছে। আর তোমার ওই কিন স্লেট কথাটাও আমার পছন্দ হয়েছে। আমেরিকায় আরেকটা নতুন আরম্ভ হলে ক্ষতি কী ?
সেদিন সন্ধ্যায় এভাবেই স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে জন্ম হলো এম এন রায়ের।






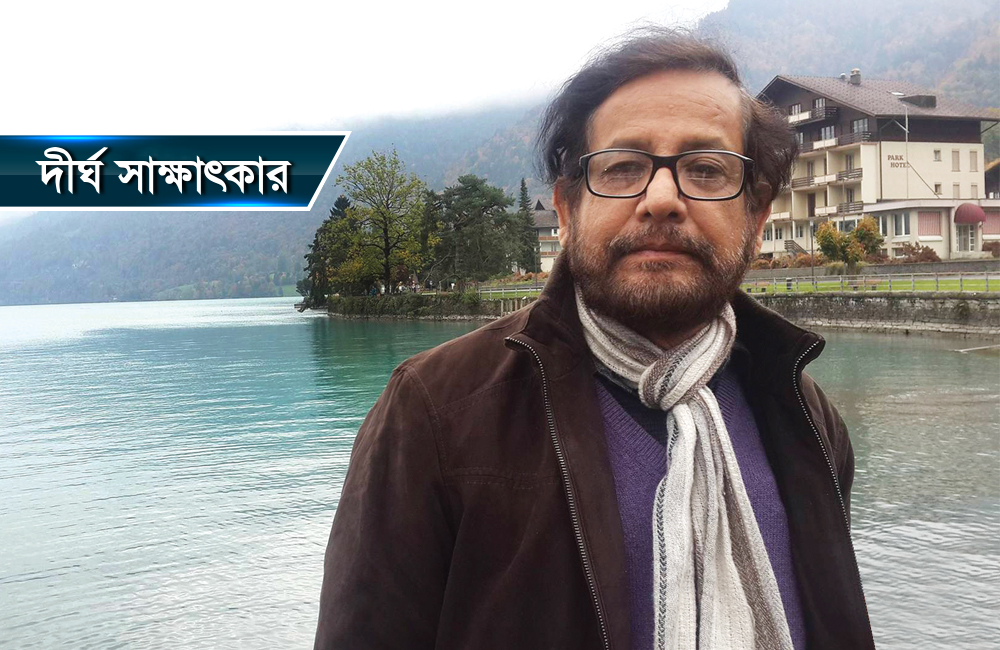
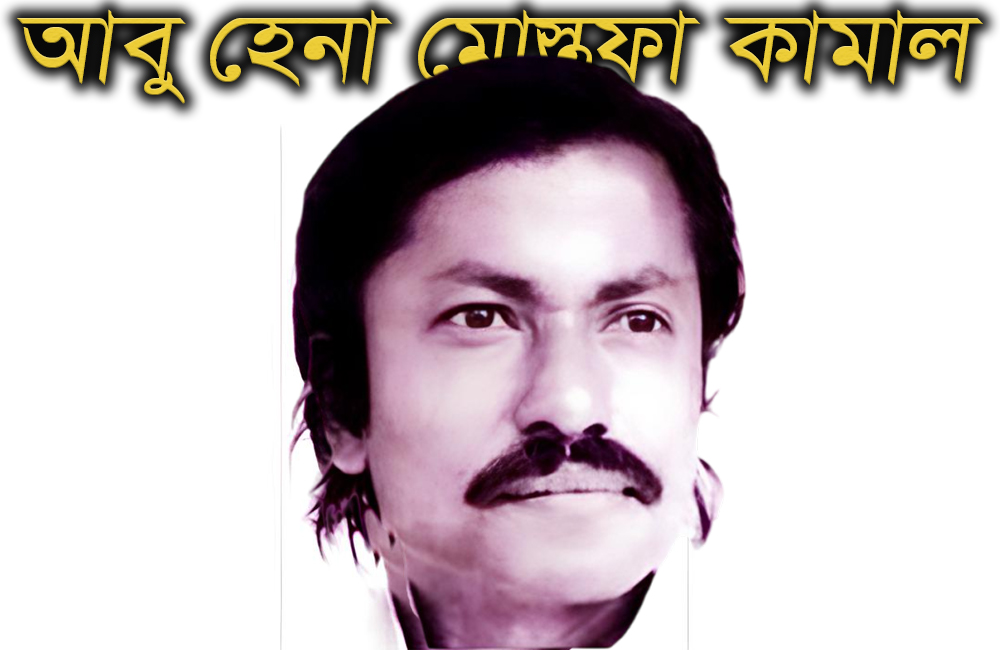


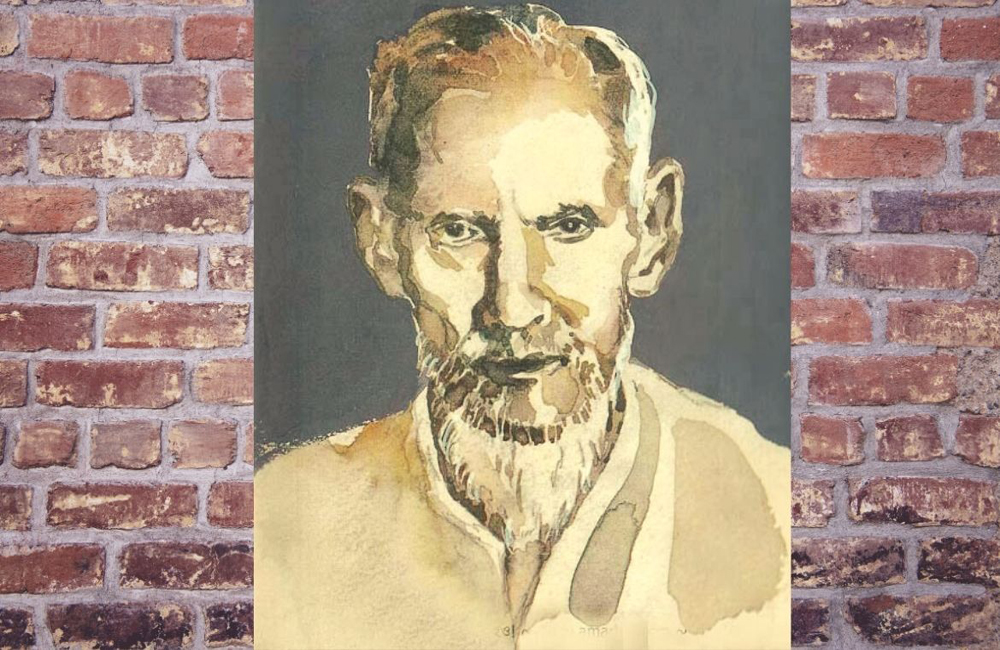




Leave a Reply
Your identity will not be published.