[বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীও রয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য ভুবন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধÑসব ধরনের রচনাতেই নারীরা সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। এমনকি সংস্কৃতিতেও। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সেইসব স্মরণীয় নারী এবং তাঁদের কীর্তির কথাই এই ধারাবাহিক রচনায় তুলে ধরা হয়েছে।]
৯১) সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) : বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট মুসলিম মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল। সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালে বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ পরগণায় মাতামহ সৈয়দ মুয়াজ্জম হোসেন চৌধুরীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কুমিল্লা জেলার সৈয়দ আবদুল বারী বিএল। সুফিয়া কামাল স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান নি। তাঁদের পরিবারে বাংলা ভাষার প্রবেশ এক রকম নিষিদ্ধ ছিল। এই বিরুদ্ধ পরিবেশে সুফিয়া কামাল স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। ১১ বছর বয়সে জ্ঞাতি ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তার সংস্পর্শে এসে তিনি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার সুযোগ পান। কিছুদিন পরে নেহাল হোসেন ইন্তেকাল করলে চট্টগ্রামের কামালউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। সুফিয়া কামাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় নিজকে নিয়োজিত করে কবি হিসাবে বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘সাঁঝের মায়া’ (১৯৩৮), ‘মায়া কাজল' (১৯৫১), ‘মন ও জীবন' (১৯৫৭), ‘উদাত্ত পূরবী’ (১৯৭১)। এ ছাড়াও তিনি গল্প, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথাও লিখেছেন।
কবির বিভিন্ন কবিতায় বিশেষ করে তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যুর পর যে সব কবিতা তিনি রচনা করেছেন তাতে শোকের অপূর্ব অভিব্যক্তি ঘটেছে। কামিনী রায়ের পর বাংলা সাহিত্যে অনেকদিন পর্যন্ত বিশিষ্ট কোনো নারী কণ্ঠস্বর শোনা যায় নি। সুফিয়া কামালের কবিতায় সেই কণ্ঠস্বর যেন আবার নতুন করে বাংলা ভাষায় উচ্চারিত হলো।
তবে কবি বা সাহিত্যিক হিসেবে সুফিয়া কামাল যত না নন্দিত তাঁর চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতি তাঁর বাংলাদেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের, বিশেষ করে নারী জাগরণ ও নারী আন্দোলণের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরপর প্রকাশিত ‘বেগম’ পত্রিকার শুরুতেই সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন ছাড়াও যে-কোনো অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সবসময় তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনিয়েছেন, মিছিল, মিটিং এ অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন এই প্রজন্মের সকল প্রগতিশীল মানুষের কাছে তাদের প্রিয় “খালাম্মা। এই নন্দিত, বরণীয়, স্মরণীয় কবি, সমাজসেবী, নারী জাগরণের নেত্রী ১৯৯৯ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশে-বিদেশে প্রায় চল্লিশটি পদক পান।
৯২) সেলিনা পারভীন (১৯৩১-১৯৭১) : মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে আলবদর বাহিনীর সহযোগিতায় পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদদের তালিকা তৈরি করে এবং তাঁদের হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করে এক-এক করে তাঁদের ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। নিহত এইসব বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই পুরুষ। বেয়নেট ও গুলিবিদ্ধ মৃত এই দেশজ মহামূল্যবান মানবসম্পদদের বদ্ধভূমিতে যখন আবিষ্কার করা হলো, সাহসী সাংবাদিক, সাহসী বক্তা ও রাজনৈতিক সচেতন কবি সেলিনা পারভীনের ক্ষতবিক্ষত দেহও সেখানে পড়ে ছিল। তাঁকেও তাঁর বাসা থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছিল। সদ্য স্বাধীন নতুন দেশে যাঁদের গঠনমূলক ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা ছিল, বেছে বেছে তাদেরই শেষ মুহূর্তে খুন করা হয়েছিল। সেলিনা পারভীন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমা।
শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন ১৯৩১ সালে ফেনীতে এক স্কুলশিক্ষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য সংস্কার অনুসারে মাত্র ১৪ বছর বয়সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় সেলিনার। তখন থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেন। সমসাময়িক বিষয়, নিজের গল্প, কবিতা প্রভৃতি। দশ বছর পরে সেই বিয়ে ভেঙে যায়। সেলিনা অতঃপর ঢাকায় চলে আসেন। এক রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে আবার তাঁর বিয়ে হয়। ঢাকায় এসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের পরিচালক হিসেবে প্রথমে চাকরি পান। পরে সেখানে বনিবনা না হওয়ায় তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত আকতার হোসেন সম্পাদিত মেয়েদের পত্রিকা ‘ললনা’-র সঙ্গে যুক্ত হন। বিজ্ঞাপন জোগাড় করা, অর্থ সংগ্রহ, হিসাবরক্ষণ, বিভিন্ন বিল পরিশোধসহ কাগজের আর্থিক দিকটা সামলানোর ভার তার ওপরে ছিল। যখন ‘ললনা’ ১৯৬৯ সালে বন্ধ হয়ে গেল, তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কিছু ঋণ নিয়ে ‘শিলালিপি’ নামে একটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির সাহিত্য ম্যাগাজিন বের করতে শুরু করলেন নিজেই। সেই কাগজে তখনকার ঢাকার উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিকই নিয়মিত লিখতেন। দেশের বিখ্যাত সব বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় তখন। তিনি নিজেও লিখতে শুরু করেন। প্রধানত কবিতা। সেই সময় রাজনীতিতে উত্তাল দেশে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে এবং একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ ছাড়াও একাত্তরে তাঁর কাছে মুক্তিযোদ্ধারা আসতেন মাঝে মাঝে। কিছু অর্থ, ওষুধ, শুকনো খাবার দিয়ে দিতেন সেলিনা। ১৯৭১-এর ১৩ ডিসেম্বর, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাত্র তিন দিন আগে, সেলিনা পারভীনকে কয়েকজন লোক এসে বাড়ি থেকে জিপে করে তুলে নিয়ে যায়। পরে, ১৮ ডিসেম্বর, তাঁর গুলিবিদ্ধ ও বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো রক্তাক্ত লাশটি বধ্যভূমিতে অন্য আরও অনেক শহীদ বুদ্ধিজীবীর দেহের সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়। সেই দিনই তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।
৯৩) সেলিনা বানু (১৯২৬-১৯৮৩) : বিপ্লবী জননেত্রী সেলিনা বানুর কর্মক্ষেত্র যেমন ছিল পাবনা, তেমনই ছিল ঢাকা আবার কখনো কুমিল্লা। সবচেয়ে বড় কথা হলো সেলিনা বানু ছিলেন গণমানুষের নেতা। দরিদ্র জনগণের নেতা। তাঁর পৈতৃক বাড়ি পাবনাতে। তখন সমাজটি ছিল অত্যন্ত পশ্চাৎপদ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই সামাজিক পটভূমিতে সেলিনা বানু অনেককেই চমকে দেন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, ১৯৫১ সালের দিকে। পাবনার নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বনমালী ইনস্টিটিউটের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে হঠাৎ ঘোষণা করা হলো সভাপতি হিসেবে বনমালী ইনস্টিটিউটের সভাপতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মাহতাব উদ্দিন সরকারের নাম। হলটিতে লোক সমাগম ভালোই হয়েছিল। অবশ্য মহিলা দর্শকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্যভাবেই কম। সেলিনা বানু সামনের সারিতেই বসেছিলেন। সভাপতি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য বলার জন্য দাঁড়ানো মাত্রই একজন মহিলা সামনের সারি থেকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং তাঁর কণ্ঠের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, “রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্যাপনের নামে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি উপযুক্ত সম্মান না দেখিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে উচ্চাসনে বসিয়ে বিশাল একটি মালা দিয়ে মাল্যভূষিত করা হয়েছে আর মঞ্চের মেঝেতে রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট একটি ছবিতে কটি ফুল দিয়ে গাঁথা মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এভাবেই রবীন্দ্রনাথকে অপমানিত করা হয়েছে। তাই এ জাতীয় অনুষ্ঠানে আমি থাকতে পারি না”- এই কথা কটি বলেই হনহন করে মহিলাটি বেরিয়ে গেলেন। অপরদিকে সমগ্র হলটিতে নেমে এলো পিনপতন নীরবতা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্য অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাটিকে বসতে বললেন আর নিজের গলার মালাটি খুলে পরিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের ছবিটিতে। অতঃপর কিছু দর্শক হাততালি দিয়ে নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়লেন। যাঁরা তাঁকে চেনেন না, একে অন্যের মুখ্র দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখে মুখে জিজ্ঞাসা, ‘ভদ্র মহিলাটি কে ?’ অনেকেই বলে উঠলেন, ‘সেলিনা বানু— পাবনার প্রখ্যাত জননেতা খান বাহাদুর ওয়াছিম উদ্দিনের দুঃসাহসী কন্যা।’ সেলিনা বানুর জন্ম হয়েছিল ১৯২৬ সালের ১৩ অক্টোবর এবং তিনিই হলেন পাবনার প্রথম মুসলিম মহিলা, যিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে বিএসসি পাস করেন। কলেজ জীবনে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্ট ছাত্রফেডারেশনের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য ও নেত্রী এবং পরে তিনি তাঁর কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও সাহসিকতার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গৌরবের সঙ্গে অর্জন করেছিলেন। ইতিমধ্যে পার্টির নির্দেশক্রমেই সেলিনা বানু আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের মহিলা সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে পার্টির নির্দেশে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন এবং মনোনয়ন পান। কিন্তু অকস্মাৎ দেখা গেল যুক্তফ্রন্টের মনোনীত নন এমন একজন অরাজনৈতিক মহিলাকে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন দেওয়া হলো, সেলিনা বানুর মনোনয়ন বাতিল করে। কারণ হলো, বৃহত্তম শরিক দল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যকার রাজনৈতিক মতপার্থক্য। মওলানা ভাসানী সমর্থন করতেন সেলিনা বানুকেই এবং সে কারণেই তিনি মনোনয়ন পেয়েও গিয়েছিলেন, কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো দক্ষিণপন্থী নেতা আমলাদের ধরপাকড়ের ফলে রাজশাহীর পুলিশ সুপারের অত্যাধুনিক স্ত্রীকে মনোনয়ন দেন। মহিলা প্রার্থীদের সংরক্ষিত নির্বাচনী এলাকা গঠিত হয়েছিল পৌর এলাকাগুলো নিয়ে। শেষে দেখা গেল, বিশাল এক ব্যবধানে সেলিনা বানু নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীক ছাড়াই। বৃহত্তর ও প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ তাঁর সপক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালায়।
১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে আওয়ামী লীগে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মধ্যে প্রচুর বাক-বিতণ্ডা হয়। কারণ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগ পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও সাম্র্রাজ্যবাদবিরোধী পররাষ্ট্রনীতির দাবিতে অবিচল ছিল। দুই নেতার তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা না হওয়ায় কাউন্সিলরদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদের পর মওলানা ভাসানী অনুসারীরাই ভোটে জয়ী হন। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে।
এই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সোহরাওয়ার্দী অনুসারীরা মানলেন না, শেখ মুজিব ঢাকায় পাল্টা কাউন্সিল ডাকলেন কাগমারী কাউন্সিলে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাব দুটিকে কেন্দ্র করে। ফলে দলে ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে, মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করলেন। দেশব্যাপী ওই দুটি নীতির অনুসারী হাজার হাজার নেতাকর্মী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করলেন। সেলিনা বানু, অলি আহাদ, ভাষা মতিন প্রমুখও ওই একই সময় আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করলেন। পরিণতিতে ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে ঢাকায় এক নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন আহ্বান করলেন মওলানা ভাসানী। সেই কনভেনশনে সেলিনা বানুসহ পাবনা থেকে অনেকে, ঢাকা শহরসহ সমগ্র প্রদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশ থেকেই ট্রেন ও বিমানযোগে বহু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতা ও কর্মী যোগ দেন। এই কনভেনশনেই সারা পাকিস্তান ভিত্তিতে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক দল গঠিত হলো পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামে। মওলানা ভাসানী সর্বসম্মতিক্রমে ন্যাপের কেন্দ্রীয় ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। সেলিনা বানু নবগঠিত ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ন্যাপ গঠনের বছর দেড়েক যেতে না যেতেই এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন জারি করেন আইয়ুব খান। সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান বাতিল করা হয়, রাজনৈতিক দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। বছর কয়েকের মধ্যেই রুশ-চীন আদর্শগত দ্বন্দের ফলে ন্যাপে বিভক্তি আসে। চীনপন্থী গ্রুপটি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পিকিংপস্থী ন্যাপ নামে পরিচিতি লাভ করে। আর বৃহত্তর অংশটি সীমান্ত গান্ধী খান আবুল গাফফার খানের পুত্র খান আবদুল ওয়ালি খানের নেতৃত্বে কেন্দ্রে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হয়ে পরিচিত হয় মস্কোপন্থী ন্যাপ বলে। সেলিনা বানু পাবনা জেলা কমিটির সভাপতি এবং জননেতা বাদশা সম্পাদক। অতঃপর ১৯৭০-এর নির্বাচনে সেলিনা বানু জাতীয় পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু সেবার বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফার জোয়ারে দেশব্যাপী আওয়ামী লীগ প্রার্থীরাই শুধু নির্বাচিত হন। যা হোক, ১৯৭৩ সালে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সেলিনা বানু, আমিনুল ইসলাম বাদশা, নুরুজ্জামান বাবলু পৃথক পৃথক আসন থেকে ন্যাপের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর আগে, ১৯৭১ সালে তাঁর মেয়ে শিরীন বানু মিতিল পুরুষের বেশে অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে। মিতিলের যোদ্ধাবেশের ছবি কলকাতায় দৈনিক স্টেটসম্যান এবং আরও অনেক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। স্টেটসম্যানের পূর্বাঞ্চলীয় বিশেষ প্রতিনিধি তখন পাবনা এসেছিলেন এবং মিতিলের ছবি ও দীর্ঘ ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন, যা তাঁর পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। মিতিল তখন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রী, জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী। অতঃপর সেলিনা বানু স্বামী শাহজাহান ও কন্যা মিতিলকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বাকি সময়ের জন্যে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।
৯৪) স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) : রবীন্দ্রনাথের নদিদি স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক লেখিকা। তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, পত্রিকা সম্পাদক, সমাজসেবী ও প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী বলে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কোনো বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন তিনি করেন নি। কেশবচন্দ্র সেন এবং ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের পড়াতেন। এদের কাছে পাঠ নিয়ে স্বর্ণকুমারী বিদূষী হয়ে উঠেছিলেন। স্বর্ণকুমারীর বিয়ে হয়েছিল ১১ বছর বয়সে জমিদার জয়চন্দ্র ঘোষালের পুত্র জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে। তাঁর লেখা ‘দীপনির্বাণ’ বাংলা সাহিত্যে নারীরচিত প্রথম সার্থক উপন্যাস বলে পরিচিত। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে তিনি ‘সখি সমিতি’ নামে মেয়েদের জন্যে প্রথম একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় কংগ্রেসের অনতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। ‘দীপনির্বাণ’ ছাড়াও তিনি ‘স্নেহলতা’, ‘ফুলের মালা’, ‘কাহাকে’ বলে আরও তিনটি উপন্যাস রচনা করেন। এছাড়া তিনি দুটি নাটক লেখেন। ‘গাথা’, ‘বসন্ত উৎসব’ ও ‘গীতগুচ্ছ’ তাঁর কবিতাগ্রন্থের নাম। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি জগত্তারিণী স্মৃতি পদক লাভ করেন। তিনি ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই বিখ্যাত কন্যার নাম হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী চৌধুরানী। বিশেষ করে সরলা দেবী চৌধুরানী স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বনামধন্য নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ১৯৩২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
৯৫) সৈয়দা মোতাহেরা বানু (১৯০৬-১৯৭৩ সাল) : সৈয়দা মোতাহেরা বানু ১৯০৬ সালের নভেম্বর মাসে বরিশাল জেলার বামনা গ্রামে নানা মীর সরোয়ার জানের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শাহ সৈয়দ সাজ্জাদ মোজাফ্ফর। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের আপন ভাগ্নে এ. এন. এম ইউসুফ আলীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর থেকেই তিনি স্বামীর প্রবল উৎসাহে নিয়মিত কাব্যচর্চা শুরু করেন।
১৯১৯ সালের জুন মাসে মোতাহেরা বানু ‘খেলার সাথী’ নামক একটি কবিতা রচনা করেন, যা ‘সওগাত’ পত্রিকায় ছাপা হয়। তিনি প্রায় দেড়শত কবিতা রচনা করেন, যার মধ্য থেকে একশতের উপর ‘কাফেলা' নামক গ্রন্থে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। ‘সওগাতে’র মহিলা সংখ্যায় ১৩৩৬ সালে তাঁর ‘শাওন নিশিথ’, ১৩৩৭ সালে ‘অবেলায়’, ১৩৫২ সালে ‘হেমন্ত রজনী’ কবিতা প্রকাশিত হয়। সওগাত ছাড়া তাঁর কবিতা সাপ্তাহিক ‘বেগম’-এ নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। মোতাহেরা বানুই বাংলার মুসলিম কবিদের মধ্যে স্বভাবকবি হিসেবে খ্যাত। বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীমতি মোহিনী সেন গুপ্তা তাঁর ‘অধীরা’ ও ‘প্রতিক্ষা’ নামক কবিতা দুটিতে সুর সংযোজন করেন এবং পরে বিখ্যাত গায়ক কে, মল্লিকের কণ্ঠে এই গান গীত এবং রেকর্ড করা হয়েছিল। বাংলার মুসলমান মহিলা কবিদের মধ্যে তাঁর গানই প্রথম রেকর্ড করা হয়। ২০০১ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সাহিত্যে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করেন।
৯৬) হরিপ্রভা তাকেদা (মল্লিক) (১৮৯০-১৯৩২) : পুরোনো ঢাকার অধিবাসী শশিভূষণ মল্লিক ও নগেন্দ্রবালা দেবীর কন্যা হরিপ্রভা। ঢাকার বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরির এক সাধারণ কর্মচারী জাপানি তরুণ ওয়েমন তাকেদার সঙ্গে ১৯০৭ সালে বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পরে ওয়েমন নিজেই ‘ঢাকা সোপ ফ্যাক্টরি’ নামে একটি সাবানের কারখানা খোলেন। ওয়েমন বিয়ের কিছুদিন পর স্ত্রী হরিপ্রভাকে নিয়ে জাপান যান, তাঁর পিতামাতার সঙ্গে নববিবাহিতা স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে। হরিপ্রভা যাত্রাপথে বিশেষ বিশেষ ঘটনা, বিভিন্ন স্থানের নাম, কথা, ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, অন্যান্য জরুরি তথ্য সযত্নে ডায়েরিতে তুলে রাখেন যার ওপর ভিত্তি করে ‘বঙ্গ মহিলার জাপান যাত্রা’ রচনা করেন। পরে সেই পাণ্ডুলিপি থেকে ৬০ পৃষ্ঠার ছোট একখানি বই প্রকাশিত হয় এবং বাংলার নারীর ভ্রমণবৃত্তান্তের ওপর রচিত প্রাচীন লেখাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অর্থবহ ভ্রমণকাহিনি বলে গৃহিত হয়।
৯৭) হাজী সহিফা বানু ওরফে হাজী বিবি (১৮৫০-১৯১৭) : হাসন রাজার পিতা নাম দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী এবং মায়ের নাম হুরমত জাহান বিবি। আলী রাজার এক খালাত ভাই লক্ষ্মণশ্রীর জমিদার আমীর বখশ চৌধুরী বিরাট জমিদারিসহ অল্পবয়স্কা স্ত্রী হুরমত জাহান বেগমকে রেখে মারা গেলে আলী রাজা তাকে বিয়ে করেন। এই দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে হাসন রাজার জন্ম। আলী রাজার প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র দেওয়ান ওবায়দুর রাজা চৌধুরী হাসন রাজা থেকে বয়সে চৌত্রিশ বছরের বড় ছিলেন। আর এক মাত্র কন্যা হাজী সহিফা বানু ওরফে হাজীবিবি হাসন রাজার অল্প ছোট ছিলেন। হাজী বিবি কবি ছিলেন এবং দেওয়ান ওবায়দুর রাজা চৌধুরীও।
হাজী বিবির জন্ম ১৮৫০ সালে বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা গ্রামে। পিতা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী। তিনি মরমী কবি হাসন রাজার বৈমাত্রেয় বোন ছিলেন। সহিফা বানুর বড়ভাই ফারসি ভাষার একজন কবি ছিলেন। তার স্বামী আবদুল ওয়াহেদ ওরফে হাজী হিরন মিয়া শেখঘাট এলাকার কুয়ারপাড় নিবাসী আলী আমজাদ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। সেকালে অতি দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তিনি একাধিকবার হজ্জ পালন করায় ‘হাজী বিবি’ নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন।
সহিফা বানু বাংলা ও উর্দুতে কাব্য রচনা করতেন। তাঁর লেখায় হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্র অনুভূতি প্রকাশ পায়। নিঃসন্তান সহিফা বানু ১৯১৭ সালে ইন্তেকাল করেন। সহিফা বানুর বাংলায় রচিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে সহিফা সঙ্গীত’ ও ‘ছাহেবানের জারি’। উর্দুুতে রচিত গ্রন্থ ‘ইয়াদ গারে সহিফা’। তাঁর সহিফা সঙ্গীত গ্রন্থটি সিলেট থেকে ১৯০৭ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়। সহিফা বিবি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। বিবি সহিফা বানুর উর্দু-বাংলার বেপরোয়া মিশ্রণে কাব্য রচনা অনেককেই সচকিত করে তোলে। তার কবিতায় সে কালের সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে। সমাজের উদ্দেশে তিনি ব্যঙ্গ করে লিখেছেন :
ধনে জনে ভাল যারা, মিথ্যা
হইলে জয়ী তারা
দুঃখিত এতিম বিধবারা, তারা
জিতে মরা।
চোরা যারা, ভাল তারা, চোরা
ধনে বুক তার পুরা
টাকার বলে যা না ধরা কি
বুঝিবে বেচারীরা।
সহিফা ভাবিয়া বলে সারা
তেলেঙ্গী বিষম চোরা।
হাজী সহিফা বিবির কাব্যসমগ্র হয়তো সাহিত্যের বিচারে পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ বলে দাবি করা যায় না। কিন্তু তাঁর রচনার সুরমাধুরী সহজভাবে মনকে ছুঁয়ে যায়। যে কালে মেয়েরা কাব্যরচনার কথা দূরে থাক, তাদের লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না। সে সময় সহিফা বিবির এমন সাহিত্য রচনা কৃতিত্বের দাবি রাখে।
৯৮) হেনা দাস (১৯২৪-২০০৯) : ১৯২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সিলেট শহরের পুরান লেনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র দত্ত। মায়ের নাম মনোরমা দত্ত। স্বামী রোহিনী দাস।
তিনি এমএ ও বিএড ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন শিক্ষিকা ছিলেন। বেসরকারি শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী হেনা দাস ১২ বছর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মুখপত্র গণশিক্ষার তিনি সম্পাদক। বাংলার নারী জাগরণে যে ক’জন নারী তাঁদের সময়ের চেয়ে ছিলেন বেশি অগ্রসর এবং নারী প্রগতিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হেনা দাস। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা-আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ বাংলাদেশের সকল ক্রান্তিলগ্নে, সকল দুঃসময়ে, সমস্ত লড়াইতে তিনি সক্রিয় ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনেরও অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি একসময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং পার্টির হয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তখনই তার কমরেড রোহিনী দাসকে বিয়ে করেন। হেনা দাসের দুই কন্যা দীপা ইসলাম ও চম্পা জামান যথাক্রমে একজন ডাক্তার ও কম্পিউটার বিজ্ঞানী। ১৯৮৭ সালে স্বামী রোহিনী দাস মারা যান। হেনা দাস নারী প্রগতি ও নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে জীবনভর কাজ করেছেন। দেশের বিভিন্ন নারী আন্দোলনে ও নারীর শিক্ষা বিস্তারে হেনা দাস বরাবর সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। ২০০০ সালে তিনি বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালে এই বহুমুখী কর্মে তৎপর নারীর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : স্মৃতিময় দিনগুলো, স্মৃতিময় ’৭১, আমার শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন, উজ্জ্বল স্মৃতি, চার পুরুষের কাহিনী, নারী আন্দোলন : কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, নির্বাচিত প্রবন্ধ।
৯৯) হেমপ্রভা দেবী (১৮৮৮-১৯৬২) : নোয়াখালীর গগনচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা। হেমপ্রভা দেবী একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেত্রী ও সমাজসেবক। হেমপ্রভার স্বামী বসন্ত মজুমদার কুমিল্লার যুগান্তর পার্টির একজন বড় নেতা ছিলেন। ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগ দিয়েই হেমপ্রভা ঊর্মিলা দেবীর ‘নারী কর্ম মন্দিরে’র সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুবিধ কাজ ও সভা-সমিতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ান। ১৯২২ সালে নিজেই ‘মহিলা কর্মী সংসদ’ গঠন করেন। তাঁর দুই কন্যা শান্তিপ্রভা ও অরুণাসহ ১৯৩০ সালে আইন অমান্য করার অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং কারাবাস করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য হন। জানা মতে, তিনিই প্রহম নারী যিনি কোনো আইন সভার জন্য মনোনীত হন। ১৯৩৯ সালে হেমপ্রভা বঙ্গীয় ‘ফরোয়ার্ড ব্লকে’ যোগ দেন এবং নেতাজি সুভাষ বসুর অন্তর্ধানের পর দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর তিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গেই থেকে যান।
১০০) হোসনে আরা (১৯১৪-১৯৯৯) : চব্বিশ পরগনা জেলার পায়রা গ্রামে জন্ম। পিতা ছিলেন একজন পুঁথিসাহিত্যিক। চাচা স্বনামধন্য সর্বশ্রদ্ধেয় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। স্বামী সাহিত্যিক সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের। স্বামীর সঙ্গে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিতে কলকাতা চলে আসেন তরুণ গৃহবধূ শিশুসাহিত্যিক হোসনে আরা। তাঁর লেখা বিখ্যাত ছড়া ‘সফদার ডাক্তার’ বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং বহুবার কারাবরণ করেন। তিনি ভাষাআন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। কলকাতা যাওয়ার পরপরই তিনি যোগ দেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। সেদিন এক বিশাল মিছিল করে মনুমেন্টের দিকে যাচ্ছিল হাজার হাজার মানুষ। সেই মিছিলে বিরাট এক ব্যানার নিয়ে মিছিলের অগ্রভাগে হেঁটে যাচ্ছে, সরকারের আদেশ অগ্রাহ্য করে, সেদিনের মিছিলের সম্ভবত সর্বকনিষ্ঠা ও একমাত্র মুসলমান নারী সদস্য হোসনে আরা। ঘোড়ায় চড়ে এসে ইংরেজরা বাধা দেয় সে মিছিলে। হোসনে আরা প্রথম দিন মিছিলে এসে কারারুদ্ধ হন ছ’মাসের জন্যে। জেল খাটার পর সমাজে ফিরে গিয়ে বহুভাবে লাঞ্ছিত হতে হয় তাঁকে। কিন্তু নেতাজি ও কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে অভিনন্দিত করেন। জেলখানায় দেখা হয় বিপ্লবী শান্তিঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর সঙ্গে। কারাগারেই অসীম স্নেহ লাভ করেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক প্রফুল্ল সরকারের স্ত্রী নির্ঝরিণী সরকারের কাছ থেকে। স্বামীর উৎসাহে হোসনে আরা পড়াশোনা ও সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় ছড়া ‘সফদার ডাক্তার’—
সফদার ডাক্তার
মাথা ভরা টাক তার
খিদে পেলে পানি খায় চিবিয়ে।
চেয়ারেতে রাত দিন
বসে গুনে দুই তিন
পড়ে বই আলোটারে নিভিয়ে।
ইয়া বড় গোঁফ তার
নাই তার জুড়ি দার
শুলে তার ভুঁড়ি ঠেকে আকাশে।
নুন দিয়ে খায় পান
সারাক্ষণ গায় গান
বুদ্ধিতে অতি বড় পাকা সে।
রোগী এলে ঘরে তার
খুশিতে সে চার বার
কষে দেয় ডন আর কুস্তি।
হোসনে আরা বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রবর্তনের পরপরই শিশুসাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। তাছাড়া তিনি শিশু একাডেমি পুরস্কারও পান।









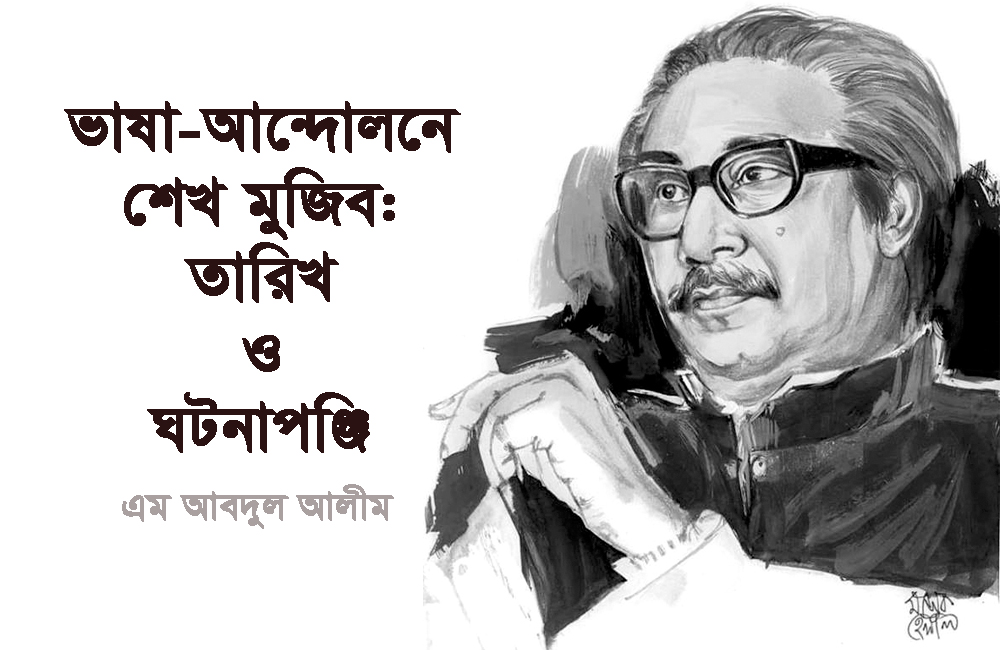

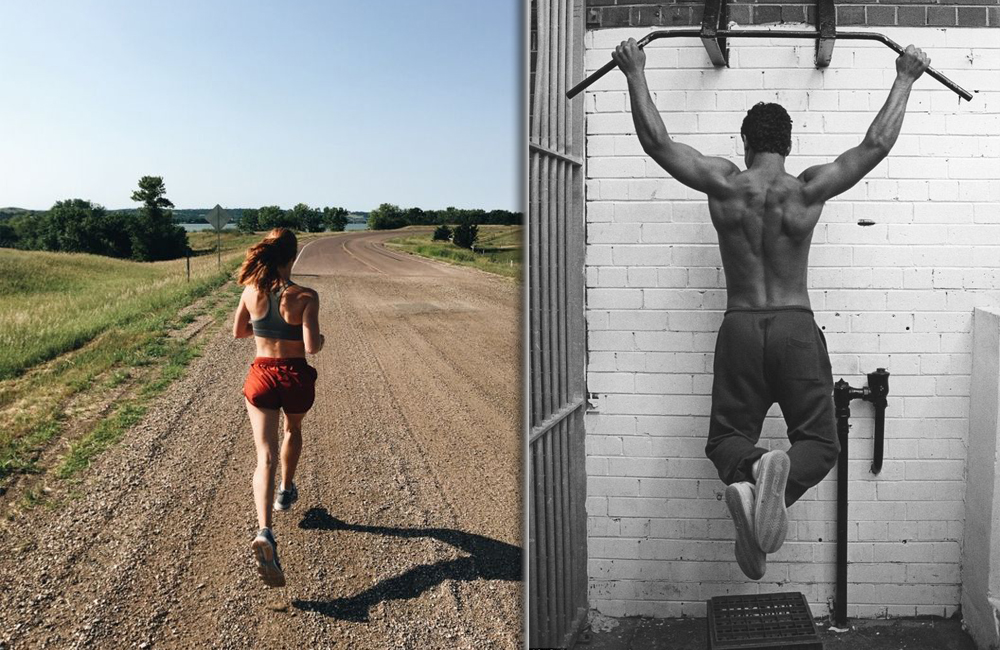


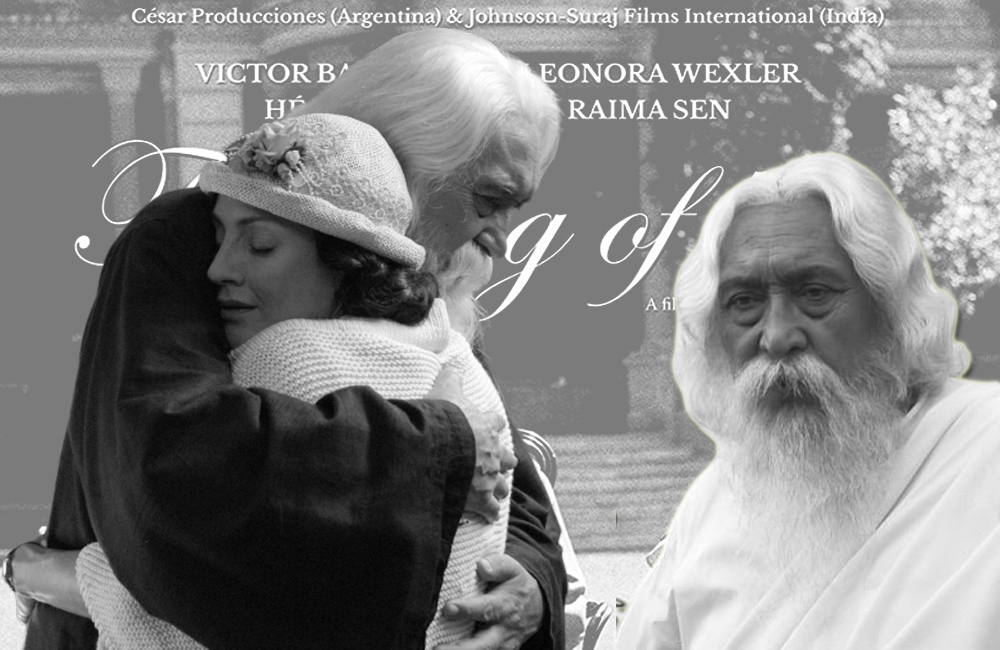
Leave a Reply
Your identity will not be published.