বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মুহম্মদ এনামুল হকের অবদান অতুলনীয়। বিশেষ করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক পুরোধা এবং নির্ভীক প্রবক্তা ছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। এদেশে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মÑ আবাহন (১৯২০-২১), ঝর্ণাধারা (১৯২৮), চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ (১৯৩৫), আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সঙ্গে একযোগে রচনা, ১৯৩৫), বঙ্গে সুফী প্রভাব (১৯৩৫), বাঙলা ভাষার সংস্কার (১৯৪৪), ব্যাকরণ মঞ্জরী (১৯৫২), মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৫৭), বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধান (স্বর বর্ণাংশ সম্পাদনা, ১৯৭৪), বুলগেরিয়া ভ্রমণ (১৯৭৮)। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর প্রয়াত এই জ্ঞানতাপসের ১২১তম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে এ রচনাটি পত্রস্থ হলো।
এবারে আমাদের গন্তব্য চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির বখতপুর গ্রাম। আলোকচিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ সরকার ও আমি এ উপলক্ষে চট্টগ্রামের বহদ্দার হাট থেকে উঠে পড়লাম ফটিকছড়ির উদ্দেশে। আমাদের যিনি পথনির্দেশ দিচ্ছিলেন তিনি বারবার বলে দিয়েছিলেন ফটিকছড়ি যেতে। ফটিকছড়ির কিছুদূর আগে একটা স্টেশন আছে, নাম নানুপুর। সেখানে একট সিনেমাহল রয়েছে। ওই সিনেমাহলের পাশের রাস্তা দিয়ে চান্দের গাড়িতে করে যেতে হবে বখতপুর বাজারে। ওখান থেকে রিকশায় আমরা যাব বাজারের অদূরেই ছায়াঢাকা, পাখিডাকা একটি বাড়ি। যেখানে জন্মেছিলেন প্রখ্যাত মনীষী ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।
মুহম্মদ এনামুল হকের নামের সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে নামটি একাকার হয়ে মিশে আছে সেটা হচ্ছে বাংলা অভিধান। বস্তুত অভিধান একটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ও অনবরত শব্দ যোজনাগত কর্মপ্রয়াস। বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে এই সংযোজনা বা সংস্করণ রীতিটি ছিল বিচিত্র এবং বিশেষত ১৯ শতকে ছিল পরিকল্পনাহীন। ভাওয়ালের গির্জা কিংবা গড় উইলিয়ামের দেওয়াল থেকে বেরিয়ে বাংলা একাডেমির চত্বর পর্যন্ত দীর্ঘ পথযাত্রায় বাংলা অভিধানের সঞ্চয় তাই একপেশে মাত্র। বলা যায় সংস্কৃত ঘেঁষা। ক্রমে সংস্কৃত অভিধানের আদর্শ, আরবি ভাব প্রণালি এবং জনসনের ইংরেজি অভিধানের আদর্শের দ্বন্দ্ব পেরিয়ে ঘটে বিংশ শতকের পদাপাত, রামেন্দু সুন্দর ত্রিবেদী বা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যেখানে সকল শব্দের সকল ঐতিহ্যের ও সকল আদর্শের এক মহামিলনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এরপরে আসে জ্ঞান্দ্র মোহন-হরিচরণ, আসে রাজশেখর বসুর চলন্তিকা ও তার নবসজ্জা।
এছাড়া দেশজ শব্দের প্রতি অনীহা আরবি-ফারসি শব্দের ঐতিহ্য বিষয়ে সন্দেহ, বিদেশি শব্দের প্রতি যত্নশীলতা। শুধু সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ শব্দের সংগ্রহ প্রীতি অথবা শুধু বাংলা শব্দের সংকলন ইত্যাদিতে একরূপ দ্বন্দ্বমূলক চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যেত। তেমনি বানানের ক্ষেত্রেও এবং শব্দের প্রধান অর্থ বা প্রতিশব্দাদি প্রদানের ক্ষেত্রেও অভিধানে সমাদর্শ অনুসৃত হতো না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো পরিকাঠামো নির্মাণের চিন্তাটি অনুপস্থিত ছিল। আবার ক্রম, বানান, অর্থ প্রদান, ব্যাকরণী বিবরণ বা পদপরিচয় দান, উদাহরণ উল্লেখ, ব্যুৎপত্তি প্রদান এমনকি দুই কলামে বিভক্ত প্রক্রিয়ায় সাজানো ও মূল ভুক্তিগুলি স্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত করার যেসব নীতি অভিধানে নানারূপ ভ্রান্তি সৃষ্টি করত জ্ঞানেন্দ্র মোহনে এসেই অভিধান প্রথম নির্ভরযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যায় এবং টাইপ ব্যবহারের ও প্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহারযোগ্যরূপ গ্রন্থের আকার নির্মাণে চলন্তিকা বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখে। সংসদ ও বাংলা একাডেমি এই নির্মাণের আধুনিক রূপ মাত্র। এই নতুন ধারা ও ঐতিহ্যকেই স্পষ্টতর করেন মুহম্মদ এনামুল হক।
মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর আরবি-ফারসি ও সংস্কৃত জ্ঞান, উপভাষিক প্রাদেশিক শব্দের ও বাংলাদেশের ভাষা পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও ভাষাভিত্তিক জ্ঞান এবং সর্বোপরি বাংলা ব্যাকরণে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি নিয়ে এই অভিধান সম্পাদন করেন। যার ফলে ইমেন্যু বর্ণিত ভালো ব্যাকরণ ও উপভাষিক তথ্য সাপেক্ষ অভিধানের সম্ভাব্য ফসল এখানে সুলভ হয়েছে, প্রণয়ন কৌশল ও নীতি হয়েছে সহজ, পূর্ববর্তী অভিধানসমূহের সংকীর্ণতা, একপেশিতা ও সীমাবদ্ধসমূহের স্বচ্ছন্দ বিদূরণ অপসারণ ঘটেছে অনায়াসে। এতে যেমন বর্ণমালার ক্রম, শব্দের বিন্যাস ও প্রধান অর্থের অবস্থান নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট হয়েছে তেমনি শব্দের শ্রেণিগত পরিচয় বুৎপত্তি পদপরিচয় ও অর্থায়নও ঘটেছে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ও একটি স্বচ্ছ বোধের মাধ্যমে। সেইসাথে মধ্যযুগের সমৃদ্ধ ভান্ডারটিকে এবং আরবি-ফারসি শব্দের অতুল ঐশ্বর্যকে এখানে প্রায় নতুনরূপে আবিষ্কার করেছেন। এই বিষয়গত সমৃদ্ধ ও ব্যবহারোপযোগিতার প্রশ্নটি তাই অনেক বিস্তৃত ও সম্ভাবনাময়। এনামুল হক এখানেই শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে বাঙালি মুসলিম সমাজের উত্থানলগ্নে এবং আরও স্পষ্ট ভাষায়, দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে তিনি এক অনিবার্য মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।
এই মহান পণ্ডিত বঙ্গভঙ্গের পূর্ব মুহূর্তে ১৯০২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম এবং স্বাধীন বাংলাদেশ পুনরায় স্বৈরাচারের কবলমুক্ত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ১৯৮২ সালের ১৬ ফেব্র“য়ারি তাঁর মৃত্যু। এই সময়ে এদেশে, এই বঙ্গভূমি স্বাধীন হয়েছে তিনবার—এদেশের জনমানসে পরিবর্তন ঘটেছে আমূল। এগুলির পেছনে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে এনামুল হকের ভূমিকা ছিল। তিনি পূর্ববাংলার শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর অন্যতম নির্মাতা। বাংলাভাষা ও সাহিত্য গবেষণায় আধুনিকতার অন্যতম পুরোধা।
তাঁর জীবন বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ঘুরপাক খেয়েছে। এনামুল হকের শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর পিতার হাতে। যখন তিনি নানুপুর মাইনর স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে নাম লেখান তখনই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। ১৯১৫ সালে মধ্য ইংরেজি বৃত্তি ও ১৯২০ সালে মহসিন বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ করে যখন চট্টগ্রাম কলেজে নাম লেখান, তখন চলছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল পর্ব। ফলে কৈশোরের উত্তেজনায় দেশমাতৃকার টানে তিনি যোগ দেন অসহযোগে, বর্জন করেন স্কুল ও বিলাতি পণ্য, ব্যবহার করেন খদ্দর, রচনা করেন স্বদেশী-সংগীত। এরপর ১৯২৫ সালে আইএ এবং ১৯২৭ সালে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বিএ পাস করেন। অতঃপর এমএ পড়তে কলকাতায় গিয়ে সংস্পর্শ লাভ করেন বাংলা সাহিত্যের দিকপাল দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯), ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০-১০৭৭)। তাঁরা মুহম্মদ এনামুল হককে ঠিকই চিনেছিলেন। এনামুল হককে তাঁরা বাংলা বিভাগে ভর্তি করেন। এই বিভাগ থেকে ১৯২৯ সালের এমএ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন, সাথে সাথে ভারতীয় সমুদয় ভাষার রেকর্ড মার্কসও তিনি পেয়ে যান।
সেই সময় এমএ শ্রেণির সিলেবাস ছিল বাংলা ৫০০ ও অন্যান্য অপ্রধান ভাষা ৩০০ নম্বরের। অপ্রধান ভাষায় উর্দু ছিল ২০০ এবং ফরাসি ও পালি ছিল ৫০ নাম্বার করে। মুহম্মদ এনামুল হকের ফলাফল ছিল বাংলায় ৭০%, উর্দুতে ৯০%, ফারসিতে ৯৬%। এই পরিমাণ নাম্বার তৎপূর্বে কেউ পান নি। বিস্ময়কর বদৌলতে তিনি গৌরবময় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরকারের উচ্চতর গবেষণা শিক্ষাবৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তিতে তিনি আচার্য সুনীতি কুমারের তত্ত্বাবধানে ১৯৩৪ সালে ‘ডক্টর অব ফিলসফি’ অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, বাংলায় সুফি প্রভাব। উল্লেখ্য যে, মুহম্মদ এনামুল হক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৭) থেকে ফিলসফি ডিগ্রি অর্জনকারী সর্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ ও প্রথম বাঙালি মুসলমান। এটা উল্লেখ এ জন্যেই প্রাসঙ্গিক যে, উচ্চতর আধুনিক শিক্ষায় বাঙালি মুসলমানদের গতি দ্রুত ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানপদ ‘রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক’ পদের গবেষণা সহকারী (১৯৩০-৩৫) হিসেবেও মুহম্মদ এনামুল হক একই সম্মানের দাবিদার।
মুহম্মদ এনামুল হকের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন সম্পর্কে সবাই কমবেশি ওয়াকিবহাল। ড. আহমদ শরীফের দৃষ্টিতে, তাঁর যোগ্যতায় দক্ষতায় বুদ্ধিমত্তায় ও ব্যক্তিত্বে আস্থা ছিল বলেই সব সরকার তাঁকে দায়িত্বপূর্ণ স্থানে বসিয়েছে। সরকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে বলতে হয়—এনামুল হক পাকিস্তান আমলের শেষার্ধে টিক্কা খানের রোষানল ও ব্রিটিশ আমলেও কর্মজীবনের সূচনায় ব্যাপক বিড়ম্বনার শিকার হন।
ব্রিটিশ আমলে তিনি কলকাতার ব্রিটিশ দফতরে একটি চাকুরি নিয়েছিলেন, কাজ ছিল রাজবন্দিদের চিঠি তরজমা। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তরজমাকৃত চিঠিগুলো ব্যবহৃত হয় দেশপ্রেমিক রাজবন্দিদের ফাঁসানোর কাজে; এটা বোঝা মাত্রই তিনি এ কাজ থেকে ইস্তফা দেন এবং শিক্ষকতাকে অনুকূল জ্ঞান করেন। এ ধারায় তিনি ১৯৩৬ সাল থেকে দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জোরারগঞ্জ, বারাসত, মালদা, হাওড়া ও ঢাকা কলেজিয়েটে প্রধান পদে কর্মরত থাকেন। দেশভাগের অব্যাবহিত পর এ দেশের শিক্ষা ও সমাজ অঙ্গনে ধর্মভিত্তিক এক নৈরাজ্য শুরু হয়। সেকালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অধিকাংশ ছিল অস্থির। কিন্তু তিনি ১৯৪৮ সালে রাজশাহী কলেজ, দৌলতপুর কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই শিক্ষক হিসেবে সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৪ সালে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে এতবার দ্রুত বদলির ধকল সামলাবার পর দায়িত্ব পড়ে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার, সেখানেও তিনি তৎপর ছিলেন।
১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে পূর্ববাংলা স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলা একাডেমি ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সূচক—কর্ণধার হিসেবে তাঁর ভূমিকা জাতীয় ইতিহাসের অঙ্গ। এরমধ্যে ১৯৬১ সাল থেকে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেও কাটান চার বছর। বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক হিসেবে ১৯৬৮ সালে তিনি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন।
বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই মনীষীর বাড়িতেই রয়েছে তাঁর কবর। তাঁর বাড়িতে যারা আছেন সবাই ভীষণ মুক্ত মনের মানুষ, তাদের আতিথেয়তা সে কথাই বলে। এনামুল হকের বাসভবন থেকে তাঁর নামে গড়া স্কুলের একাধিক ছবি তুলে ফেলে আলোকচিত্র শিকারি বিশ্বজিৎ। এর মধ্যে বৃষ্টি নামে। আমরা একটি চলন্ত চান্দের গাড়িতে উঠে পড়ি।





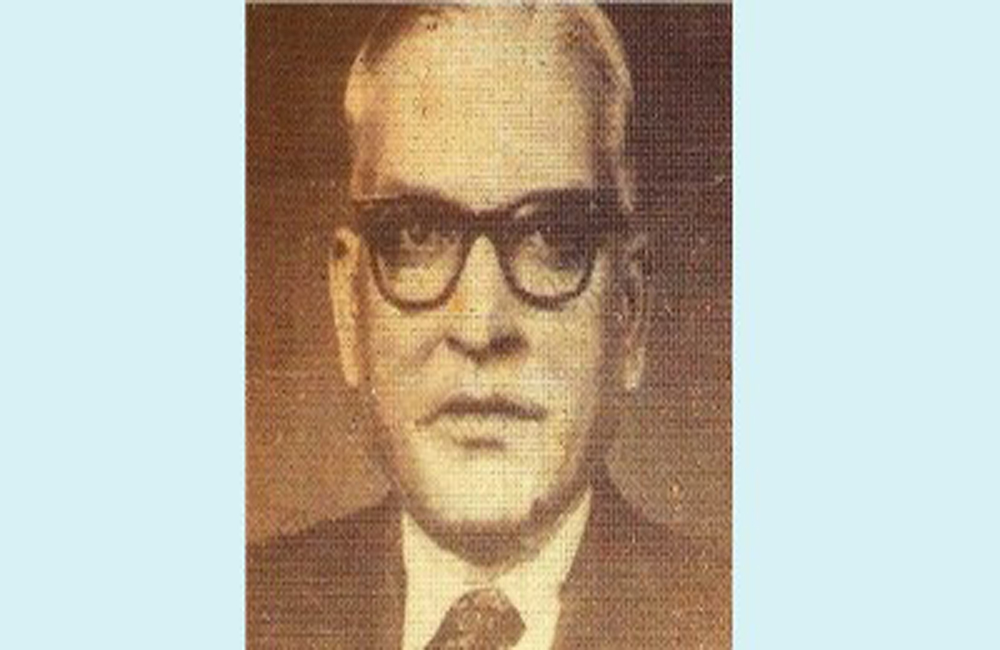
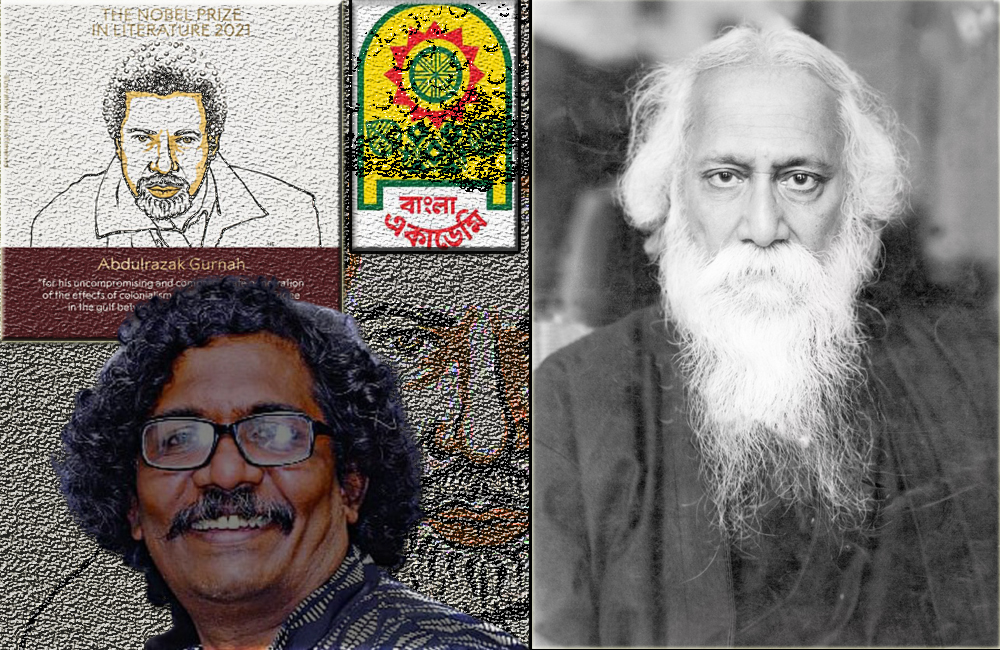
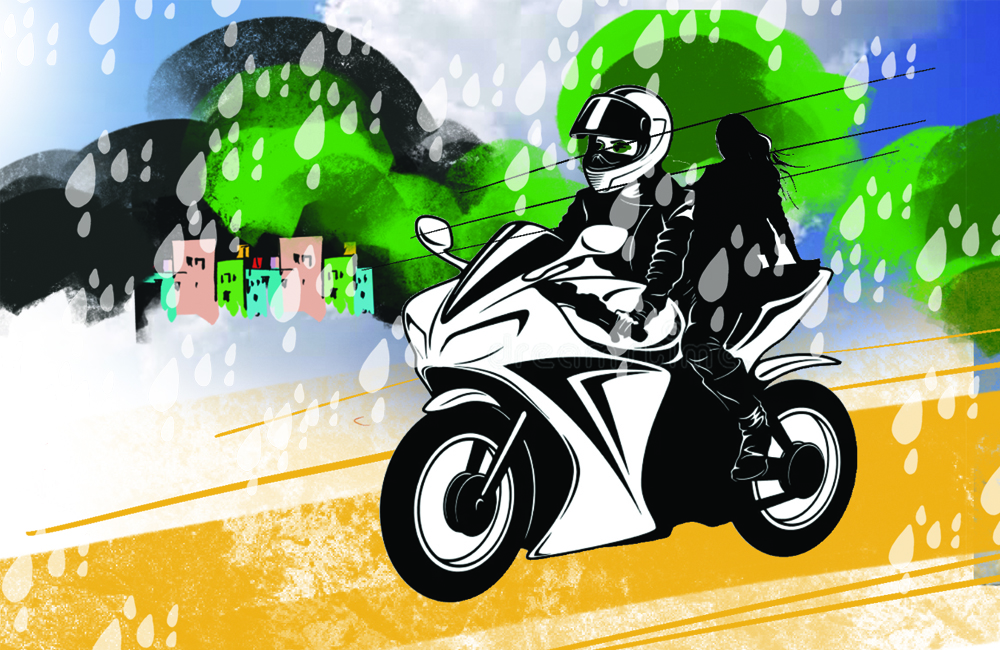







Leave a Reply
Your identity will not be published.