[বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীও রয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য ভুবন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সব ধরনের রচনাতেই নারীরা সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের সেইসব স্মরণীয় নারী এবং তাঁদের কীর্তির কথাই এই ধারাবাহিক রচনায় তুলে ধরা হয়েছে।]
বাংলার নারী জাগরণ/সমাজ উন্নয়নে স্মরণীয় নারী
ধর্ম ও পুরুষতন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট, কুসংস্কার-অশিক্ষার ভারে নত, বহু সন্তানের জননী, ভগ্নস্বাস্থ্য ভারতবর্ষের নারীর যে করুণ অবস্থা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, তার থেকে প্রথম মুক্তির আলোর যে সন্ধান পায় মেয়েরা, পায় বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার অর্জনের সুযোগ, তার পেছনে ছিলেন প্রধানত বাংলার দুই মহাপুরুষ—দুই নারীবাদী সমাজ সংস্কারক, রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—যাঁরা প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন মেয়েদের এই চরম দুরবস্থা, হীন অবস্থার পরিবর্তন করতে। রাজতন্ত্রে ইংরেজদের উপস্থিতি তাঁদের এই কঠিন প্রচেষ্টাকে সার্থক ও জয়ী হতে সাহায্য করেছে। ১৮১৮ সালে রামমোহন কলকাতায় সহমরণ এবং সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য জনমত তৈরি করেন, এবং ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিং কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই প্রথা বিলোপ করে আইন পাস করেন। আরেক মহান পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫০-৫৫ সালে বিধবা বিবাহের সপক্ষে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে ভারতবর্ষে বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়। বিধবা বিবাহের সামাজিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ১৮৬৭ সাল নাগাদ ৬০টি বিধবা বিবাহের আয়োজন করেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বাল্যবিবাহ-ও রোধ হয়। হুমায়ুন আজাদ ঠিকই বলেছিলেন, রামমোহন বাংলার মেয়েদের জীবন দান করেছিলেন, কিন্তু তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিদ্যাসাগর।
সম্ভ্রান্ত এক জমিদারের কন্যা নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বিশ শতকের আগে এ ধরনের বিদ্যালয়ে মুসলমান মেয়েরা যোগদান করে নি। ঢাকা কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী কিছুসংখ্যক মুসলিম ব্যক্তি উনিশ শতকের আশির দশকে ‘মুসলমান সুহূদ সম্মিলনী’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠন মেয়েদের জন্য ধর্মীয় নিয়মানুসারে গৃহশিক্ষার অনুকূলে মত প্রকাশ করে এবং এ আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি পাঠক্রম প্রস্তুত করে। এ ছাড়া বাড়িতে বাড়িতে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা এবং পরীক্ষা নেওয়ারও ব্যবস্থা করে। এর বিপরীতে মুসলমান বালিকাদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যিনি শুরু করেন তিনি হলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। সম্ভ্রান্ত জমিদার ঘরে জন্মগ্রহণকারী রোকেয়া তাঁর ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে গোপনে লেখাপড়া শিখেন। তাঁর ইংরেজি শিক্ষিত স্বামীও তাঁর শিক্ষার এ ধারাটি অব্যাহত রাখেন। বেগম রোকেয়ার স্বামী মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেন। রোকেয়ার অবিরাম পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে ১৯১১ সালে বাংলায় মুসলমান নারীদের জন্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল।
পর্দা ও অবগুণ্ঠনের ক্ষতিকারক দিকগুলো সম্পর্কে রোকেয়া শুধু অবগত ছিলেন না, এই সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন, লিখেছেন বিষদভাবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ১৯২৯ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত রচনা সংকলন ‘অবরোধবাসিনী’। অবগুণ্ঠনের বাড়াবাড়িকে তিনি যতই অপছন্দ করুন না কেন, রোকেয়া তাঁর স্কুলে বোরকাসহ পর্দার সকল নিয়মকানুন পালন করতেন। হয়তো একসঙ্গে অনেক জায়গায় ঘা দিতে গিয়ে সর্বত্র দুর্বলতার চিহ্ন রেখে যেতে চান নি তিনি। মেয়েদের স্কুলে পড়াশোনা করতে নিয়ে আসার জন্যে পর্দা যদি জরুরি হয়, সেটা মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হয়েছে তাঁর কাছে। তাঁর থেকে চার দশক আগে নবাব ফয়েজুন্নেসাকেও একই সমস্যার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুসলমান মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার অনুরোধ করতে নবাব ফয়েজুন্নেসা বোরকা পরে পাল্কিতে করে যাতায়াত করতেন। তিনি জানতেন তিনি নিজে যদি সমাজ দ্বারা পরিত্যক্ত হন, যত ভালো জিনিসই তিনি উপহার দিন না কেন, তা কখনো গ্রহণীয় হবে না।
কুমিল্লায় বহু রকমের সংস্কারের জন্যে একবার প্রচুর টাকার দরকার হয়েছিল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইংরেজ সাহেব সকল জমিদারের কাছে হাত পেতেও কিছু পান নি। ফয়েজুন্নেসা তখন তাঁর ভাণ্ডারে যে অর্থ তিনি রেখেছিলেন এ ধরনের প্রকল্প নিজে করবেন বলে, সে সব নগদ টাকা তুলে দেন সাহেবের হাতে। বলেন, কাজটাই আসল। সেটা আপনি সম্পন্ন করলে আমি খুশিই হব। তার এই অসামান্য দানশীলতার জন্যেই তিনি প্রথম এবং একমাত্র নারী যিনি ব্রিটিশ রানীর কাছ থেকে নবাব উপাধি অর্জন করেন।
বিশ শতকের শুরু থেকেই সামাজিক সংস্কারকে এগিয়ে নিতে বাংলার নারীরা তাদের নিজস্ব সংগঠন তৈরি করতে থাকে। সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫) ভারতীয় নারীদের জন্য একটি স্থায়ী সংঘের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ‘স্ত্রী মহামণ্ডল’ নামক তাঁর সংগঠন ১৯১০ সালে এলাহাবাদে প্রথম সভায় মিলিত হয়। সংগঠনটি শিগগিরই বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর ও কলকাতাসহ ভারতের অন্যান্য নগরীতে এর শাখা গড়ে তোলে। এ সংগঠনটির উদ্যোগের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল নারীশিক্ষা এবং যেসব শিক্ষক নারীদের তাদের বাড়িতে গিয়ে পড়া, লেখা, সংগীত, সেলাই ও এমব্রয়ডারি শিক্ষা দিত তাদের এ সংগঠন আর্থিক সহায়তা দিত। সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত মুসলিম নারীদের মাঝে কাজ করার জন্য ১৯১৬ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। একই সময় বাংলায় নারীদের ইনস্টিটিউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সরোজ নলিনী দত্ত (১৮৮৭-১৯২৫) জেলা শহরগুলোতে মহিলা সমিতি সংগঠিত করেন।
বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে সর্বভারতীয় নারী সংগঠনগুলো আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে, যেখানে বাংলার নারীরাও যোগদান করে। দি ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন ইন ইন্ডিয়া এবং অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স —দুটি সংগঠনেরই বাংলায় শাখা ছিল এবং বাংলার নারীরা সেগুলোর জাতীয় কাউন্সিল ও কমিটিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। লতিকা ঘোষ (জন্ম ১৯০২) কর্তৃক ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ ছিল বাংলার নারীদের রাজনীতিতে সংগঠিত করার প্রথম নিয়মমাফিক সংগঠন। ওই বছর কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শোভাযাত্রায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের মার্চ করে যাওয়ার জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল গঠনের জন্য সুভাষচন্দ্র বসু লতিকাকে অনুরোধ করেন। লতিকা বেথুন কলেজ ও ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের ছাত্রী এবং কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষিকাদের নিয়ে ৩০০ নারীর একটি দল গঠন করেন। পরের বছর (১৯২৯) জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য নারীদের প্রস্তুত থাকতে কংগ্রেসের আহ্বানে কলকাতার নারীরা নারী সত্যাগ্রহ সমিতি গঠন করে। আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে নারীরা লবণ তৈরি ও বিক্রয় করে, দেশিয় পণ্যের প্রচার করে, বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং চালায়, খদ্দরের উপযোগিতা সম্পর্কে বক্তৃতা করে এবং শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।
নারীর অগ্রগতির আরেক বাহক সাময়িকপত্রগুলো, বিশেষ করে নারীকল্যাণ ও প্রগতিতে নিবেদিত ও নারী-সম্পাদিত (পরিশিষ্টের তালিকা)। এই ধরনের পত্রিকা সম্পাদনা করে অথবা সম্পাদনা বিভাগে কাজ করে অনেক নারী সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ পান, শিক্ষিত নারীরা নতুন আয়ের পথ, বাইরে কাজের জায়গা খুঁজে পান, সাময়িকপত্রের লেখা বিষয় ও নারীদের মন খুলে নিজেদের কথা ও সমস্যা ভাগাভাগি করে নেওয়ার এই সুযোগ ও বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ উপদেশ ও পরামর্শ নারীর সৃজনশীল চর্চায় প্রভূত সাহায্য করে। কেননা সাধারণ দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি তখনো হাতেগোনা। পশ্চিম বাংলার কবিতা সিংহ ও বাংলাদেশের লায়লা সামাদের মতো সাহসী ও অগ্রসর নারীরাও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন, খবরের কাগজের অফিসে দীর্ঘ দিবসব্যাপী সকল পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে একা মেয়ে কাজ করে যাওয়া কত কঠিন। বাংলার প্রথম দিকের সাংবাদিক কবিতা সিংহ বলেছেন, মেয়েদের জন্য কোনো ভিন্ন বাথরুম না থাকায় কী যে অসুবিধা হতো সারা দিন ধরে দাঁড়িয়ে বা ছোটাছুটি করে কাজ করতে! কবিতা সিংহ অবশ্য পরের দিকে প্রিন্ট মিডিয়া ছেড়ে দিয়ে আকাশবাণী কলকাতায় কাজ করেছেন সাংবাদিকতায়; কিন্তু কাজের পরিবেশ বা সুযোগ-সুবিধা সেখানেও ছিল অপ্রতুল।
একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ওপার বাংলায় শরণার্থীদের জন্যে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরিতে পশ্চিমবাংলার যে নারী লেখক ও সমাজকর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁদের মধ্যে মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরী আইয়ুব, লীলা রায় (অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রী) ও মহাশ্বেতা দেবীর নাম উল্লেখ্যনীয়। স্বাধীনতার পরে দেশ পুনর্গঠনে, ধর্ষিতা মেয়েদের পুনর্বাসনে ও মেয়েদের অধিকার রক্ষায় ও জাগরণে বাংলাদেশে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহীম, জাহানারা ইমাম, হামিদা হোসেনের অবদান স্মরণ না করে উপায় নেই। জাতীয় মহিলা পরিষদের নেত্রীগণ যেমন আয়েশা খানম, মালেকা বেগম, হেনা দাস, নূরজাহান মুরশিদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বিরুদ্ধে ও শান্তির সপক্ষে অবস্থান নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে আসেন দুই বাংলার নারী সংগঠনগুলো। ব্যক্তি পর্যায়ে মৈত্রেয়ী দেবী কেবল দাঙ্গার সময়টুকুতে নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাড়াবার লক্ষ্যে ‘নবজাতক’সহ দুটি কাগজ প্রকাশ করতে শুরু করেন ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর, যা আজীবন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে গেছেন।
বাংলায় তথা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে নারী আন্দোলনের ভিত্তি হচ্ছে স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষার বড় অন্তরায় ছিল বাল্যবিবাহ। প্রথম দিকে বাঙালি মেয়েদের শিক্ষাদানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন মিশনারিগণ ও ব্রাহ্মসমাজ। তারা নারীদের ঘর থেকে বের করে আনতে ও মৌলিক শিক্ষা দিতে ১৮১৮-১৮২৮ সালের মধ্যে কলকাতা শহরে ও আশপাশে অনেকগুলো স্কুল খোলেন। নারী শিক্ষায় বাঙালি নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে কলকাতা ভিক্টোরিয়া গার্লস হাই স্কুল, যা ১৮৪৯-তে স্থাপিত হয় এবং পরে প্রতিষ্ঠাতা বেথুনের নামানুসারে প্রতিষ্ঠানটি বেথুন স্কুল নামে পরিচিত হয়। বিক্রমপুরের নারী কল্যাণে নিবেদিত-প্রাণ অক্সফোর্ডের মেধাবী ছাত্র বেথুন ১৮৪৮-এ ভারতে আসেন এবং তার সমস্ত সম্পদ স্কুলটির পেছনে ব্যয় করেন। এই বেথুন স্কুলই পরে বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয়, যা বাংলার মেয়েদের কাছে উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলে দেয়। এ ছাড়া দুর্গামোহন দাশ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ভগবান চন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় বেনী পুকুরে ১৮৭৬ সালে যে হিন্দু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, যা পরে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় হয়, সেই স্কুলও বেথুন স্কুলের সঙ্গে মিশে গিয়ে বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয়। আসলে যা ঘটেছিল সেটা এরকম। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় নামে এই বেসরকারি স্কুলটি প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই নারীদের উচ্চ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ওদিকে সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেথুন বিদ্যালয়ের অবস্থা তখন বড় শোচনীয়। তাই এর উন্নতিকল্পে বেথুন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এবং বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে বেথুন স্কুল ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় একত্রিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বেথুন কলেজ যে এতটা জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তার নেপথ্য কাহিনি এটাই। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে দুর্গামোহন দাশ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, শিবরাম শাস্ত্রী, রাজা রাধাকান্তদেবসহ আরও বেশ কিছু ব্যক্তির মনোভাব ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক, বলা চলে বিপ্লবী। কেশব চন্দ্র সেন কয়েকজন শিষ্যসহ উমেশচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে ১৮৬৩ সালে ‘বামাবোধিনীসভা’ স্থাপন করেন। ওই বছরই তারা ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙালি নারী আন্দোলনে এ পত্রিকাটি অসামান্য ভূমিকা রাখে। ১৮৬৯ সালে কেশব চন্দ্র সেন ঢাকায় আসেন। তার সহযোগিতায় ১৮৭১ সালে ‘ঢাকা শুভসাধনী’ নামে আরেকটি সমাজসংস্কারক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সভার উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে ঢাকায় প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করা হয়। ১৮৭৬ সালে মেরিকার্পেন্টার ঢাকায় এসে সেই স্কুলটি পরিদর্শন করেন। স্কুলের ব্যবস্থাপনা দেখে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হন। প্রতিষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তিনি সরকারের কাছে একটি চিঠি লিখেন। সেই প্রশংসাপত্রের সুবাদে সরকার ১৮৭৮ সালের জুন মাসে এটিকে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে। লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ করা হয় ইডেন গার্লস হাই স্কুল। সেই স্কুলটিই আজকের ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ইডেন কলেজ। নারী শিক্ষার বিস্তারে বহু নারী নেত্রী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। এঁদের মধ্যে লীলা নাগ, দাশ ভগিনী (দুর্গামোহন দাশের দুই কন্যা), অবলা দাশ (বসু) ও সরলা দাশ (রায়), স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা সরলা দেবী চৌধুরানী ও হিরন্ময়ী দেবী, বেগম রোকেয়া, নবাব ফয়েজুন্নেসা, ইলা মিত্র, দুর্গামোহন দাশ, ভগবান চন্দ্র বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল বিপ্লবী নেতাগণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি বিশেষ ভূমিকা রাখে।
বাংলায় প্রথম নারীবাদী সংগঠন ‘সখি সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ১৮৮৫ সালে তিনি লাঠি এবং অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারের চেষ্টা করেন। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে সরোজিনী নাইডু ও সরলা দেবী চৌধুরানী যোগ দেন। এই দুই নারী নেত্রী কংগ্রেসের বিভিন্ন ইউনিটে সভা প্রধানের পদেও উন্নীত হন। ১৯২৫ সালে বিক্রমপুরের অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সরোজিনী নাইডু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। বাংলায় প্রথম নারীবাদী হিসেবে খ্যাতি পান সরলা দেবী চৌধুরানী। তিনি ১৯১০ সালে সর্বভারতীয় নারী সংগঠন ‘স্ত্রী মহামণ্ডল’ প্রতিষ্ঠা করেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ‘স্ত্রী জাতির অবনতি’ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলায় এক অসাধারণ নারীবাদীর উত্থান ঘটে, যাঁর নাম বেগম রোকেয়া। তিনি লিখেছেন, ‘এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে আমরা কি ? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি না।’ সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত ও সরলা দেবী বাংলার নারী আন্দোলনের জননী। নবাব ফয়েজুন্নেসা ও বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষ করে মুসলমান নারীদের শিক্ষাদানের জন্যে স্কুল স্থাপন করেন। লীলা নাগ তাঁর দীপালী সংঘের মাধ্যমে ৩৩টি প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন ঢাকা শহরে। এছাড়া নারী শিক্ষা মন্দির ও শিক্ষাভবনও প্রতিষ্ঠা করেন। কাদম্বিনী বসু, চন্দ্রমুখী বসু, তাঁর বোন বিধুমুখী বসু, অবলা বসু, কামিনী রায়, মেরী ভার্জিনিয়া মিত্র, লীলা নাগ, ফজিলাতুন্নেসার মতো শিক্ষার্থীরা প্রথম এগিয়ে আসেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে। কেবল নারীদের সেবাদান করার জন্যে নবাব ফয়েজুন্নেসা কুমিল্লায় একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন জেনানা হাসপাতাল এই নামে। ওই সময় বেশ কিছু প্রধানত নারী-সম্পাদিত নারীবান্ধব প্রগতিশীল সাময়িকপত্র (পরিশিষ্ট) ও নারীনেত্রী পরিচালিত কিছু সংগঠন নারী-কল্যাণ ও স্ত্রী-শিক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে যতই বিরুদ্ধাচরণ করেন না কেন পুরুষরা, ধীরে ধীরে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার মেনে নিতে তাঁরা বাধ্য হন। কিন্তু নারীদের বাইরে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়া মেনে নিতে আরও বহুদিন সময় লাগে। মেয়েদের পড়ালেখার উপযোগিতা ছিল কেবল শিক্ষিত স্বামীদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জনের জন্যে। স্ত্রী শিক্ষিত হলে সে স্বামীর কাছে উন্নত মানের সঙ্গী হতে পারে, দিতে পারে স্বামীকে তাঁর কাজে এবং ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট উদ্দীপনা। নিজের বুদ্ধি ও চর্চিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে, সুন্দর বাচনভঙ্গি রপ্ত করে স্বামীর জীবনকে করে তুলতে পারে যথেষ্ট আনন্দকর ও উপভোগ্য। আর এসবই ছিল নারী শিক্ষা সমর্থনের পেছনের কারণ। সন্তানের প্রাথমিক পড়ালেখাটাও সহজে নিশ্চিত করা যাবে ঘরে শিক্ষিত স্ত্রী থাকলে—একথাটাও মনে ধরেছিল কারও কারও। কিন্তু পড়াশোনা করার মাধ্যমে নারী যে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে, তাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়তে পারে, পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, এসব কথা কারও মনে আসে না। ১৮৮২ সালে বহু চেষ্টা করেও দ্বারকানাথ ও দুর্গামোহন দাশ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অবলা দাশ (বসু)-কে ভর্তি করাতে পারলেন না। মেডিকেল কলেজের দরজা কিছুতেই খুলবে না মেয়েদের জন্যে। কিন্তু ১৮৮৩ সালে দ্বারকানাথের অসীম মনোবলের কাছে মাথা নত করে কর্তৃপক্ষ। কাদম্বিনী দেবীই প্রথম নারী যে বাংলার মেডিকেল কলেজে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হওয়ার অনুমতি পান। মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার আগেই, কাদম্বিনীর থেকে বয়সে ১৬ বছরের বড় বিপত্নীক শিক্ষক দ্বারকানাথের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিয়ে হয়। মেডিকেল কলেজে জোর করে পড়তে আসার ব্যাপারটা গোড়া হিন্দু শিক্ষকদের পছন্দ হয় না। তাঁদের একজন ফাইনাল পরীক্ষায় মেডিসিনের প্রাকটিকেলে ১ নম্বরের জন্যে কাদম্বিনীকে ফেল করিয়ে দেন যাতে ডাক্তারি পাস করতে না পারেন কাদম্বিনী। কিন্তু অধ্যক্ষ ইংরেজ সাহেবের সদিচ্ছায় কাদম্বিনীকে এম.বি. ডিগ্রি দিতে না পারলেও মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের তরফ থেকে একটি বিশেষ সার্টিফিকেট (এৎধফঁধঃব ড়ভ ইবহমধষ গবফরপধষ ঈড়ষষবমব বা এইগঈ) দেওয়া হয় তাঁকে ১৮৮৬ সালে, যা দিয়ে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতে পারেন তিনি। সেই হিসেবে ভারতের মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করে প্রথম যে ভারতীয় নারী ডাক্তার হন এবং ডাক্তারি শাস্ত্র প্র্যাকটিস করার অধিকার অর্জন করেন, তিনি কাদম্বিনী বসু। কিন্তু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রায় কোথাও উল্লেখিত হয় না, আর সেটা হলো, সূত্র মতে মহারাষ্ট্রের আনন্দীবাই যোশী (১৮৬৬-১৮৮৭) যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো মেয়েদের মেডিকেল কলেজে (ডড়সবহ’ং গবফরপধষ ঈড়ষষবমব ড়ভ চবহহংুষাধহরধ) পড়াশোনা করে কাদম্বিনী যে বছর এইগঈ অর্জন করেন সেই বছরেই অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে (মতান্তরে ১৮৮৪ সালে) ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করেন। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, পাস করে দেশে ফেরার পরপরই যক্ষা রোগে মাত্র ২১ বছর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। মহারাষ্ট্রের সাধারণ একজন নারী কেবল স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় অসুস্থ শরীর নিয়ে কী অসাধারণ লড়াই করে আমেরিকায় পড়াশোনা করে ডাক্তার হন সে কাহিনি আজ রূপকথার মতো লাগে শুনতে। তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী যিনি উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকা যান। সম্ভবত প্রথম উপমহাদেশের নারী যিনি আমেরিকার মাটিতে পা রাখেন। ফলে কাদম্বিনী বাংলার প্রথম নারী ডাক্তার, ভারতবর্ষের মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশোনা করে প্রথম নারী ডাক্তার দুটো তথ্যই ঠিক। কিন্তু সাধারণভাবে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গা থেকে ভারতীয় মেয়েদের ডাক্তার হওয়ার প্রাথমিক লড়াইতে কাদম্বিনী অন্যতম প্রথম ডাক্তার। ভিন্নভাবে বলা চলে, আনন্দীবাঈ যোশী ও কাদম্বিনী দুজনেই ভারতের প্রথম নারী ডাক্তার—একজন বিদেশে পড়াশোনা করেন, আরেকজন করেন বাংলায়।।
একজন ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে এসে কাদম্বিনী লক্ষ করেন, কর্মক্ষেত্র শিক্ষাক্ষেত্র থেকে আরও কঠিন জায়গা। হাসপাতালে মাসে ৩০০ টাকার একটা চাকরি করতে গিয়ে কাদম্বিনী লক্ষ করেন, সেখানে কাদম্বিনীই একমাত্র দেশি ডাক্তার বাকি সব সাদা ডাক্তার—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। তারা কাদম্বিনীকে হাসপাতালের অন্য কাজে ব্যস্ত রাখেন, কিন্তু ডাক্তারের কাছে প্রথম ও প্রধান যে কাজ রোগী দেখা, তা কাদম্বিনীকে করতে দেন না। কাদম্বিনী রোগী দেখতে পারেন না। বাধ্য হয়ে কাদম্বিনী হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিয়ে প্রাইভেট প্র্যাক্টিস শুরু করেন, যার জন্যে রোগী দেখতে বাড়ি বাড়ি যেতে হতো তাকে। গোঁড়া হিন্দুরা ভালো চোখে দেখেন না এটা। এক খবরের কাগজের সম্পাদক তো পাঁচ সন্তানের জননী কাদম্বিনীকে রীতিমতো স্বৈরিণী আখ্যা দিয়ে লেখেন স্বামী এবং একগাদা ছেলেপুলে ঘরে রেখে সে দিব্যি দেহব্যবসা করে চলেছে। ব্যঙ্গরসাত্মক খবরটির সঙ্গে একটা কার্টুনও ছপা হয়েছিল, যেখানে দেখানো হয়েছে দ্বারকানাথের নাকের ভেতর দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছেন কাদম্বিনী। পেশায় এ ধরনের বাধা সহ্য করেন নি কাদম্বিনী। মানহানির মামলা করে জেল খাটিয়েছেন, আর্থিক দণ্ড দিতে বাধ্য করেছেন ‘বঙ্গবাসী’র সম্পাদক মহেশচন্দ্র পালকে। জেদি কাদম্বিনী তাঁর ডিগ্রি নিয়ে মানুষের মনে যে সন্দেহ তা দূর করার জন্যে ইংল্যান্ড গিয়ে পর পর তিনটি ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসেন। কাদম্বিনীই প্রথম ভারতীয় নারী ইংল্যান্ড থেকে তিনটি ডিগ্রিসহ যিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পরে ডাক্তারি পেশায় তাঁর যোগ্যতা নিয়ে আর প্রশ্ন ওঠে নি। বিশেষ করে নেপালের রাজমাতা যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কাদম্বিনীর ডাক এল একজন ডাক্তার হিসেবে তাঁর চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলার জন্যে। কাদম্বিনী তা করেন। এর জন্যে তাঁর সম্মানী ছাড়াও রাজপরিবার থেকে তাঁকে অনেক দামি দামি উপহার দেওয়া হয়েছিল। যেমন, দু’কুইন্টাল ওজনের রুপোর বাসন (রাজপরিবার থেকে খেতে দেওয়ার পর বাসন ফেরত নেওয়ার নিয়ম ছিল না), দুটো মস্ত হাতির দাঁত, একটা টাট্টু ঘোড়া, আর দেড় বছরের ছেলের জন্য রাজপোশাকের খুদে সংস্করণ। শুধু তাই নয় এর পরে আরও দেড় বছর তিনি নেপালের রাজপরিবারের ডাক্তার হিসেবে কাজ করেন। তারপর সেই চাকরিটি বিখ্যাত কবি কামিনী রায়ের ছোটবোন ডাক্তার যামিনী সেনের হাতে তুলে দিয়ে তিনি সার্বক্ষণিকভাবে নিজের প্র্যাক্টিসে মন দেন। এদিকে কাদম্বিনীর মতো যামিনী সেনকেও কেউ ডাক্তার হিসেবে গ্রাহ্য করত না, যতদিন পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ড গিয়ে এফআরসিএস করে দেশে না ফেরেন। যামিনী সেনই বাংলার নারীদের মধ্যে প্রথম এফআরসিএস। প্রথম দিকের অন্য দুই ডাক্তারের, বিধু মুখী ও ভারজিনিয়া মেরী মিত্রের, বাধা অপেক্ষাকৃত কম ছিল তারা খ্রিষ্টান ছিলেন বলে। তারপরেও তারা সাধারণত নারী রোগীই কেবল দেখতেন। আর যামিনী সেন তাঁর পেশা বজায় রাখতে গিয়ে সারাজীবন বিয়েই করতে পারেন নি। সম্প্রতি একটি বই বেরিয়েছে যেখানে বাংলার প্রথম এই চার নারীর ডাক্তারি পেশা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের দুঃসহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে। আরেকটি জিনিস লক্ষ করা গেছে যে প্রথম দিকের এইসব নারী যারা সকল বাধা উপেক্ষা করে উচ্চশিক্ষিত হয়েছিলেন, তারা সকলেই বেশি বয়সে বিয়ে করেন অথবা সারাজীবন অবিবাহিত থেকে যান। ফলে বোঝাই যায়, বিয়ে তখনকার দিনে নারীকে শিক্ষিত ও পেশাজীবী করে গড়ে তোলার অন্তরায় ছিল। অবলার বড়বোন সরলা দাশের উদাহরণ প্রযোজ্য এখানে। ড. গোলাম মুরশিদ তাঁর ‘হাজার বছরের বাংলা সংস্কৃতি’ বইয়ের ভেতর একটি টেবিল দেন যাতে তথ্য হিসেবে দেওয়া থাকে প্রথম দিকের এইসব নারীদের ডিগ্রি, পেশা ও বিয়ের সময় কনের বয়স। তাঁর টেবিলটার একটু পরিবর্ধন করা হলো তিনটি নাম ঢুকিয়ে—
কামিনী রায় ও বেগম রোকেয়ার মতো সাহসী, প্রগতিশীল, নারীবাদী লেখকেরা পর্যন্ত, যাদের স্বামীরাও তাদের পড়াশোনা ও লেখালেখিতে উৎসাহ যুগিয়েছেন, স্বামীর মৃত্যুর আগে বাইরে কাজ করতে যাওয়ার সুযোগ পান নি। মেয়েরা প্রথম যখন বাইরে কাজ করতে যাওয়ার অধিকার পেল, তখনো কাজ করত প্রথম প্রথম বিনা বেতনেই। মেয়েদের কাজের বিনিময়ে বেতন নেওয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক মনে করা হতো তখন। তাহলে পড়াশোনা কিসের জন্যে? লেখাপড়া, আদব-কায়দার দরকার সুশিক্ষিত স্বামীর পাশে যোগ্য স্ত্রী হিসেবে দাঁড়াবার জন্যে, একটি আদর্শ দম্পতি হিসেবে সমাজে নিজেদের শোভা বাড়াবার জন্যে। সুন্দর করে কথা বলা, মার্জিত চলফেরার জন্যে। শোনা যায় রাধামনি অথবা রাধারানী বলে কোনো নারী তিরিশ টাকা বেতনে (মতান্তরে চল্লিশ টাকা) প্রথম চাকরি নেন। আরও পরে বেতন নিয়ে কেবল শিক্ষিকার পেশা গ্রহণ করা নারীদের জন্যে জায়েজ হলো। এরপর ধীরে ধীরে মেনে নেওয়া হলো ডাক্তারি পেশা বিশেষ করে প্রসবসংক্রান্ত অথবা মেয়েলি অসুখের জটিলতায়। ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র ডাক্তার হয়েও সারা জীবন ধরে কেবল তাঁর স্বামীর নারী রোগীদের দেখেই ডাক্তারি পেশা বজায় রাখতে বাধ্য হন। বিধুমুখী বসু বিয়েই করেন নি।
সংকোচ পরিত্যাগ করে নির্দ্বিধায় নারী যাতে অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে, সেজন্য জ্ঞানদা দেবী নারীকে শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ পরার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করলেন। প্রকৃতপক্ষে শায়া ব্লাউজসহ সামনে কুচি দিয়ে শাড়ি পরে স্বচ্ছন্দে নারীরা বাইরে বেরুতে শিখল। জ্ঞানদা দেবী নারীকে একটি সংস্কৃত পোশাক উপহার দিলেন। এতদিন ধরে নারী শিক্ষাকে পুরুষ ও সমাজ দেখত পুরুষের তৃপ্তি ও বিনোদনের উপকরণ হিসেবে। নারীর আলোকিত হয়ে ওঠা বা আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্যে এটা কেউ ভাবতে পারত না। কিন্তু বাইরে বেরুবার পোশাক পরে নারীর আত্মবিশ্বাস ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ জাগ্রত হলো, তখন থেকেই নারী সমাজে ধীরে ধীরে রোজগার করার জন্যে কর্মক্ষেত্রে যেতে শুরু করলেন।
মাদার তেরেসার মতো আত্মত্যাগী, দরদি, মানবতাবাদীদের দিয়ে কত নিগৃহীত ও দরিদ্র মেয়েরা যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে! ভগ্নি নিবেদিতা কেবল বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতায় বিমুগ্ধ ছিলেন না, বিবেকানন্দ মারা যাওয়ার পর নিজে ভারতের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন।
উপার্জনের জন্যে বাইরে বেরিয়ে পড়া নারীদের দিনের আলো থাকা অবস্থায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর বাড়ি ফেরার আবশ্যিকতা মেনে নিয়ে, সেই ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েই কাজ করতে হতো। তবে লক্ষণীয় যে, উনিশ শতকের সত্তরের দশকে বারাঙ্গনা, বাইজিরা যেমন অভিনয়, নৃত্য ও সংগীতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন অন্তঃপুরের নারীদের জন্যে, বিংশ শতাব্দীর শেষে বস্ত্রশিল্পের মেয়েরা দলে দলে হাজারে হাজারে কাজে যোগদান করে নারীদের দিনে রাত্রে সবসময় কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। তাই নব্বইয়ের দশকে আমরা শামিল হই রাত্রিতে নারীপক্ষের মশালযাত্রায়, যার প্রতীকী ব্যঞ্জনা হলো, রাতের ভয়ে নারীর চলাচল শুধু দিনের আলোয় সীমাবদ্ধ থাকবে না। বস্ত্রশিল্পের মেয়েরা তাদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীর চলার পরিধি এক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম আত্মজীবনী রাসসুন্দরীর ‘আমার জীবন’-এর পথ ধরে একের পর এক নারী লেখকদের অকপটে আত্মজীবনী লেখা, সারা তৈফুরের মতো সাহসী নারীর ধর্মচর্চায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ঈদের নামাজে পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে খোলা ময়দানে সমবেত নারীদের (মাঝখানে একটি পর্দা খাটিয়ে) একত্রে নামাজ পড়া, দেশ শাসন থেকে আইনসভায় নারীর সদর্প উপস্থিতি এবং সবরকম পেশায় নারীদের স্বতঃফূর্ত যোগদান নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেছে।
স্মরণীয় নারী যাঁদের অবদানে সমাজ এতটা এগিয়ে এসেছে, নারী প্রগতির উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তাঁদের কয়েকজনের নাম দেওয়া হলো নিচে :
১. অবলা বসু (১৮৬৫-১৯৫১)
২. অরুণা আসফ আলী (১৯০৯-১৯৯৬)
৩. আরতি সাহা (গুহ) (১৯৩৩-১৯৯৪)
৪. আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৭২)
৫. ইলা মিত্র (১৯২৫-২০০২)
৬. ঊর্মিলা দাশ (১৮৮৩-১৯৫৬)
৭. করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২২)
৮. কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়) (১৮৬১-১৯২৩)
৯. কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)
১০. কৃষ্ণভামিনী দাস (১৮৬৪-১৯১৯)
১১. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১)
১২. চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪)
১৩. জাহানারা ইমাম (১৯২০-১৯৯৪)
১৪. জোবেদা খাতুন চৌধুরানী (১৯০১-১৯৮৬)
১৫. জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৪৫)
১৬. তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭)
১৭. নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী (১৮৫৮-১৯০৩)
১৮. নীলিমা ইব্রাহীম (১৯২১-২০০২)
১৯. নূরজাহান মুরশিদ (১৯২৪-২০০৩)
২০. ফজিলাতুন্নেসা (১৯০৫-১৯৭৬)
২১. বদরুন্নেসা আহমেদ (১৯২৭-১৯৭৪)
২২. বেগম ফজিলাতুন্নেসা (১৯৩০-১৯৭৫)
২৩. বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)
২৪. ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৫-১৯১১)
২৫. মনিকুন্তলা সেন (১৯১০-১৯৮৭)
২৬. মনোরমা বসু (১৮৯৭-১৯৮৬)
২৭. মাদার তেরেসা (১৯১০-১৯৮৭)
২৮. মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩)
২৯. মেহেরুন্নেসা (১৯৪০-১৯৭১)
৩০. মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-১৯৯০)
৩১. রওশন জামিল (১৯৩১-২০০২)
৩২. রানী চন্দ (১৯১২-১৯৯৭)
৩৩. রানী ভবানী (১৭০৪-১৭৯৩)
৩৪. রানী রাসমনি (১৭৯৩-১৮৬১)
৩৫. রাশমণি হাজং (১৮৯৮-১৯৪৬)
৩৬. লীলা নাগ (রায়—১৯০০-১৯৭০)
৩৭. লীলা রায় (১৯১০-১৯৯২)
৩৮. সরলা দাশ (রায়) (১৮৬১-১৯৪৬)
৩৯. সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫)
৪০. সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯)
৪১. সারা তৈফুর (১৮৮০-১৯৭১)
৪২. সুচেতা কৃপালনী (১৯০৮-১৯৭৪)
৪৩. সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)
৪৪. সেলিনা পারভীন (১৯৩১-১৯৭১)
৪৫. সেলিনা বানু (১৯২৬-১৯৮৩)
৪৬. স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)
৪৭. হেনা দাস (১৯২৪-২০০৯)
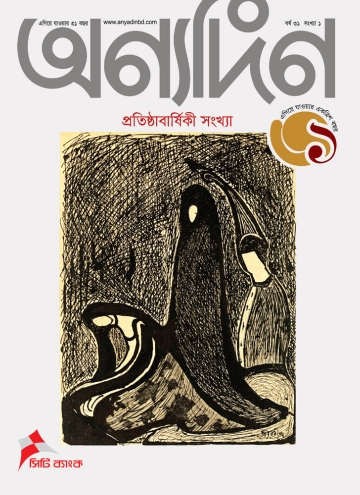














Leave a Reply
Your identity will not be published.