[বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীও রয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য ভুবন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধÑসব ধরনের রচনাতেই নারীরা সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। এমনকি সংস্কৃতিতেও। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সেইসব স্মরণীয় নারী এবং তাঁদের কীর্তির কথাই এই ধারাবাহিক রচনায় তুলে ধরা হয়েছে।]
৮১) সন্তোষকুমারী দেবী (১৮৯৭-১৯৮৯) : চটকল শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লেবার পার্টির সদস্য টমাস জনস্টন ও জন সাইয়ের লিখিত Exploitation in India (১৯২৫) গ্রন্থ থেকে তখনকার দিনে চটকল শ্রমিকদের অবস্থা ও শ্রমিক আন্দোলনে সন্তোষকুমারী দেবীর ভূমিকা সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যায়। সে সময় কাগজে কলমে দু-একটি সংগঠন থাকলেও সন্তোষকুমারী দেবীর নিজের অর্থ ও শ্রমে গড়া Bengal Jute Workers Association ছাড়া কোনো সত্যিকার শ্রমিক সংগঠন ছিল না। এই সংগঠনের সদস্য ছিল ৩০০০। শ্রমিকদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্যে তিনি বহু ধর্মঘট পরিচালনা করেন। এর মধ্যে গৌরিপুর চটকল ধর্মঘট বিখ্যাত। ১৯২৪ সালে শ্রমিকদের চেতনাবৃদ্ধির প্রয়াসে একটি পত্রিকা বের করেন। নাম ‘শ্রমিক’Ñদাম ১ পয়সা। বাংলা, হিন্দি ও উর্দু তিন ভাষায় কাগজটা বেরোত। শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করা ছাড়াও তাদের অবস্থা এবং নিজস্ব মতামত নিয়ে সন্তোষকুমারী অনবরত বিভিন্ন কাগজে লিখতেন। শ্রমিকনেত্রী প্রভাবতী দাশগুপ্ত ও চটকল শ্রমিক দুখমৎ দিদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। কায়িক পরিশ্রম ও নৈতিক সম্মানই শুধু নয়, সন্তোষকুমারী দেবী নিজের অর্থ ব্যয় করে হাজার হাজার শ্রমিকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা মিটিয়েছেন।
৮২) সরলা দাশ রায় (১৮৬১-১৯৪৬) : বিক্রমপুরের বিপ্লবী ব্রাহ্ম সংস্কারবাদী দুর্গামোহন দাশের প্রথমা কন্যা, জগদীশ চন্দ্র বসুর স্ত্রী অবলা বসু (দাশ)-এর জ্যেষ্ঠ সহোদরা। ১৮৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নানা রকম পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের পরে যে দুজন নারীকে সর্বপ্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে মনোনীত করেন তাঁদের একজন কাদম্বিনী বসু, আরেকজন ছিলেন এই সরলা দাশ। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বাঙালি অধ্যক্ষ প্রসন্ন চন্দ্র রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সরলার আর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হয় না। নারী প্রগতির একটি বিশাল ইতিহাস গড়তে গড়তে শেষ মুহূর্তে তাঁকে পিছিয়ে আসতে হলো, কিন্তু তিনি আজীবন নারী শিক্ষা প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। মেয়েদের শিক্ষার্থে গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠিত করেন। সরলা রায় নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের সভানেত্রী ছিলেন। তিনি স্বামীর কর্মক্ষেত্র ঢাকায় একটি মহিলা সমিতি ও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলকাতায় এসে স্বর্ণকুমারী দেবীর সখী সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত সখী সমিতির অর্থায়নের জন্যে সরলার বিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে প্রথম ‘মায়ার খেলা’ গীতিনাট্যটি লিখে দেন। সরলা নিজের নির্দেশনায় ‘মায়ার খেলা’ মঞ্চস্থ করেন, বেথুন কলেজে সখী সমিতির জন্যে তহবিল সংগ্রহ করার জন্যে। স্বাধীন ভারতের প্রথম বিমানবাহিনী প্রধান যাকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর পিতা বলে আখ্যায়িত করা হয়, সেই অসাধারণ বাঙালি সুব্রত মুখার্জি সরলা ও প্রসন্নের দৌহিত্র।
৮৩) সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫) : রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষালের কন্যা। বেথুন কলেজ থেকে সরলা ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ পাস করেন ১৭ বছর বয়সে। মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সরলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘পদ্মাবতী স্বর্ণপদক’ লাভ করেন। তিনিই এই মেডেলের প্রথম প্রাপক। তিনি ফরাসি এবং ফারসি ভাষা নিয়েও পড়াশোনা করেছিলেন এবং পরে সংস্কৃত নিয়ে এম.এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। স্কুলে তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন কবি কামিনী রায় (সেন) এবং লেডি অবলা বসু। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভের বাসনায় তিনি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে মনস্থ করেন। স্কুলে বিজ্ঞান কিছুটা পড়েছিলেন কিন্তু সেকালে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ ছিল না। অবশেষে তিনি মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসনে তাঁর দুই দাদার সঙ্গে (জ্যোৎস্নানাথ ও সুধীন্দ্রনাথ) বিজ্ঞানের ক্লাসে বসে থাকতেন। তবে বিজ্ঞানে শেষ পর্যন্ত উৎসাহ পান নি সরলা।
সঙ্গীতে অসামান্য প্রতিভা ছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের স্বরলিপিও তিনি তৈরি করেছেন। পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করে ‘সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে' গানটিকে পিয়ানোতে বাজানোর জন্যে উপযুক্ত করে তোলেন তিনি। হাফেজের একটি কবিতায় সুরারোপ করে মহর্ষিকে শোনানোয় তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে সরলা দেবীকে এক হাজার টাকার হীরে বসান নেকলেস উপহার দেন। নানা জায়গা থেকে সরলা গানের সুর সংগ্রহ করতেন। তাঁর সুরে কথা বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’, ‘চিরবন্ধু চিরনির্ভর’, ‘এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ’ ইত্যাদি গানগুলো রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ‘বন্দেমাতরম’ গানের সুর তিনিই প্রথমে দিয়েছিলেন। এই গানটি তাঁর কণ্ঠে গীত হওয়ার জন্য কংগ্রেস অধিবেশনে যখন তাঁর ডাক পড়ে, শোনা যায় তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ‘সপ্ত কোটির’ বদলে ‘ত্রিংশ কোটি’ বসিয়ে গানটিকে সর্ব ভারতীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ সরলা দেবীকে আদর করে ‘সল্লি’ বলে ডাকতেন। চিঠিপত্রেও সম্বোধন করতেন ‘সল্লি’ বলে। সরলা রবীন্দ্রনাথকে ডাকতেন ‘রইমা’ (রবিমামা) বলে। ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদনার ভার যৌথভাবে তার দিদি হিরন্ময়ী দেবী ও তিনি পালন করতেন। সরলা দেবী ভারতী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁর লেখার বিষয় ছিল দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ। তাঁর বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান ‘নমো হিন্দুস্থান’ ১৯০১ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে গাওয়া হয়। সরলা দেবী কিছুকাল মহীশূরে মহারাণী স্কুলে শিক্ষকতা করেন, এমন কি মহারাণীর সেক্রেটারির কাজও করেছেন। ১৯০৪ সালে তিনি ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ নামে একটি স্বদেশি দোকান খোলেন। মূলত হাতে বোনা পোশাকের ব্যবহার জনপ্রিয় করতেই তাঁর এই প্রয়াস। স্বদেশি জিনিস যোগাড় করে বম্বে কংগ্রেসে পাঠানোর উদ্যমকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। সেকালের প্রচলিত রীতি ভেঙে সরলা দেবী প্রায় তেত্রিশ বছর বয়স অবধি অবিবাহিত ছিলেন। সরলা দেবীর জীবনের সবচেয়ে মহৎ কীর্তি হলো ‘ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল’ ও ‘ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদন’ স্থাপন করে তিন হাজার মহিলাকে শিক্ষাদান করা। রবীন্দ্ররচিত অনেক সংগীতের বাণীতে কেবল সুরই দেন নি, স্বরলিপিও করেছেন। ১৯০৫ সালে ৩৩ বছর বয়সে অভিভাবকদের প্রচেষ্টায় তাঁর বিয়ে হয় পাঞ্জাবের ছেলে রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে। স্বামী রামভজ অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন এবং ‘হিন্দুস্থান’ নামে একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করতেন। নানা জ্বালাময়ী রচনা প্রকাশ করে তিনি শাসকদের রোষে পড়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। মতান্তরে তিনি গ্রেফতার এড়িয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড চলে যান। সরলা দেবী এই সময়ে পত্রিকাটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এর ইংরাজি অনুবাদও প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ আগস্ট মুসৌরীতে স্বামী রামভজের মৃত্যুতে সরলা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং পাঞ্জাব থেকে ফিরে এসে ‘ভারতী’ সম্পাদনা ও অন্যান্য কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করেন। সাময়িকপত্রে লেখার জন্যে লেখককে দক্ষিণা দেওয়ার প্রথাও তিনিই প্রথম শুরু করেন। ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতায় 'ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদন’ নামে মেয়েদের একটি স্কুল খোলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র দীপক দত্তর বিয়ে হয় মহাত্মা গান্ধির এক নাতনি রাধার সঙ্গে। প্রথমে বিপ্লবী চিন্তাদ্বারা চালিত হলেও পরে তিনি মহাত্মা গান্ধির অহিংসানীতি ও অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা আকৃষ্ট হন। ‘ভারতী’ সম্পাদনার সূত্রে তিনি স্বামী বিবেকান্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজী সরলার গুণের অত্যন্ত প্রশংসা করতেন এবং বলতেন তিনি ‘নারীকুলের রত্ন’। নিবেদিতাকে বিদেশে গিয়ে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা প্রচার করতে বলেন কিন্তু যা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। খাঁটি দেশপ্রমিক অত্যন্ত পরিশ্রমী এই রাজনৈতিক নেত্রী নারী কল্যাণ, সাহিত্য রচনা, সংগীতে তাঁর পাণ্ডিত্যের চিহ্ন রেখেছেন। শেষ জীবনে রচিত আত্মজীবনী ‘জীবনের ঝরাপাতা’ একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ আগস্ট ৭২ বছর বয়সে অসাধারণ তেজস্বী দেশপ্রেমিক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মহিলা লোকান্তরিত হন।
৮৪) সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) : বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক পরিবারের মেয়ে অসাধারণ প্রতিভাময়ী সরোজনী নাইডু একাধারে কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক কর্মী ও নারী স্বাধীনতার সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেত্রী। ১৯১১ সালে অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে যুগ্ম নেতৃত্বে তিনি নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে মহিলা দলের তরফ থেকে স্মারকলিপি পেশ করেন। ১৯২৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বভারতীয় সংগ্রেস সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে আমেরিকায় ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের পক্ষে প্রচার করেন। গান্ধীজির সঙ্গে লবণ আইন অমান্য করার দায়ে ১৯৩০ সালে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকে অন্যতম নেত্রী ছিলেন। ভারতের তদানীন্তন রাজনীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন ‘ভারতের নাইটিংগেল’ সরোজিনী নাইডু। ভারতের স্বাধীনতার পর উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু সে দায়িত্ব পালন করেন।
৮৫) সারা তৈফুর (১৮৮০-১৯৭১) : বেগম রোকেয়ার পরে যিনি সমাজের অবরুদ্ধ পরিবেশে নির্ভীকচেতা নারী হিসেবে সকল প্রতিকূলতাকে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি মিসেস সারা তৈফুর। ১৮৮০ সালে (মতান্তরে ১৯৮৮) বরিশাল শহরে বেগম তৈফুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মজহার হোসেন নূর আহম্মদের বাড়ি ছিল ঢাকার নওয়াবগঞ্জ থানার নয়াবাড়ীতে। তাঁর মা ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বড় বোন। সারা শৈশবে মাতৃহীন হন এবং মাতামহীর তত্ত্বাবধানে লালিত হন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী। সমাজ কল্যাণের কাজে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের জন্য তিনি পেয়েছিলেন কায়সারে হিন্দু মেডেল। বেগম সারা তৈফুরের সাহিত্য জীবন ছিল উল্লেখযোগ্য। বিবাহের মাত্র দু’বছর পর ১৯১৬ সালে হযরতের জীবন ও আদর্শ ভিত্তি করে তিনি রচনা করেন ‘স্বর্গের জ্যোতি' নামক গ্রন্থ। তা ছাড়া বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, আল ইসলাম প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো।
বাঙালি মুসলিম নারী উন্নয়নের ইতিহাসে সারা তৈফুরের বহুমুখী পরিচয়। তিনি একাধারে সমাজসেবী, সাহিত্যসেবী, উন্নয়নকর্মী ও নারী জাগরণের অগ্রদূত। শৈশব থেকে তিনি ঝুঁকে পড়েন শিক্ষা ও সাহিত্যের দিকে। সারা তৈফুরের শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগকে শাণিত করে মহিলাবান্ধব, বামাবোধিনী ইত্যাদি পত্রপত্রিকা। সারা তৈফুরের আসল নাম ছিল হুরুননেসা সারা খাতুন। ১৯১৪ সালে সারা খাতুনের বিয়ে হয় ঢাকার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের সঙ্গে। বিয়ের পর সারা খাতুন স্বামীর পদবি গ্রহণ করে পরিচিত হন সারা তৈফুর হিসেবে। শ্বশুরবাড়ির রক্ষণশীল পরিবেশে থেকেও উচ্চ শিক্ষিত স্বামীর আন্তরিক সহযোগিতায় তিনি ইংরেজি শিখলেন, নিজেকে সমৃদ্ধ করলেন যুগোপযোগী ভাবধারায়। তৈফুর সাহেবই স্ত্রীকে পর্দা প্রথা ভাঙতে সহায়তা করেন। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে স্ত্রীকে বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁদের সঙ্গে বসে গল্প করার সাহস জোগান। ১৯২২ সালে সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর যোগাযোগ ঘটে কলকাতার আঞ্জুমানে খাওয়াতীনের সঙ্গে। এ সময় তিনি আঞ্জুমানে খাওয়াতীনের সদস্যপদ লাভ করেন। এরপর তাঁকে তাঁর স্বামী কলকাতা নিয়ে যান এবং সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল দেখার সুযোগ করে দেন। আঞ্জুমানে খাওয়াতীনের পাশাপাশি তাঁর যোগাযোগ ঘটে দীপালী সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী লীলা নাগের সঙ্গে। ঢাকায় অবস্থিত এ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের কারণে সারা তৈফুর প্রকাশ্য সমাজসেবার সুযোগ লাভ করেন। প্রকাশ্যে সমাজসেবামূলক কাজে তিনিই প্রথম মুসলিম মহিলা, যিনি সামাজিক ভ্রƒকুটি অবজ্ঞা করে উত্তরসূরিদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দীপালী সংঘ সে সময় ঢাকায় নিয়মিত শিল্পমেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয়। মেলা উপলক্ষে কলকাতা থেকে ঢাকায় যাওয়ার সুযোগ ঘটে তাঁর। এ নির্ভীকচেতা নারী মেয়েদের ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে খোলা ময়দানে পুরুষদের পাশে একটি পর্দা টানিয়ে ঈদের নামাজ পড়েন ১৯৩৯ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানুষের দুর্দশা লাঘব করার জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন সমাজসেবায়। পরবর্তী সময়ে তাঁকে শিশুকল্যাণ ও মাতৃসদন ট্রাস্ট, সরকারি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় বোর্ড ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া তিনি ছিলেন মিটফোর্ড হাসপাতালের স্বাস্থ্যপরিদর্শক। রেড ক্রস ও উইমেন্স ভলান্টারি অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্মের একজন অসাধারণ কর্মী ছিলেন তিনি। ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের পরিদর্শক হিসেবে তাঁর অসামান্য অবদান ছিল। ১৯৩৯ সালে তিনি জেল ভিজিটরের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি নারীবন্দিদের দাবিদাওয়া ও তাদের প্রধান সমস্যা তৎকালীন সরকারের গোচরে আনেন। ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর এ সংগ্রামী, নির্ভীক জননেত্রী ও শিক্ষানুরাগী মহীয়সীর জীবনাবসান ঘটে।
৮৬) সাহানা দেবী (১৮৯৭-১৯৯০) : সাহানা দেবী জন্মগ্রহণ করেন ফরিদপুরে। পিতা ড. প্যারিমোহন গুপ্ত, মাতা তরলা দাশ। মামা চিত্তরঞ্জন দাশ, মাসি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গায়িকা অমলা দাশ (যাঁর কাছে জীবনে প্রথম গান শেখা শুরু করেছিলেন সাহানা), মেসোমশাই জগদীশচন্দ্র বসু। অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর পিসতুতো ভাই। বড় পিসিমা সরলা দেবী ছিলেন জগদ্বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের মাতামহী।
জীবনে বহু গুণীজনের সান্নিধ্যে এসেছেন সাহানা দেবী। সুকণ্ঠী সাহানা তাঁর মাসি অমলা দাশের কাছে গান শেখা শুরু করলেও তাঁর বয়স যখন বারো, তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাকে। সাহানা দেবীকে গান শেখাবার জন্যে। এক নাগাড়ে তিন বছর তাঁর কাছে গান শিখেছেন সাহানা। তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে গান শেখান সাহানাকে। গানের প্রতি সাহানার অবিচল আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হন। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও দাদা অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে অতুলপ্রসাদের গান শেখেন, দিলীপ রায়ের কাছ থেকে শেখেন দ্বিজেন্দ্রগীতি। ১৯২২-২৩ সালের দিকে কলকাতা থেকে প্রথম অতুলপ্রসাদের গানের রেকর্ড বের হয় সাহানা দেবী ও হরেন চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে।
সাহানার বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ একবার কাশীতে যান এবং সাহানার সঙ্গে দেখা করেন। সাহানা তাঁর আত্মজীবনী ‘স্মৃতির খেয়া’-তে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তখন বলেছেন, ‘যাক শুনে খুশি হলুম যে তোমার গান শেখার মন আছে। এক তোমাকেই দেখলুম বিয়ে করেও গান ছাড়ে নি। তোমাদের মেয়েদের হয় বিয়ে, নয় গান। দুটোর মাঝামাঝি কিছু নেই।’ রবীন্দ্রনাথ সাহানা দেবীর মুখে গান শুনতে যে কী পছন্দ কতেন তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর লিখিত একখানি চিঠিতে যা ৪/৮/৩৮-এ সাহানা দেবীকে উদ্দেশ করে লেখা।
‘তুমি যখন আমার গান করো, শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে, যে গানে যতখানি আমি আছি, ততখানি ঝুনু-ও আছে। এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে, সেটার জন্যে রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে। আমি যদি সেকালের সম্রাট হতুম, তাহলে তোমাকে বন্দিনী করে আনতুম লড়াই করে। কেননা তোমার কণ্ঠের জন্যে আমার গানের একান্ত প্রয়োজন আছে।’
সাহানা দেবী শুধু সুগায়িকাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কবিও। তাঁর বহুল পরিচিত কবিতার মধ্যে রবি স্মৃতি, আলোর সঙ্গে ছায়ার সঙ্গে, শৈশব হতে গীতিসুধা পানে উল্লেখযোগ্য। জন্ম থেকে শুরু করে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তাঁর স্মৃতি ঘেঁটে লেখা ‘স্মৃতির খেয়া’ ১৯৭৮ সালেই প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালে ৯৩ বছর বয়সে তিনি মারা যান।
৮৭) সুচিত্রা মিত্র (১৯২৪-২০১১) : সুচিত্রা মিত্রের জন্ম হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের শালবন ঘেরা গুঝাণ্টি নামে একটি রেলস্টেশনের কাছে, ট্রেনের কামরায়। তাঁদের পৈতৃক নিবাস উত্তর কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে। তাঁর পিতা ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬, যিনি রামায়ণ-অনুবাদক কবিকৃত্তিবাস ওঝা’র উত্তর পুরুষ)। সুচিত্রার মায়ের নাম সুবর্ণলতা দেবী। কলকাতার বেথুন কলেজিয়েটে স্কুলে তিনি লেখাপডা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি পড়াশোনা করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
খুব অল্প বয়সে তিনি রবীন্দ্রসংগীত শিখতে শুরু করেন। পরে তিনি গান শিখেছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শৈলজারঞ্জন মজুমদার এবং শান্তিদেব ঘোষের কাছে। ছেলেবেলায় তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ সাহচর্য লাভ করেছিলেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ক্লাস টেন-এ পড়ার সময় শান্তিনিকেতনের সংগীত ভবন থেকে বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে তিনি শান্তিনিকেতন চলে যান। তার মাত্র ২০ দিন আগে রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হয়েছিলেন। ১৯৪৩-এ শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে প্রাইভেটে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন। একই বছর রবীন্দ্রসংগীতে ডিপ্লোমা লাভ করেন। এরপর স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ বিএ পাস করেন। ১৯৪৭ সালের ১ মে তিনি ধ্রুব মিত্রের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাদের একমাত্র পুত্র সন্তান কুণাল মিত্রের জন্ম হয়। কুণাল মিত্র বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের বাসিন্দা। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বিবাহবিচ্ছেদ হয় সুচিত্রা মিত্রের।
কলেজজীবনে তিনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অভিযোগে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাদের মুক্তির জন্য রাস্তায় মিছিল করেছেন। সক্রিয় রাজনীতির অংশ হিসেবে মিছিল, প্রতিবাদ করতে গিয়ে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে মার পর্যন্ত খেয়েছেন। রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে ছয় বছর আকাশবাণী থেকে তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে গান গাইতে দেওয়া হয় নি।
তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘদিন। প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি পেয়ে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন ২১ বছর একনাগাড়ে (১৯৬৩-১৯৮৪)। রবীন্দ্র ভারতীতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তিনি বাংলায় এমএ পাস করেন।
১৯৪৫-এ প্রথম তাঁর গানের রেকর্ড বেরোয়। তখন তাঁর বয়স ২১ বছর। সেটা রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড; এক পিঠে ‘মরণেরে তুঁ হু মম শ্যাম সমান’, অন্য পিঠে ‘হৃদয়ের একূল ওকূল দু’কূল ভেসে যায়’। দ্বিতীয় রেকর্ডটি তাঁর পিতার লেখা গান : এক পিঠে ‘তোমার আমার ক্ষণেক দেখা’, অন্য পিঠে ‘আমায় দোলা দিয়ে যায়’। এরপর আমৃত্যু তাঁর সাড়ে চার শ’রও বেশি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বের হয়েছে। কয়েকটি চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে গান গেয়েছেন। তাঁর গায়কি ঢং ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। তাঁর কণ্ঠমাধুর্যের সঙ্গে ছিল এক ধরনের দৃঢ়তা । রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও তিনি গেয়েছেন অতুলপ্রসাদের গান, ব্রহ্মসংগীত, আধুনিক বাংলা গান এবং হিন্দিভজন। শান্তিনিকেতনে তিনি নানা বাদ্যযন্ত্র শিখেছেন : সেতার, এস্রাজ, তবলা। শেষ পর্যন্ত তিনি কণ্ঠসংগীতই বেছে নিলেন।
ছোটবেলা থেকেই অভিনয় ভালোবাসতেন। পরিণত বয়সে ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত ‘দহন’ নামক চলচিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে নির্মিত উমাপ্রসাদ মৈত্রের ‘জয় বাংলা’ এবং মৃণাল সেনের ‘পদাতিক’ ও বিষ্ণু পাল চৌধুরীর টেলিফিল্ম ‘আমার নাম বকুল’-এ অভিনয় করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা, বিসর্জন, তপতী, নটীর পূজা, মায়ার খেলা, চিরকুমার সভা ও নীলদর্পণ নাটকে অভিনয় করেছেন।
১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সংগীত নাটক একাদেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন; এ ছাড়া এইচএমভি গোল্ডেন ডিস্ক অ্যাওয়ার্ড, বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে আলাউদ্দিন পুরস্কার লাভ করেছেন। পেয়েছেন সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কারসহ নানা সম্মান। সাম্মানিক ডি-লিট পেয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর ভেতর রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে তাঁর গবেষণামূলক বইটি উল্লেখযোগ্য। ছোটদের জন্য লিখেছেন কবিতা ও গল্প; লিখেছেন স্মৃতিকথা। তিনি খলিল জিবরানের কবিতার অনুবাদ করেছেন। সুচিত্রা মিত্র আবৃত্তি করতে ভালোবাসতেন। ছবি আঁকতেন। ছবির প্রদর্শনী পর্যন্ত তিনি করেছেন। সুচিত্রা মিত্র ১৯৪৬-এ কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীতের স্কুল ‘রবিতীর্থ’ স্থাপন করেন। রবিতীর্থের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তিনি বহুদেশে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেছেন।
তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে এবং নীরেন্দ্রনাথ। তাঁর আবক্ষ মূর্তি গড়েছেন শিল্পী রামকিংকর ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে। প্রামাণ্য চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন সুব্রত ঘোষ ও রাজা সেন। ওস্তাদ আমজাদ আলী খান সুচিত্রা মিত্রকে রবীন্দ্রনাথের এক উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আমজাদ আলী খানের সরোদের সঙ্গে সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসংগীতের মেলবন্ধন-এর রেকর্ড তুমুল সাড়া জাগিয়েছিল। ১৯৯৫ সালে আজকাল পত্রিকার উদ্যোগে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মকথা ‘মনে রেখো’।
৮৮) সুচিত্রা সেন (১৯৩১-২০১৪) : সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার অন্তর্গত সেন ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে সুচিত্রা সেনের জন্ম। কথিত আছে, তিনি ছিলেন কবি রজনীকান্ত সেনের দূর সম্পর্কের নাতনি। বাংলাদেশ সরকারের সিরাজগঞ্জ জেলার অফিসিয়াল গ্যাজেটে উভয়ের জন্মস্থান বেলকুচি থানার অন্তর্গত সেন ভাঙ্গাবাড়ি বলে লিখিত আছে। লোকমুখে পরিচিত যে সুচিত্রার জন্ম হয়েছিল তাঁর মায়ের বাপের বাড়িতে সেন ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে। কিন্তু শিল্পকলা একাডেমীর গবেষণা দল সেই গ্রামে গিয়ে অনেকের সঙ্গে কথা বলে সুচিত্রা সেনকে রজনীকান্ত সেনের নাতনি হিসেবে শনাক্ত করতে অসমর্থ হন। পাবনা শহরে লেখাপড়া শিখে সুচিত্রা সেন কলকাতায় চলে যান এবং পরবর্তীকালে সকল রেকর্ড ভঙ্গকারী অসাধারণ জনপ্রিয় মনোমোহিনী চিত্রতারকা হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। জন্মকালে সুচিত্রার নাম ছিল রমা দাশগুপ্ত। দেশভাগের পর তাঁরা সপরিবারে কলকাতা চলে যান। অসামান্য সুন্দরী রমার মাত্র ষোলো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় শিল্পপতি প্রিয়নাথ সেনের ছেলে দিবানাথ সেনের সঙ্গে। স্বামীর উৎসাহেই সিনেমায় অভিনয় করতে আসা। সুচিত্রার আগে ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা অভিনয় করতে আসতেন না। সেই প্রথা ভেঙেছিলেন সুচিত্রা। প্রথমে চলচ্চিত্রে নামতে গিয়ে সেখানকার পরীক্ষায় ফেল করেন সুচিত্রা। তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। পরে স্ক্রিনটেস্টে সফল হয়ে ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ পান। ১৯৫২ সালে প্রথম ছবি ‘শেষ কোথায়’-এর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় তার চলচ্চিত্রজীবন। কিন্তু সেই ছবি মুক্তি পায় নি। সুচিত্রার মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি ‘সাত নম্বর কয়েদি’ (১৯৫৩)। এই ছবিতেই রমা দাশগুপ্ত পরিবর্তিত হয়েছিলেন সুচিত্রা সেনে। ছবির পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তের সহকারী নীতিশ রায়ই রমার নতুন নামকরণ করেছিলেন। তবে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম সফল ছবি উত্তমকুমারের বিপরীতে ‘সাড়ে চুয়াত্তর’। এর পরে উত্তমকুমারের সঙ্গে জুটি বেঁধে অনেক ছবি করেন তিনি। এ এক অবিশ্বাস্য, অসাধারণ জুটি। ছবিতে তাদের রসায়ন এত মধুর ও সাবলীল ছিল যে দর্শকদের মাতাল করে দেয় সুচিত্রা-উত্তম জোড়া। এই জুটির প্রায় সব ছবিই বক্স অফিস হিট হতে শুরু করে। অগ্নিপরীক্ষা, হারানো সুর, শিল্পী, শাপমোচন, চাওয়া পাওয়া, পথে হলো দেরী, সাগরিকা, সপ্তপদী, বিপাশা ইত্যাদি। এ ছাড়া অন্যদের সঙ্গে করা সুচিত্রার উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে সাত পাকে বাঁধা, দীপ জ্বেলে যাই, মরণের পরে, উত্তরফাল্গুনী ইত্যাদি। অভিনয়ের জন্যে সুচিত্রা প্রচুর সম্মান ও পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে ফিল্মফেয়ারে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পুরস্কার মনোনীত হন। ১৯৭২ চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৭৬ সালে আবারও ফিল্ম ফেয়ারে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। ২০১২ সালে বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার লাভ করেন। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে সুচিত্রা সেন ১৯৭৮ সাল থেকে পরিপূর্ণভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান। কন্যা মুনমুন ও দুই নাতনি রাইমা ও রিয়া (তিনজনই অভিনেত্রী) ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেন না। জনসম্মুখে না আসার সিদ্ধান্তের কারণে বহু চিত্রপরিচালকের সাধ্যসাধনা থাকা সত্ত্বেও আর কোনো ছবি করানো যায় নি। এমন কী বিখ্যাত পুরস্কার দাদা সাহেব ফালকে গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান তিনি, যেহেতু দিল্লী গিয়ে তাকে পুরস্কারটি গ্রহণ করতে হতো। ২০১৪ সালের জানুয়ারির ১৭ তারিখে তিনি মারা যান। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী নিভৃতিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।
৮৯) সুচেতা কৃপালনী (১৯০৮-১৯৭৪) : পাঞ্জাব প্রবাসী বাঙালি ডাক্তার এস. এন মজুমদারের কন্যা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এ পাস করেন সুচেতা। পরে কাশ্মীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৬ সালে আচার্য্য কৃপালিনীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকেই সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ক্রমে তিনি একজন সফল নেত্রী হিসেবে জাতীয় কংগ্রেসে নিজস্ব জায়গা করে নেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কঠিন নিয়মতান্ত্রিক সুচেতা কৃপালনীই ভারতের কোনো রাজ্যের প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সারাজীবন সাংবিধানিক রাজনীতি করে গেছেন।
৯০) সুনীতি চৌধুরী (১৯১৭-১৯৮৮) : বিপ্লবী সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার ইব্রাহিমপুরে ১৯১৭ সালের ২২ মে জন্মগ্রহণ করেন। সুনীতির বাবা উমাচরণ চৌধুরী কুমিল্লা কালেক্টরিয়েটের কর্মচারী ছিলেন। মায়ের নাম সুর সুন্দরী দেবী। বাবা-মায়ের উৎসাহেই সুনীতি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। শান্তি ঘোষের বন্ধু ও সহচরী, একই ক্লাসে অধ্যয়নরত সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে হত্যা করেন। শান্তি ঘোষের সঙ্গে একই মিশনে ধরা পড়ে অপ্রাপ্তবয়স্কা বলে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ পান। গান্ধীর ১৮৩৮ সালের দেশজুড়ে বন্দি রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তির আন্দোলনের সুফল হিসেবে শান্তি ঘোষ কেবল নন, সুনীতি চৌধুরীও ছাড়া পান। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পরবর্তীকালে আবার নতুন করে পড়াশোনা শুরু করেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করে চিকিৎসা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শ্রমিকনেতা প্রদ্যুৎ কুমার ঘোষকে ১৯৪৭ সালে বিয়ে করেন। এই মহান বিপ্লবী ১৯৯৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।






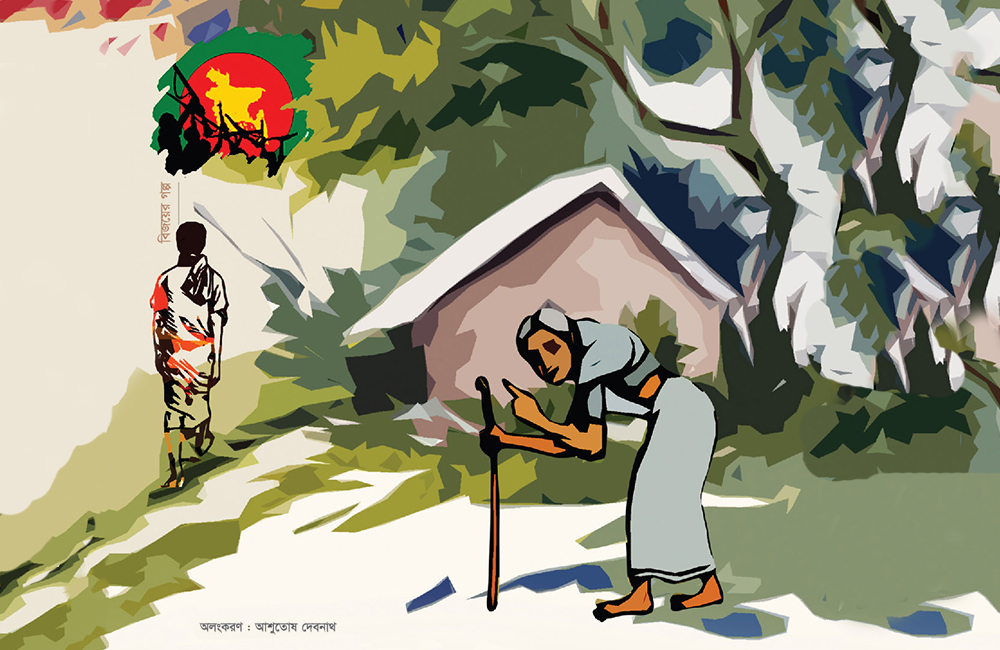

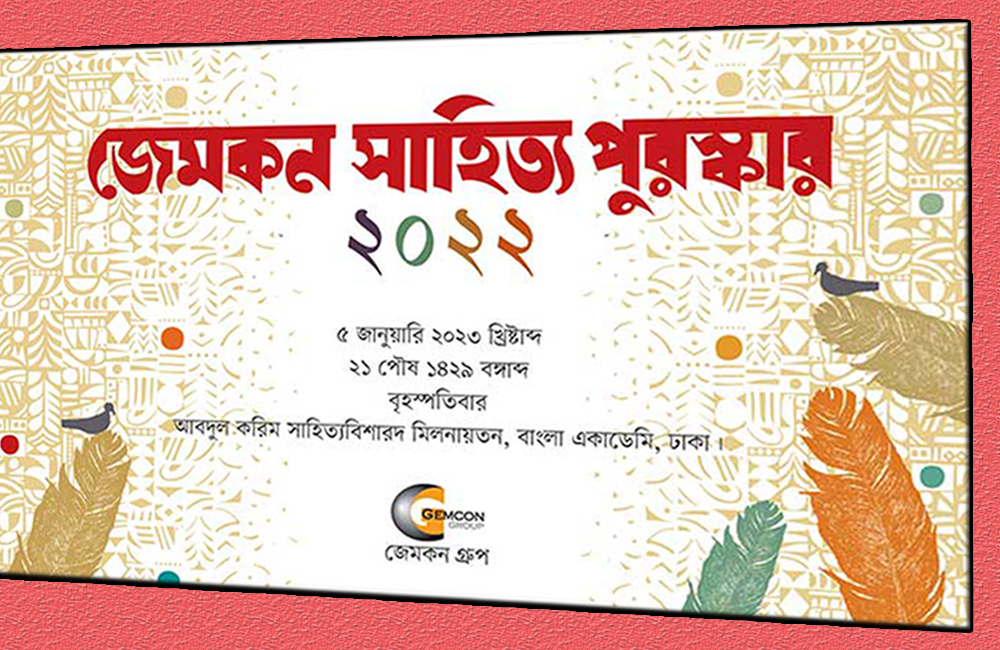
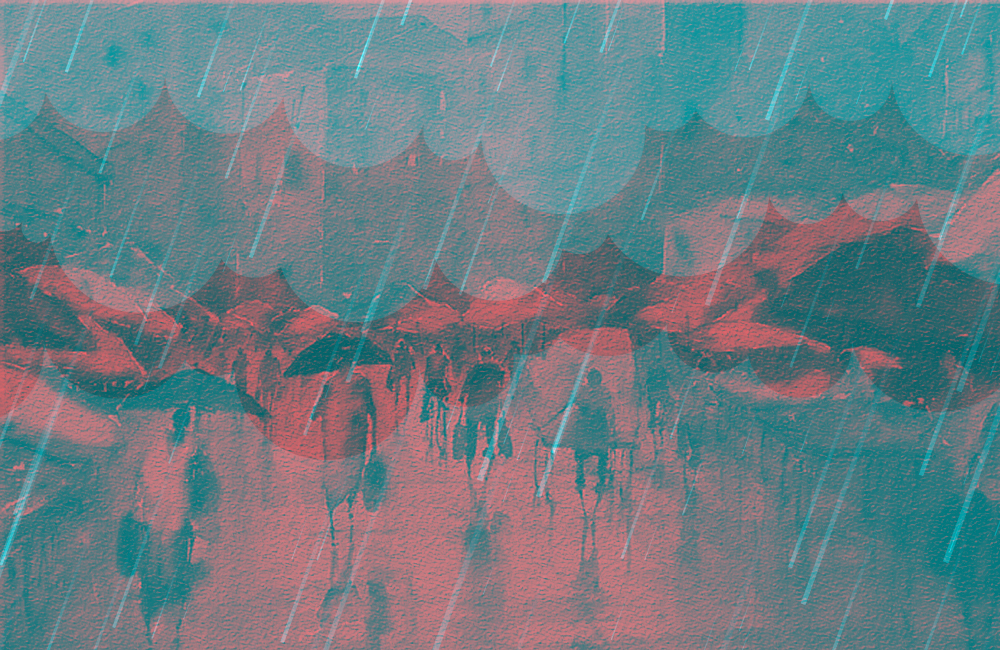
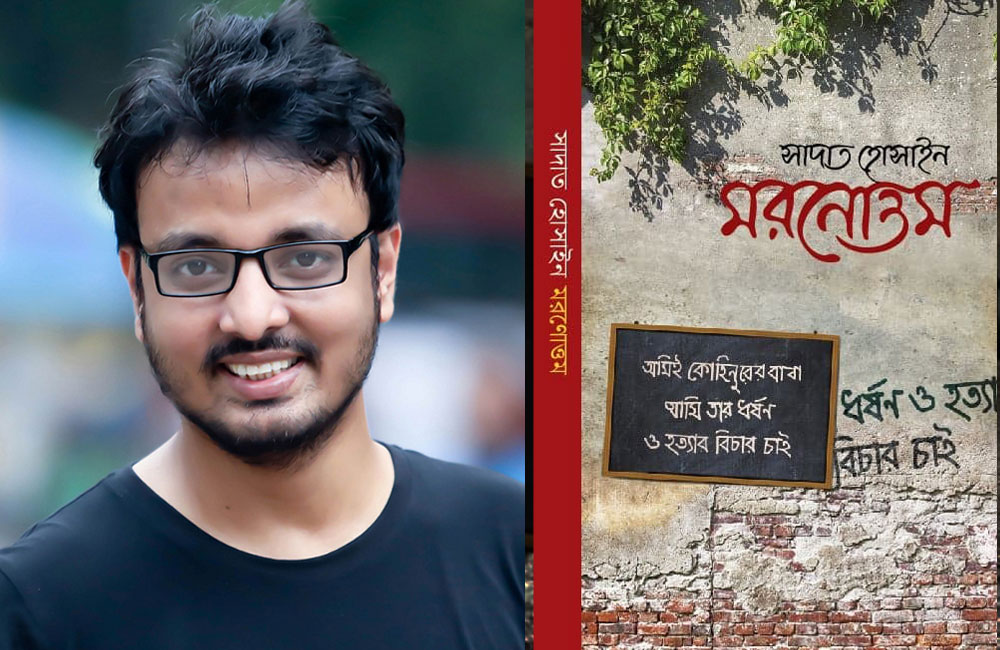




Leave a Reply
Your identity will not be published.