[বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীও রয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য ভুবন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধÑসব ধরনের রচনাতেই নারীরা সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। এমনকি সংস্কৃতিতেও। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সেইসব স্মরণীয় নারী এবং তাঁদের কীর্তির কথাই এই ধারাবাহিক রচনায় তুলে ধরা হয়েছে।]
৬১) মনোরমা বসু (১৮৯৭-১৯৮৬) : বরিশালের বাঁকাইর জমিদার বাড়ির বউ-পরবর্তীকালে নারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী হয়েছিলেন। সমাজের লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও বিধবা মহিলাদের প্রতি তাঁর দরদ তাঁকে সরোজনন্দিনী মহিলা সমিতির একটি শাখা খুলতে অনুপ্রাণিত করে। সমাজসেবামূলক কাজ ও অর্থকরী উপার্জনে মেয়েদের উৎসাহিত করেন তিনি। শুধু সমিতির সেলাই কাজের মাধ্যমে নারী আন্দোলনের মুক্তি আসা সম্ভব নয়, এটা মনোরমা বসু বুঝতে পেরেছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মধারার মধ্যেই নারীমুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। স্বদেশি আন্দোলনে অনুপ্রাণিত মনোরমা পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।
৬২) মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২) : মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত হোগলা গ্রামে দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮ বছর বয়সে বিধবা হন। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। গান্ধীবুড়ি বলে খ্যাত মাতঙ্গিনী হাজরা গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য, লবণ সত্যাগ্রহ ও চৌকিদারি করে প্রতিরোধে যোগ দেন। আগস্ট বিপ্লবের সময় তমলুক থানা অভিযানে নেতৃত্ব গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন প্রৌঢ়া এই বীরাঙ্গনা।
৬৩) মাদার তেরেসা (১৯১০-১৯৮৭) : মাদার তেরেসা, যাঁর আসল নাম ছিল আগনেস গঞ্জা বায়াজু, একজন ভারতীয় ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী। ১৯৫০ সালে স্বদেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে তিনি মিশনারিজ অফ চ্যারিটি নামে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তিনি দরিদ্র, অসুস্থ, অনাথ, একাকী ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের সেবা করেছেন। সেইসঙ্গে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিকাশ ও উন্নয়নেও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রথমে ভারতে ও পরে সমগ্র বিশ্বে তাঁর এই সেবামূলক কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মৃত্যুর পর পোপ দ্বিতীয় জন পল তাঁকে স্বর্গীয় আখ্যা দেন; এবং তিনি কলকাতার স্বর্গীয় তেরেসা (ইষবংংবফ ঞবৎবংধ ড়ভ ঈধষপঁঃঃধ) নামে পরিচিত হন।
সত্তরের দশকের মধ্যেই সমাজসেবী এবং অনাথ ও অসুস্থজনের বন্ধু হিসেবে তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ম্যালকম মাগারিজের বই ও প্রামাণ্য তথ্যচিত্র সামথিং বিউটিফুল ফর গড তাঁর সেবাকার্যের প্রচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭৯ সালে তিনি তাঁর সেবাকার্যের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার ও ১৯৮০ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ভারতরত্ন লাভ করেন। মাদার তেরেসার মৃত্যুর সময় বিশ্বের ১২৩টি রাষ্ট্রে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ৬১০টি কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল। প্রতিটি কেন্দ্রে কয়েকটি বিভাগ থাকে, যেমন ভয়ংকর সংক্রামক রোগের (এইচআইভি/এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষার) চিকিৎসাকেন্দ্র, ভোজনশালা, শিশু ও পরিবার পরামর্শ কেন্দ্র, অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয়।
যদিও অধিকাংশ ব্যক্তি, সংস্থা ও সরকার তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, কিছু কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমালোচনার মুখেও তাঁকে পড়তে হয়। জন্মনিরোধক এবং গর্ভপাতের বিষয়ে তাঁর আপত্তি, দারিদ্র্যের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য বর্ণন, তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী স্বজনবিহীন মৃত্যুপথযাত্রীদের স্বর্গে পাঠাবার জন্যে তাদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার সমালোচনা সহ্য করতে হয় তাঁকে। বিভিন্ন মেডিক্যাল জার্নাল তাঁর প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসার মান নিম্ন বলে অভিযোগ তোলে। কেউ কেউ আবার তাঁর প্রতিষ্ঠানের দানের অর্থের অস্বচ্ছ ব্যয়ের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
আগনেস গঞ্জা বয়াজু (আলবেনীয় ভাষায় গঞ্জা শব্দের অর্থ গোলা পকুঁড়ি) ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট অটোম্যান সাম্রাজ্যের ইউস্কুবে (অধুনা ম্যাসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্কোপিয়ে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর মা-বাবার কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁদের আদি নিবাস ছিল আলবেনিয়ার শকড্য অঞ্চলে। তাঁর পিতা আলবেনিয়ার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আগনেসের মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর মা তাঁকে রোমান ক্যাথলিক আদর্শে লালনপালন করেন। অ্যাগনেস মিশনারিদের জীবন ও কাজকর্মের গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতেন। ১২ বছর বয়সেই তিনি ধর্মীয় জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে একজন মিশনারি হিসেবে যোগ দেন সিস্টার্স অফ লোরেটো নামক সংস্থায়। সেই যে ঘর ছাড়লেন, মা আর দিদিদের সঙ্গে আর তার কোনোদিন দেখা হয় নি।
অ্যাগনেস প্রথমে আয়ারল্যান্ডে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেন। কারণ এই ভাষাই ছিল ভারতে সিস্টার্স অফ লোরেটোর শিক্ষার মাধ্যম। ১৯২৯ সালে ভারতে এসে দার্জিলিংয়ে নবদীক্ষিত হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৩১ সালের ২৪ মে তিনি নান বা সন্ন্যাসিনী হিসেবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি তেরেসা নাম গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালের ১৪ মে পূর্ব কলকাতায় একটি লোরেটো কনভেন্ট স্কুলে পড়ানোর সময় তিনি চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করেন।
স্কুলে পড়াতে তাঁর ভালো লাগলেও কলকাতার দারিদ্র্যে তিনি ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে থাকেন। তার ওপর পঞ্চাশের মন্বন্তরে এবং ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাতে বহু মানুষের মৃত্যু তেরেসার মনে গভীর রেখাপাত করে।
১৯৪৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং যাওয়ার সময় তার মধ্যে এক গভীর উপলব্ধি আসে। তিনি তখন একটা বড় সিদ্ধান্ত নেন। কনভেন্টের বিলাস ও আয়েশ ত্যাগ করে দরিদ্রদের মাঝে বাস করা ও তাদের সাহায্য করার বাসনা নিয়ে ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি দরিদ্রের মাঝে মিশনারি কাজ শুরু করেন। পোশাক হিসেবে পরিধান করেন নীল পাড়ের একটি সাধারণ সাদা সুতির বস্ত্র। এ সময়ই ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বস্তি এলাকায় কাজ শুরু করেন। সেই ছোট্ট কার্যক্রম ধীরে ধীরে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে।
১৯৮৩ সালে পোপ জন পল ২-এর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে রোম সফরের সময় মাদার তেরেসার প্রথম হার্ট অ্যাটাক হয়। এর পর থেকে বহু রকম শারীরিক অসুস্থতায় ভোগেন তিনি। ১৯৯৭ সালের ১৩ মার্চ শারীরিক কারণে মিশনারিস অফ চ্যারিটির প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
৬৪) মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) : যশোহরের রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সাড়ে আঠারো বছর বয়সে বিধবা হন। সাহিত্যে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মানকুমারী নারীর সমস্যা বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লেখেন। চৌদ্দ বছর বয়সে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা তাঁর কবিতা ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ ছাপা হয়েছিল। সাহিত্যকৃতির জন্য বহু পুরস্কার ও বৃত্তি পান। বৈষম্যের শিকার নারী জাতির নানান দুরবস্থার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন। তবে ধর্মে আস্থাশীল মানকুমারীর স্ত্রীজাতির মুক্তির পথ প্রদর্শনে বৈপ্লবিক চিন্তার তেমন নিদর্শন মেলে না। স্বামী-স্ত্রীর গতানুগতিক সম্পর্ককে মেনে নিয়ে, স্ত্রীজাতির সামাজিকভাবে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত ভূমিকাকে গ্রহণ করেই তাদের অবস্থা পরিবর্তনের কথা তিনি বলতেন। মেয়েদের বাল্যবিবাহে ঘোরতর আপত্তি জানালেও বিধবাবিবাহ প্রকাশ্যে সমর্থন করেন নি। হয়তো নিজে বিধবা ছিলেন বলেই। চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের স্বাধীনতার জন্যে তিনি প্রচুর সাহিত্য রচনা করেছেন।
৬৫) মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৭) : ১৯০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাবনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান বাহাদুর মোহাম্মদ সোলায়মান সিদ্দিক। এক সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করায় তাঁর কাব্য প্রতিভা অতি শৈশবেই বিকশিত হতে শুরু করে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তিনি প্রথম কবিতা লেখেন। মাত্র নয় বছর বয়সে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘আল ইসলাম’ পত্রিকায় তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ত্রিশ বছর ধরে তার কবিতা সাপ্তাহিক ‘বেগম’ পত্রিকায় ছাপা হযেছে। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পসারিণী’ ১৯৩৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় মুসলমান মহিলা কবির এটাই প্রথম প্রকাশিত আধুনিক কবিতার বই। কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ ‘মন ও মৃত্তিকা’, ‘অরণ্যের সুর’। ছোটদের জন্য তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ ‘রাঙা ঘুড়ি’, ‘রোদ বৃষ্টি’ ও ‘শ্রাবণ’। অসাধারণ কাব্য প্রতিভার জন্য এই কবিকে ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমি এবং ১৯৭৭ সালে ‘একুশের পদকে’ ভূষিত করা হয়। ১৯৭৭ সালের ২ মে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা মৃত্যুবরণ করেন।
৬৬) মেহেরুন্নেসা (১৯৪০-১৯৭১) : জানামতে কবি মেহেরুন্নেসা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম নারী শহীদ। তিনি ১৯৪০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশবিভাগের ঘনঘটায় তাঁর পরিবার ঢাকায় চলে আসেন। অসময়ে পিতাকে হারিয়ে মা ও দুটি ছোট ছোট ভাইকে নিয়ে অতি কষ্টে দিনযাপন করতেন মেহেরুন্নেসা। সাংসারিক খরচের টাকা যোগাতে তিনি বাংলা একাডেমিতে কপি রাইটিং-এর কাজ করতেন। এ ছাড়া বিভিন্ন কাগজে কবিতা লিখতেন। মিরপুরে বিহারি অধ্যুষিত অঞ্চলে সপরিবারে বাস করতেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা ঘুচাতে তিনি ফিলিপস-এর কারখানায় অ্যাসেম্বলি লাইনেও খণ্ডকালিন কাজ করতেন। সম্প্রতি বেগম-সম্পাদক নূরজাহান বেগম বলেছেন ১৯৫৫ সালে তিনি প্রথম মেহেরুন্নেসার কবিতা ছাপান। কবিতার শিরোনাম ছিল ‘কবিতা’। এরপর নিয়মিত বেগম-এ মেহেরুন্নেসার কবিতা ছাপাতেন তিনি। এ ছাড়া অন্যান্য কাগজেও তাঁর কবিতা ছাপা হতো। ব্যক্তিগত জীবনে খুব উচ্ছল, আমুদে এবং চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন মেহেরুন্নেসা। এই সংগ্রামী কবি একাত্তরের প্রথমদিকে তাঁর লেখা ‘জনতা জেগেছে’ নামক কবিতাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সাহিত্য সভায় পাঠ করেন। এতে ঢাকার অবাঙালিরা তার ওপর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়। সেই কবিতার কিছু পঙ্ক্তি এরকম :
“মুক্তি শপথে দীপ্ত আমরা দুরন্ত দুর্বার
সাতকোটি বীর জনতা জেগেছে এই জয় বাংলার।
বাঁচবার আর বাঁচাবার দাবি দীপ্ত শপথে
আমরা দিয়েছি সব ভীরুতাকে পূর্ণ জলাঞ্জলি
বেয়নেট আর বুলেটের ঝড় ঠেলে
চির বিজয়ের পতাকাকে দেব সপ্ত আকাশে মেলে।”
মুক্তিযুদ্ধের সময় ২৫ মার্চ পাকবাহিনীর অত্যাচার শুরু হলে, ২৭ মার্চ মেহেরুন্নেসার প্রতিবেশী কাদের মোল্লা ও তার সাঙ্গপাঙ্গ মেহেরুন্নেসা ও তার দু’ ভাইকে মায়ের সামনে কুপিয়ে খুন করে তাদের বিচ্ছিন্ন মাথা কাপড় শুকাবার তারে ঝুলিয়ে রেখে চলে যায়। সুফিয়া কামাল মেহেরুন্নেসাকে নিয়ে একখানা কবিতা লেখেন। এই কবিতাটি ১৯৮৭ সালে নওরোজ কিতাবিস্থান থেকে প্রকাশিত ‘মুক্তিযুদ্ধ : নির্বাচিত কবিতা’ সংকলনভুক্ত।
৬৭) মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-১৯৯০) : বিখ্যাত লেখক ও শিক্ষাবিদ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও তাঁর পত্নী হিমানী মাধুরীর কন্যা মৈত্রেয়ী দেবী। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাধের সান্নিধ্য ও স্নেহ পেয়েছেন। মৈত্রেয়ী দেবী শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করেন। মৈত্রেয়ী দেবী লিখিত ও প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে ‘ন হন্যতে’, ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’, ‘স্বর্গের কাছাকাছি’, ‘হিরন্ময় পাখি’, ‘রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে’, ‘চীনে ও জাপানে’ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যকর্মের জন্যে তিনি আকাডেমী পুরস্কার পান। নারীকল্যাণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে তিনি সারা জীবন কাজ করে গেছেন। বিশেষ করে ১৯৬৪ সালের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় সমাজসেবী মৈত্রেয়ী দেবী কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বাড়ানোর জন্য একটি সমিতি গঠন করেন ‘কাউন্সিল ফর দ্য প্রোমোশন অব কমিউনাল হার্মনি’ নামে। সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলা পত্রিকাটির নাম ‘নবজাতক’ আর ইংরেজিটির নাম ‘ব্রাদার্স ফেইস’। আর এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাড়াবার লক্ষ্যে তাঁর যাবতীয় কাজে তাঁর সঙ্গে ছিলেন গৌরী আউয়ুব। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরী আইয়ুব ও অন্নদাশঙ্করের স্ত্রী লীলা রায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। বেসরকারি উদ্বাস্তুদের প্রাথমিক খাওয়া, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্যে তাঁরা সভা, মিছিল করা ছাড়াও দেশ-বিদেশের গণমাধ্যমে লেখা ও সাক্ষাৎকার দেন।
৬৮) রওশন জামিল (১৯৩১-২০০২) : নৃত্যশিল্পী, অভিনেত্রী। ১৯৩১ সালের ৮ মে ঢাকার রোকনপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় লক্ষ্মীবাজার সেন্ট ফ্রান্সিস মিশনারি স্কুলে। স্কুল শেষ করে তিনি ইডেন কলেজে পড়াশোনা করেন।
শৈশবেই রওশন নাচের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নৃত্যতে অনুশীলন নিতে শুরু করেন। সেই সময় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা, বিশেষ করে অভিজাত মুসলমান পরিবারের মেয়েরা প্রকাশ্যে নাচের কথা ভাবতে পারতেন না। নাচের সঙ্গে বহুযুগ ধরে চলে আসা বাইজি ও বারবনিতা সংস্কৃতির যোগাযোগ তাঁদের এবং অভিভাবকদের কুণ্ঠিত করে রাখত নৃত্যকে নিজ গৃহে শিল্পের মর্যাদা দিতে। এর মাঝেই কিছু প্রগতিশীল, সাহসী পরিবার ও দৃঢ়চেতা তরুণী বেরিয়ে এলেন নাচ শিখতে। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য রওশন জামিল হলেও আরও যারা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের গোড়ার দিকে নাচের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করলেন তাঁরা হলেন— লায়লা সামাদ, বেগম রোকেয়া কবীর, কুলসুম হুদা, নাঈমা হুদা, বেগম লিলি খান, জিনাত, মেহের, রোজী মজিদ, লায়লা হাসান প্রমুখ।
রওশন জামিল ম্যাট্রিক পাসের পর ওয়ারী শিল্পকলা ভবনে নাচের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যকলার শিক্ষক গওহর জামিলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে সেই পরিচয় থেকে প্রণয় ও পরিণয় (১৯৫২) হয়। রওশনকে বিয়ে করার জন্যে গওহর জামিল তাঁর নিজধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তখনই তাঁর নতুন নামকরণ হয় গওহর জামিল। দুজনে একসঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের বিমোহিত করেন। তবে গওহর জামিল নৃত্যগুরু হলেও একসময় রওশনই নৃত্যশিল্পী হিসেবে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁরা ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ‘জাগো আর্ট সেন্টার’। এদেশে নৃত্যশিল্পকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে এই শিল্পী দম্পতির অবদান ও অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে স্বামীর মৃত্যু ঘটলে গভীর শোকের মাঝেও রওশন জাগো আর্ট সেন্টারের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
১৯৬৫ সালে টেলিভিশনে ‘রক্ত দিয়ে লেখা’ নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রওশন জামিলের অভিনয়জীবন শুরু হয়। বিটিভির ঢাকায় থাকি এবং সকাল সন্ধ্যা ধারাবাহিক নাটকের অভিনয় তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়।
১৯৬৭ সালে আলীবাবা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে যাত্রা শুরু করেন। চলচ্চিত্রে জীবনঘনিষ্ঠ অভিনয়ের জন্যে তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি বিকল্প ধারার বহু চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন। তিনি বহুসংখ্যক টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হলো: মনের মতো বউ, জীবন থেকে নেয়া, তিতাস একটি নদীর নাম, গোলাপী এখন ট্রেনে, আবার তোরা মানুষ হ, ওরা ১১ জন, মাটির ঘর, সূর্য দীঘল বাড়ি, দেবদাস, রামের সুমতি, জননী, নয়নমণি, জীবন মৃত্যু, মিস ললিতা, নদের চাঁদ, মাটির কোলে, বাঁধনহারা, দহন ইত্যাদি এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আগামী, পোকামাকড়ের ঘরবসতি ও লালসালু।
এদেশে যখন ছেলেরাই মেয়ে সেজে মঞ্চে অভিনয় করতেন, যেহেতু মেয়েরা যেত না প্রকাশ্য মঞ্চে অভিনয়ের জন্যে (১৯৫২ সালের দিকে), তখন রওশন জামিল জগন্নাথ কলেজে মঞ্চায়িত শরৎচন্দ্রের ‘দেবদাস’ নাটকে অভিনয় করেন। তিনি বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনচিত্রেরও মডেল হন।
রওশন জামিল ছিলেন চরিত্রাভিনেত্রী। জটিল ও কুটিল নারীর ভূমিকায় যেমন স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি, তেমনি কোমলমতি নারী চরিত্রের সঙ্গেও সম্পূর্ণ মানিয়ে যেতেন তিনি তাঁর সাবলীল অভিনয় দিয়ে। মোটকথা, সব ধরনের চরিত্রচিত্রণেই সমান পারদর্শী ছিলেন। অভিনেত্রী হিসেবে তিনি নতুন একটি স্টাইল নির্মাণ করেন। তাই সবার মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, টেনাশিনাস পদক, সিকোয়েন্স অ্যাওয়ার্ড, বাচসাস চলচ্চিত্র পুরস্কার, তারকালোক পুরস্কারসহ বহু পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হন। নৃত্যে তিনি ১৯৯৫ সালে একুশে পদক লাভ করেন। ২০০২ সালের ১৪ মে তাঁর মৃত্যু হয়।
৬৯) রানী চন্দ (১৯১২-১৯৯৭) : মেদিনীপুরে জন্ম। পিতৃভূমি বিক্রমপুর। বড় হয়ে শান্তিনিকেতনে আচার্য নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রশিল্পে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী রানী চন্দ চিত্রশিল্পী ও লেখক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কেবলমাত্র সাহিত্য ও শিল্পের পরিবেশে থেকে তাঁর মন ভরে না। কংগ্রেসের কর্মী হিসেবে নানা সমাজসেবা ও গঠনমূলক কাজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। ১৯৩৩ সালে বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অনিল কুমার চন্দের সঙ্গে বিয়ে হয়। ১৯৪২ সালে ‘ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিলেন রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনী, শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ভবানী সেন, শান্তি দাশগুপ্ত, ইলা দত্ত প্রমুখ। আন্দোলন পরিচালনাকালে গ্রেফতার হলে নয় মাসের কারাদণ্ড হয়। রানী চন্দের বহু রচনার ভেতর রয়েছে তাঁর বহুখ্যাত ‘জেনানা ফটক’—লৌহ কপাটের অন্তরালে নারীর জীবনপ্রবাহের মর্মস্পর্শী কাহিনি। ১৯৫৩ সালে বইখানি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে।
৭০) রানী ভবানী (১৭০৪-১৭৯৩) : নাটোরের স্বনামধন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় মহারানী। তিনি বগুড়া জেলার ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা। নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৭৭৬ সালে রামকান্তের মৃত্যু হলে তিনি নিজেই জমিদারি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। রানী ভবানী একজন প্রজাদরদী, নির্ভীক, কৃষ্টিসম্পন্না তুখোড় রাজনীতিবিদ ছিলেন। বর্গীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে তিনি সম্ভবপর সবকিছু করেছিলেন। এর জন্যে মুর্শিদাবাদের আলিবর্দীকেও তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। সিরাজদৌল্লাহ্র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা রানী ভবানীর সমর্থন লাভের জন্যে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মাধ্যমে তাদের আবেদন পেশ করে ছিলও। রানী ভবানী শুধু এই প্রস্তাব অস্বীকারই করেন নি, শোনা যায় কৃষ্ণচন্দ্রের এই কাপুরুষতার স্বরূপ উন্মোচনে তিনি তাঁর কাছে নারীর ব্যবহার্য জিনিস যেমন, শঙ্খ, বলয়, সিঁদুর, বালা ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে খাদ্যের অভাব, ফসলের ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে মারাত্মক বিপর্যয়ের সময় রাজস্বের জন্যে ইংরেজদের চাপাচাপিতে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। পরম দানশীলা প্রজাবৎসল রানী ভবানী তখন তাঁর রাজকোষ উন্মুক্ত করে আর্ত প্রজাদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন। এই সকল কারণে রানী ভবানীর সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বরাবরই একটা বিরোধ বজায় ছিল। তাঁর সুশাসনের ফলে রাজশাহী একটি আদর্শ রাজ্যরূপে সুনাম অর্জন করে। মুঘল শাসনের ফলে কাশীর হিন্দু সংস্কৃতির অবনতি লক্ষ করে রানী ভবানী বিভিন্নভাবে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেন। যেমন—তিনি সেখানে বেশ কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, জলাশয় খনন করেন। এ ছাড়া সাধারণ প্রজাদের স্বার্থে বেশ কয়েকটি সামাজিক সংস্কারের গুরুভার গ্রহণ করেন।







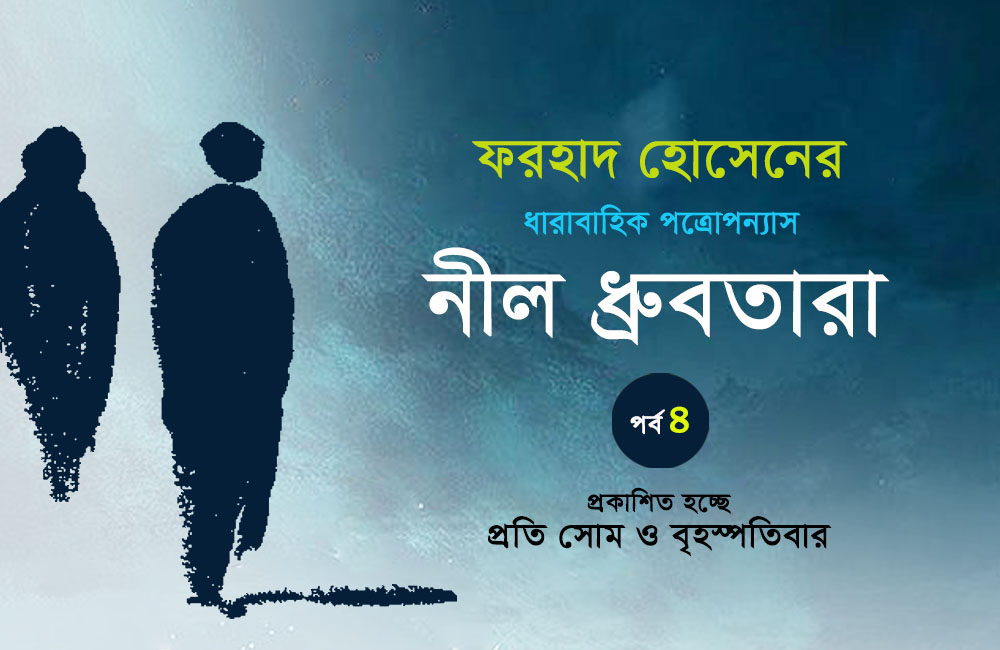
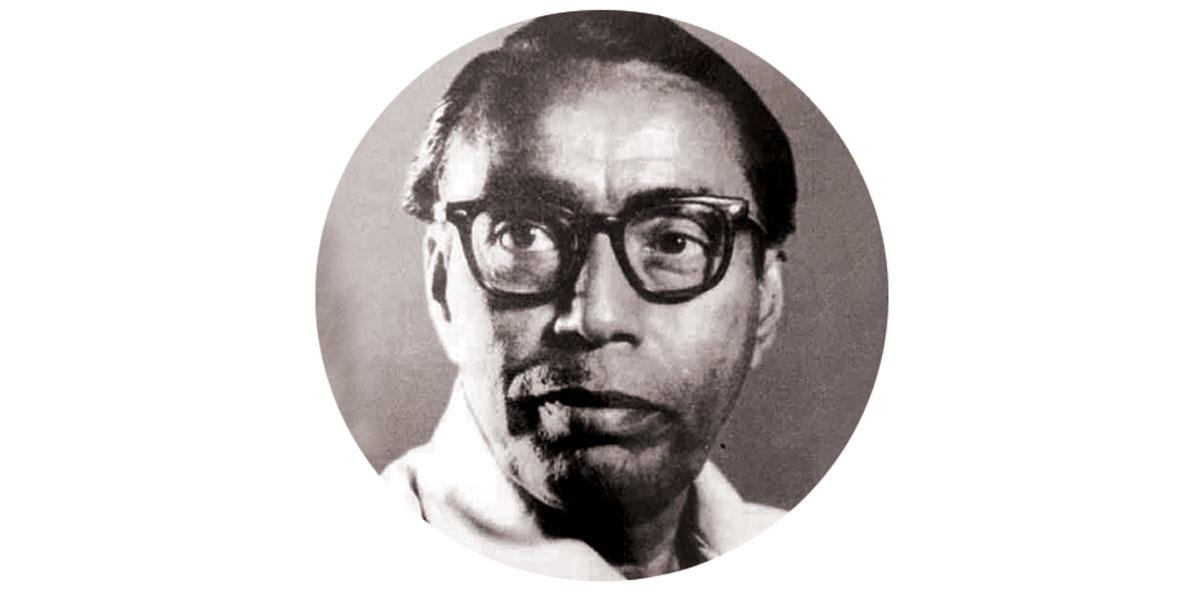
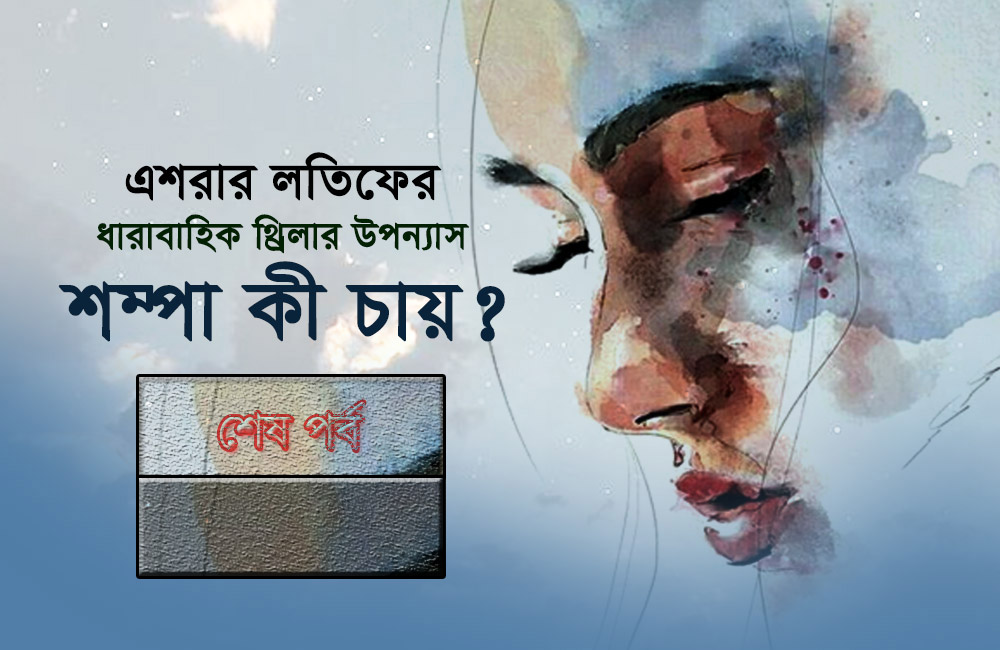





Leave a Reply
Your identity will not be published.