এবারের সংখ্যায় উপস্থাপন করা হলো কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। তিনি বাংলা সাহিত্যে বামপন্থী বিপ্লবী কবি হিসেবে খ্যাত। শোষিত মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও বিরোধের হুঙ্কার তাঁর ভাষায় ফুটে ওঠেছে। আগামী ১২ মে তাঁর ৭৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে এখানে তুলে তুলে ধরা হলো কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য-এর জীবন ও বাস্তুভিটাকে। দীপংকর গৌতম।
এবারে আমাদের গন্তব্য বহুদূর। ঢাকা থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে। গোপালগঞ্জের কোটালীপড়া। এর আগেই আমরা গিয়েছিলাম কবি আবুল হাসানের বাস্তুভিটায়।
টুঙ্গীপাড়া থেকে আমি ও আলোকচিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ সুকান্ত ভট্টাচার্যের বাস্তুভিটার সন্ধানে রওয়ানা হই কোটালীপাড়ার উদ্দেশে। এ জন্য টুঙ্গীপাড়া থেকে গোপালগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ থেকে কোটালীপাড়ার বাসে রওনা হই।
এর আগে একটা কথা বলে রাখি। আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণা সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম কোটালীপাড়ায়। কিন্তু এ তথ্য ঠিক নয়। সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলাদেশে কোনোদিন আসেন নি, তাঁর জন্মও এখানে নয়। কিন্তু যে ভিটাটা সুকান্ত’র বাড়ির পরিচিতি নিয়ে অবহেলায় অনাদরে পড়ে আছে সেখানে সুকান্ত ভট্টাচার্যের বাবা থাকতেন। পরিবার কলকাতায় থাকলেও তিনি চাকরি করতেন মাদারীপুর কোর্টে। ওখান থেকে তিনি কোটালীপাড়া আসতেন প্রায়ই। তাই এটা তাঁর বাস্তুভিটা এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই—দু’বাংলার কোথাও। সেজন্যই আমাদের কোটালীপাড়া যাওয়া।
ছায়া ঢাকা পাখিডাকা গ্রাম। সাপের মতো একে-বেঁকে চলা মাটির সড়ক। দু’পাশে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের ঘরবাড়ি। তার ভেতর দিয়ে পায়ে হাঁটাপথে হেঁটে চললাম আমরা।
কোটালীপাড়া সদরে নেমে আমরা রিকশাযোগে নামলাম গিয়ে সিকির বাজার। ওখান থেকে দুই কিলোমিটারের পথ উনশিয়া গ্রাম।
উনশিয়া গ্রামে যেতে প্রথমে চোখে পড়বে নগরবাসী সাহার জমিদারি। অসাধারণ সৌকর্য মণ্ডিত স্মৃতিমন্দির পার হয়ে সামনে এগিয়ে যেতেই একটা তালগাছওয়ালা ভিটা। তার ওপরে রয়েছে জীর্ণ একখানা ঘরবাড়ি। এলাকার যে-কোনো লোক ‘কবি সুকান্ত’র বাড়ির কথার জিজ্ঞেস করলে ওই বাড়িটাকেই দেখিয়ে দেয়। ওই বাড়ির লোকজনও জানে যে বাড়িটা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের।
এ বাড়ি নাকি প্রায়ই বহু বড় বড় লোকজন দেখতে আসে। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের বহু আশ্বাস দেয় কিন্তু আজ অবধি এখানে কিছুই হয় নি। না হওয়ার কারণে বাড়িটি ক্রমশ দখল হয়ে যাচ্ছে। সুকান্ত ভট্টাচার্য একজন কবি এটুকুই সবাই জানে। এর বাইরে তার সম্বন্ধে ধারণাও কম।
শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের জীবনযন্ত্রণা, সুপ্ত বিক্ষোভ এবং স্বপ্নদেখা মানুষের কবি ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯৬২ সালের ১৫ আগস্ট, মাতুলালয়ে, কালীঘাটের ২৪নং মহিম হালদার স্ট্রিটে। তার বাবার নাম ছিল নিবারণ ভট্টাচার্য এবং মা সুনীতি দেবী। সুনীতি দেবী নিবারণচন্দ্রের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৮ সালে সুকান্তর বয়স যখন ১২ বছর তখন তার মা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সুকান্ত লালিত হন তার মাতামহের বাড়িতে।
সুকান্তর জন্ম কলকাতায় হলেও তার পূর্বপুরুষ ছিল বাংলাদেশের বাসিন্দা। প্রথমে তাদের আবাসস্থল ছিল ফরিদপুরের কোটালীপাড়ায় উনশিয়া গ্রামে। তবে সুকান্তের পুরো সময়টাই কেটেছে কলকাতায়। সুকান্ত প্রাথমিকভাবে পড়াশোনা করেছেন স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ‘কমলা মন্দিরে’। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় ‘সঞ্চয়’ নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন সুকান্ত। তাঁর বয়স যখন ১১ বছর তখন ‘রাখাল ছেলে’ গীতিনাট্য লিখে সুকান্ত খুবই সুনাম অর্জন করেন।
সুকান্ত ভট্টাচার্য স্কুলজীবনের সাথে সাথে সাহিত্য ও রাজনীতির জীবনও শুরু করেছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে যান। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ভর্তি হন দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ে। সুকান্ত যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন ‘সপ্তমিকা’ নামে হাতে লেখা একটি পত্রিকা বের করেন। দেশবন্ধু বিদ্যালয় থেকে সুকান্ত ১৩৫২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। ততদিনে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির এক সক্রিয় সদস্যে রূপান্তরিত হন। সেকালের দৈনিক পত্রিকা ‘স্বাধীনতা’র কিশোরসভা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক ছিলেন তিনি। সুকান্তর কবিতা প্রকৃতপক্ষে গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনের এক অনবদ্য ইস্তেহার।
১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কবিতা বাঙালির মনে শক্তি ও সাহস জোগায়। সুকান্ত যখন কবিতার বিদ্যুৎশক্তিকে কলকারখানায়, খেত-খামারে, ঘরে ঘরে সর্বত্র পৌঁছে দিতে শুরু করেন ঠিক তখনই আসে তার মৃত্যুর ডাক।
আরম্ভেই পরিসমান্তির এই শোকে বাংলা সাহিত্য চিরদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। তাঁর লেখা গ্রন্থ—ছাড়পত্র (১৩৫৪), ঘুম নেই (১৩৫৭), পূর্বাভাষ (১৩৫৭), অভিযান (১৩৬০), হরতাল (১৩৬৯), গীতিগুচ্ছ (১৩৭২)।
ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে ‘আকাশ’ (১৩৫১) নামক কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তিনি। ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পার্টির উদ্যোগে পার্টির চিকিৎসাকেন্দ্রেই তার চিকিৎসা চলতে থাকে। এই সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করলে কারফিউর জন্য তাঁর চিকিৎসা ব্যাহত হয়। জেঠতুত ভাই মনোজ তাঁর সুচিকিৎসার জন্য শ্যামবাজারের বাড়িতে নিয়ে এলে ধরা পড়ে তার যক্ষ্মা হয়েছে। শ্যামবাজারের বাড়ি থেকে সুকান্তকে নিয়ে যাওয়া হয় যাদবপুর টিবি হাসপাতালে। সেখানেই, ১৯৪৭ সালের ১২ মে, বাংলার এই কিশোর কবি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।
বহু ঘটনায় ঋদ্ধ সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন ভূপেন বসু। তাদের বাড়িতে একবার একটি ঘটনায় সুকান্ত খুব আহত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই ঘটনার ভুল বোঝাবোঝি শেষ হওয়ার আগেই তিনি মারা যান। এ ঘটনায় ভীষণভাবে আহত হন ভূপেন বসু’র মা।
ঘটনাটা ছিল এমন যে সুকান্ত একবার ভূপেনদের বাড়িতে গিয়েছিলেন ভূপেনকে খুঁজতে, কিন্তু পান নি। অন্যদিকে সুকান্ত বাম কানে খুবই কম শুনতেন। সুকান্তকে চিনতে না পেরে ভূপেনের মা সুকান্তকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। সুকান্ত জবাব দেন নি শুনতে না পেরে। কিন্তু ভূপেনের মা বুঝতে না পেরে সুকান্তর সাথে দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেন। ভূপেন বাড়ি এসে একথা শুনে খুবই ব্যথিত হন। ভূপেনের মা এরপর একদিন সুকান্তকে বাড়িতে আসতে বলেন। কিন্তু সেই সুযোগ আর হয় নি। ইতিমধ্যে সুকান্ত অনন্তের উদ্দেশে চলে গেছেন।
সুকান্তর ছবি তোলা নিয়েও মজার একটি ঘটনা রয়েছে। সাধারণত সুকান্তর যে ছবিটা আমরা দেখতে পাই ওই ছবিটার সাথে আর দুটো আঙ্গিকে দুটো ছবি তোলা হয়েছিল। ঘটা করে এই ছবি তোলার কারণও ছিল। সুকান্ত যেহেতু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন সেহেতু উপনয়ন তাঁর হতেই হবে। উপনয়ন হলে তাদের নিয়মমতে সে আর ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যকারও ছোঁয়া খেতে পারবে না।
তাই উপনয়নের দুদিন আগে সুকান্তর মেজবৌদি সুকান্তকে এক টাকা হাতে দিয়ে বলেন শিঙারা জাতীয় সব এটো খাবার খেয়ে আসতে। কারণ উপনয়ন হলে তো আর বাইরের খাবার খেতে পারবে না। কিন্তু সুকান্ত ছিলেন একজন কমিউনিস্ট। তিনি তো আর জাত-পাতের মধ্যে থাকবেন না। তাই কিছু না খেয়ে সুকান্ত তিন প্রকারের তিনখানা ছবি তোলেন। যে ছবির একটা সবখানে দেখা যায়। বাকি দুটোও দেখা যায় বিভিন্ন বইয়ে।
পারিবারিক সংকট, ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের ঢেউ এবং সেই জন্য কমিউনিস্টদের ভূমিকা—এসব নিয়ে সুকান্তর ভাবনা ছিল ভিন্ন। গণমানুষের এই কবি তাঁর দায়বদ্ধতা থেকেই পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মীতে পরিণত হন। এবং পোস্টার লাগানো থেকে সব ধরনের প্রচারণায় অংশ নিতেন তিনি। সাথে রুশ বিপ্লবের অনুপ্রেরণা এবং যেসব দেশে সংগ্রাম চলছে সেসব দেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে তিনি লিখতেন অবিরাম। সর্বহারার চেতনায় উজ্জীবিত এই কবি এখনো কবিদের অহংকার বহন করে চলছেন। জীবনে ২২টি ফলবতী ফাল্গুনকে উপভোগ করতে না পারলেও তাঁর সৃষ্টি শোষকের বিরুদ্ধে গণমানুষের সংহতিকে একত্রিত করবেই। যাতে ভেঙে যাবে এই বৈষম্যের দেয়াল, প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বহারার একনায়কত্ব।
এসব ভাবতে ভাবতে বেলা হেলে পড়ে। বিশ্বজিৎ ছবি তুলে যাচ্ছে অবিরাম। উৎসুক লোকজনের ভিড় জমে উঠছে। আমরা সবার কৌতূহলকে পেছনে রেখে নতুন পথের সন্ধানে যাত্রা শুরু করি।
[অন্যদিন বর্ষ ৯ সংখ্যা ১৫, সেপ্টেম্বর ২০০৪]






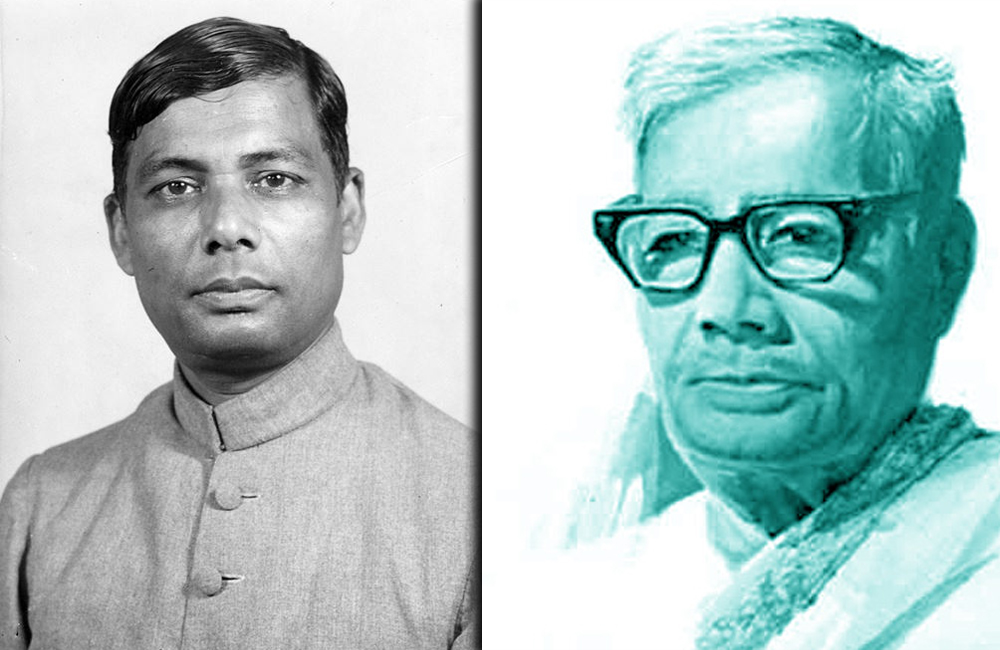
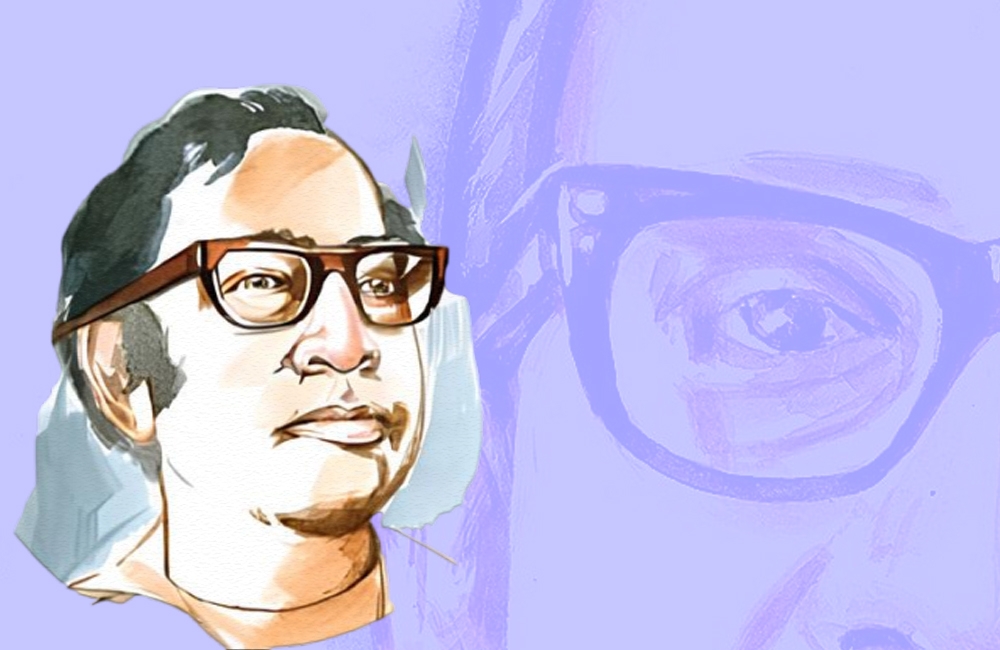
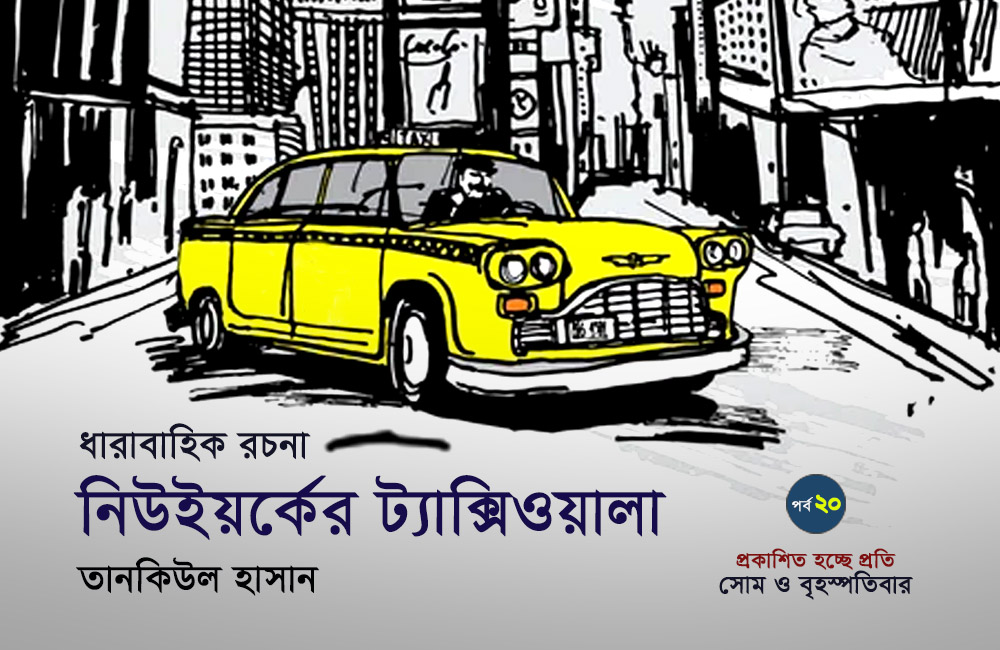


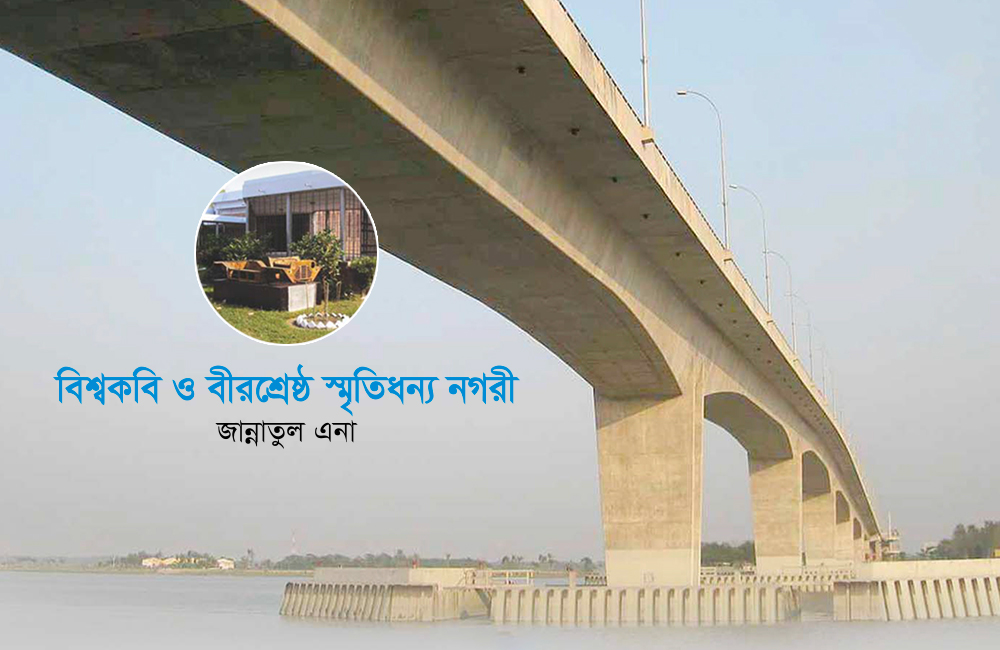
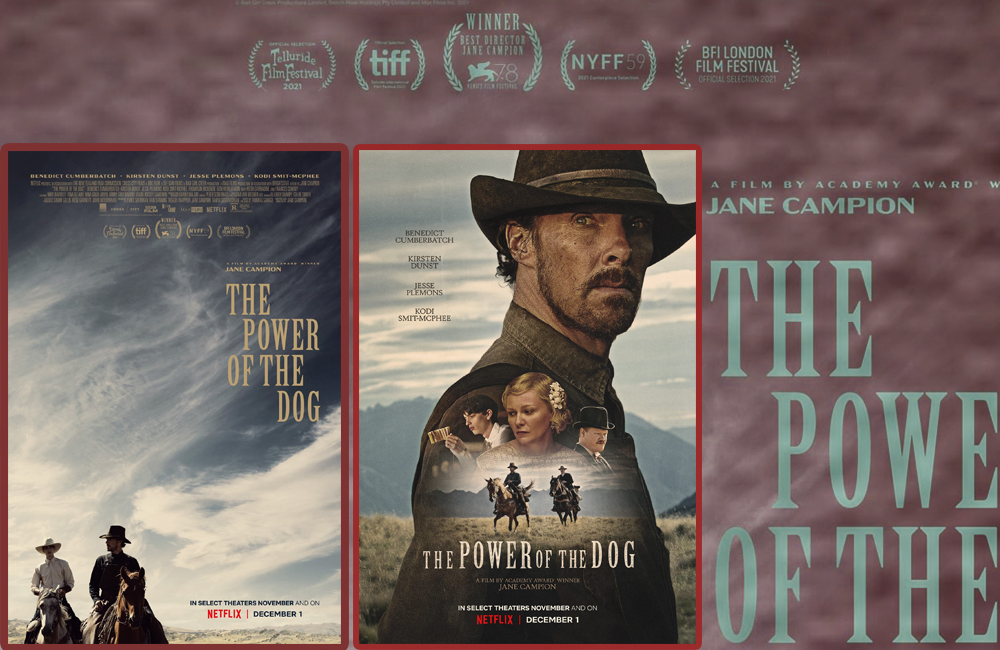


Leave a Reply
Your identity will not be published.